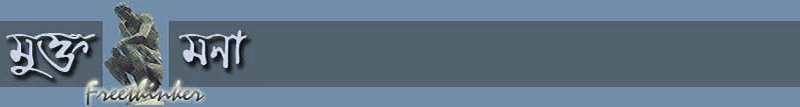
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
সৃষ্টিতত্ত্বের অসারতা
বনাম বিবর্তনতত্ত্বের সাফল্য :
সব জাগতিক বা মহাজাগতিক বস্তুর মত পৃথিবীরও একটা ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস ক্রমপরিবর্তনের ইতিহাস – যুগে যুগে নতুন আকারে বিকাশের ইতিহাস। এই পরিবর্তনের কোনো শেষ নেই, আজও তা ঘটে চলেছে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যদি পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখা যায়, তাহলে দেখা যাবে এই ইতিহাসের শুরু আজ থেকে প্রায় সাড়ে চারশো কোটি বছর আগে। এক মহাজাগতিক বিস্ফোরণে ছিটকে আসা এক জ্বলন্ত প্রস্তরখন্ড রূপে আমাদের পৃথিবী অগণিত মহাজাগতিক তারকার মধ্যে একটির চারদিকে ঘুরতে শুরু করে। সেই তারকা হল সূর্য। তারপরে আরো একশো কোটি বছর এগিয়ে গেলে দেখা যাবে পৃথিবী অনেক শীতল হয়েছে, যদিও বায়ুমন্ডল বিষাক্ত গ্যাসে ভর্তি, প্রাণী বা উদ্ভিদ কোনোটিরই দেখা নেই। তারই মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে আজকের সকল প্রাণীর পূর্বপুরুষ – কিছু অতি সরল ব্যাকটেরিয়া জাতীয় জীব। এই জীবেরা জড় পদার্থের থেকে সামান্যই আলাদা – এরা নিজেদের প্রতিরূপ বানাতে সক্ষম ও বহির্প্রকৃতি থেকে শক্তি সংগ্রহ করে জীবের গঠন উপাদান প্রোটিন সংশ্লেষ করতে পারে।
পরিবর্তনের ইতিহাস আর বিবর্তনবাদ কিন্তু প্রশ্নের কি আর শেষ হয়? কয়েকশো কোটি বছরে কিভাবে সাধারণ ব্যাকটেরিয়া থেকে আমগাছ, হাতি বা তিমিমাছের মত আলাদা প্রাণী তৈরী হল? কেন সরল প্রাণী সরল রয়ে গেল না? পৃথিবীতে এত জীব বৈচিত্র্যের কারণ কি? কেন পৃথিবীতে যত প্রজাতি বাস করেছে তাদের নব্বই শতাংশই আজ বিলুপ্ত? কেন কিছু কিছু জীব তাদের কোটি কোটি বছর আগের রূপেই বর্তমান, অথচ তাদের সমসাময়িক বাকি জীবেরা পরিবর্তিত হয়ে নতুন রূপ ধারণ করেছে? কিভাবে প্রাপ্ত ফসিল থেকে জানা যায় যে মানবজাতির আদি পুরুষ বানর জাতীয় প্রাণী? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় বিবর্তনের তত্ত্বে। বিজ্ঞানের ভাষায়, জীবসমষ্টির বংশানুক্রমিক পরিবর্তনকেই বলা হয় বিবর্তন। জিন (Gene) হল বংশগতির একক, যা জীবের বৈশিষ্ট্যকে এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে বহন করে। জিনের পরিবর্তনের মাধ্যমেই বিবর্তন ঘটে। তবে সামগ্রিক অর্থে, বিবর্তন সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য – সংষ্কৃতি, ভাষা, গান-বাজনা বা স্থাপত্য পরিকল্পনা – সবকিছুই সময়ের সাথে সাথে বিবর্তিত হয়, এগুলো তো চোখের সামনেই ঘটছে। আর বিজ্ঞানের নিরিখে বিবর্তন বর্তমান জীববিজ্ঞানের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শাখা – যার কাজ হল এই পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক গুলো উন্মোচন করে প্রাকৃতিক নিয়মনীতি অনুধাবন করা। কিন্তু কিভাবে আমরা জানতে পারলাম যে জীবসমষ্টির মধ্যে এভাবে পরিবর্তন ঘটে? কিভাবে বোঝা যায় যে কয়েকশ কোটি বছর ধরে জীব বিবর্তিত হয়েই আজকের রূপ ধারণ করেছে এবং এখনও পরিবর্তিত হয়ে চলেছে? কেন আমরা মনে করি এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল এবং কোনো দৈবপ্রভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়? এর উত্তর হল প্রমাণ। গত দুই শতক ধরে মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছে। সেই সমস্ত তথ্যপ্রমাণের সম্মিলিত তাত্ত্বিক রূপ হিসাবে সামনে এসেছে বিবর্তন তত্ত্ব। দেড় শতক আগে প্রথম প্রস্তাবিত হওয়ার পরে, আজ অবধি এই প্রস্তাবের সমর্থনে প্রমাণ এসেছে প্রস্তর স্তরে পাওয়া ফসিল আকারে, এসেছে জীবের শারীরিক গঠন-সামঞ্জস্যের মধ্যে দিয়ে, এসেছে জিন ও DNA আবিষ্কারের মাধ্যমে। তাই আজকের বিজ্ঞানীমহলে বিবর্তনবাদ, মহাকর্ষের মতই সুপ্রতিষ্ঠিত একটি তত্ত্ব।
প্রাচীন পৃথিবীর লোকগাঁথায় সৃষ্টিতত্ব এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা উচিত যে মানবসভ্যতায় একটা বড় সময় ধরে মানুষ জানতই না যে জীব আদৌ পরিবর্তিত হয়। তাদের চোখে পৃথিবী ও জীবজগৎ ছিল স্থিতিশীল এবং অপরিবর্তনীয়। তারা মনে করতেন সৃষ্টির আদি থেকে সমস্ত জীবপ্রজাতি অপরিবর্তিত আকারে বিদ্যমান। এর ফলে তাদের সৃষ্টিরহস্য ব্যাখ্যায় সাহায্য নিতে হত কোনো অতিপ্রাকৃতিক শক্তির বা কোনো অলীক কল্পনার, যার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। একারণেই পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্যতায় সৃষ্টির একেকরকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এদের অধিকাংশই ঈশ্বর প্রভাবিত সৃষ্টি-প্রক্রিয়া। ইরাকে গড়ে ওঠা প্রাচীন ব্যাবিলনের লোকেরা মনে করত যে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতকে। সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার প্রারম্ভে পৃথিবীতে শুধু জল ছিল, আর তাতে এক মিষ্টি জলের দেবতা (আপ্সু) আর এক নোনা জলের দেবী (তিয়ামাত) থাকতেন।বজ্রবিদ্যুতের দেবতা (মারদুক) তিয়ামাতকে মেরে তার শরীরের দুই অংশ নিয়ে স্বর্গ-নরক তৈরী করে। মধ্য আমেরিকার মায়া সভ্যতার সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় একাধিক দেবদেবীর ভূমিকা ছিল। তাদের মতে, পৃথিবী হল জলে ভাসমান একটি বৃহৎ কুমীরের পৃষ্ঠে অবস্থিত। স্বর্গ ও নরকের একাধিক স্তরের মধ্যে আছে সংযোগরক্ষাকারী একটি বিশাল বৃক্ষ, যা প্রকৃতপক্ষে রাজার প্রতিমূর্তি। সমগ্র পৃথিবী ৫০০ বছরের আবর্তে ধ্বংস ও সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ আমেরিকার ইনকাদেরও একইরকম চক্রাবর্তে ধ্বংস-সৃষ্টির ধারণা ছিল। তাদের মতে মৃতরা কোনো অতিপ্রাকৃতিক জগতের বাসিন্দা, তাই তারা মৃত শরীরকে মমি বানিয়ে সংরক্ষণ করত। প্রাচীন মিশরে মনে করা হত যে সৃষ্টির আদিতে সমগ্র জগৎ জলপূর্ণ ছিল, তাতে সূর্যদেব রা সর্বপ্রথম উদিত হন। দেবরাজ রা-এর দুই সন্তান হল বায়ুমন্ডল যা এক তৃতীয় সন্তানের ওপর অবস্থিত। এই তৃতীয় সন্তান হল পৃথিবী। আকাশ হল তার চতুর্থ সন্তান। আফ্রিকায় মাসাই উপজাতির মতে সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বর একটি বৃক্ষকে চিরে তিন খন্ড করেন। প্রথম খন্ড থেকে একটি লাঠি দেন মাসাইদের পিতৃপুরুষকে পশুপালনের জন্য, একটি লাঙল দেন কিকয়ু পিতৃপুরুষকে চাষ করার জন্য আর একটি তীরধনুক দেন কাম্বাকে শিকার করার জন্য। প্রাচীন গ্রীকদের ধারণায় বিশৃঙ্খল অন্ধকার শূন্যতা থেকে পৃথিবী, তারা আর পাতাল তৈরি হয়। পরে প্রমিথিউস পশুদের থেকে উন্নততর এক প্রাণীরূপে মানবজাতির সৃষ্টি করেন। প্রাচীন ভারতীয় সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে প্রজাপতি ব্রম্ভা দেব-দেবী এবং পরবর্তীকালে মানুষকে সৃষ্টি করেন। তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় সৃষ্টিতত্ত্ব হল আব্রাহামিক ধর্মগুলোর (ইহুদী, খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্ম) সৃষ্টি প্রক্রিয়া। এই মত অনুসারে, কয়েক হাজার বছর আগে ঈশ্বর ছয়দিনে স্বর্গ, নরক, পৃথিবী, মানুষ আর পশুদের সৃষ্টি করেন। এই মত অনুসারে, প্রথম পুরুষ আদম আর প্রথম নারী ইভ, ইডেন উদ্যানে আর সব প্রাণীদের সাথে সহাবস্থান করতেন। এক ধূর্ত সাপের (শয়তানরূপী) পরামর্শে ইভ নিষিদ্ধ ফল আদমকে খাওয়ালে শাস্তিস্বরূপ ঈশ্বর তাদের পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তাদের দুই ছেলে হয় – কেন আর আবেল। মানবজাতি এই আদম ও ইভের বংশধর। পরবর্তীকালে, পৃথিবীকে পাপমুক্ত করার জন্য ঈশ্বর পৃথিবী-ব্যাপী বন্যা সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরের কৃপায় নোয়া (নূহ) তার নৌকয় সমস্ত প্রজাতির একজোড়া প্রাণী নিয়ে বেঁচে থাকে। সেই বেঁচে থাকা প্রাণীদের থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান সব প্রাণীর। ইসলাম ধর্ম অনুসারে, আদম ছিলেন মানবজাতির প্রথম প্রথম নবী বা দৈবজ্ঞ। ঈশ্বর-সৃষ্ট এই পৃথিবী সার্বিকভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ, এবং এর সবকিছুই নিখুঁতভাবে পরিকল্পিত। এই শৃঙ্খলার মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ত্ব প্রতীয়মান।
বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে লোকগাঁথা আজকের বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ধর্মগ্রন্থে বা লোকগাঁথার এই সৃষ্টিতত্ত্ব স্বীকৃত নয়। কারণ খুবই সাধারণ – এদের স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। যেকোনো তত্ত্ব বা ধারণার সত্যতা যাচাই করার সবচেয়ে সহজ পন্থা হল ধারণাটির স্বপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করা এবং পরীক্ষার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা। এই পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণ করেই মানুষ আজ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণে এনেছে, অনুধাবন করেছে প্রকৃতির নীতিমালা। বিজ্ঞান কেবলমাত্র বাস্তব সত্যকেই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে পারে, মানুষের মন পরিবর্তন করতে পারে না। আমাদের বিবর্তনের ইতিহাস সেরকমই এক বাস্তব সত্য, যা বিজ্ঞানের চোখে প্রমাণিত। কিন্তু মানুষের মনে রয়ে গেছে সেই প্রাচীন লোকগাঁথার রেশ। তাই ধার্মিক মানুষেরা ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত সবকিছুই প্রশ্নাতীত সত্য বলে মেনে নেন - ধরে নেন এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মানুষ সহ সকল প্রাণের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। কিভাবে বিজ্ঞান সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে এই লোকগাঁথাগুলোর মধ্যে সত্যতা নেই? কেন মনে করে এগুলো মানুষের জ্ঞান ও প্রমাণের অভাবের ফলে তৈরি কিছু অলীক গল্প? দেখা যাক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এদের ত্রুটি কোথায়।
মাত্র সাত দিনে মহাবিশ্ব? সাতটি আক্ষরিক দিনে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে বলে এখন বিজ্ঞানীরা দূরে থাক, সাধারণ শিক্ষিত মানুষও মনে করেন না। কিন্তু এই মতাবলম্বীরা সবসময়েই মত পরিবর্তন করে চলেন। একটা সময় এই ধর্মবাদীরা ধর্মগ্রন্থের সবকিছু আক্ষরিক অর্থেই গ্রহণ করতেন। কিন্তু যখন থেকে তারা বুঝলেন যে বিজ্ঞানের দেখানো সময়ের সাথে তাদর ধর্মগ্রন্থের বেঁধে দেওয়া 'সাত দিন'-এর বিস্তর ফাঁরাক, তারা নিরূপায় হয়ে নিজেদের মত করে ঐ সাতদিনকে সাজালেন। আপাতত, তাদের ব্যাখ্যা অনুসারে সাতটি দিন আসলে সাতটি যুগ, যাতে ধাপে ধাপে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বিগ ব্যাংগ কে যদি সৃষ্টির আদি ধরে নেওয়া যায়, তাহলে মহাবিশ্বের শুরু ১৫ বিলিয়ন বছর আগে। আর পৃথিবী তৈরী হয় সাড়ে ৪.৫ বিলিয়ন বছর আগে। এই ১০ বিলিয়ন বছর যদি প্রথম দুটি দিন (তৃতীয় দিনে ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেন) হয়, তবে পরবর্তী সাড়ে চার বিলিয়ন বছর কিভাবে পরবর্তী চার দিন হয়? এই মতাবলম্বীরা আবার নতুন ব্যাখ্যা নিয়ে আসেন, বলেন দিনের দৈর্ঘ্য যে সুষম হতেই হবে তার তো কোনো মানে নেই। আপাতদৃষ্টিতে এই যুক্তি যথেষ্ট আপত্তিকর মনে হলেও এর ফলেও কিন্তু সাত দিনে সৃষ্টির কোনো কিনারা হয়না। বরং আরো বড় কিছু ত্রুটি সামনে চলে আসে। ঈশ্বর পৃথিবী তৃতীয় দিনে সৃষ্টি করলেও তখনও চন্দ্র-সূর্য কিছুই নেই, অথচ পৃথিবীতে উদ্ভিদ বর্তমান। চতুর্থ দিনে তিনি চন্দ্র-সূর্য-তারা গঠন করেন ও আকাশ আলোকিত করেন। বাস্তবে, অধিকাংশ তারাই বয়সে পৃথিবীর চেয়ে বড়। তাই পৃথিবী গঠিত হবার পরে আকাশে তারার আবির্ভাব ঘটেছে, এটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া, সূর্যের অনুপস্থিতিতে উদ্ভিদের বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তাই, শুধু সৃষ্টির সময়ে নয়, সৃষ্টির ক্রমেও এই সৃষ্টিতত্ত্ব অবৈজ্ঞানিক।
পৃথিবীব্যাপী বন্যা কবে? যদিও প্রায় সব লোকগাঁথায় প্রবল বন্যায় জীবজগৎ ধ্বংসের কথা লেখা আছে, বাস্তবে, এখনও পর্যন্ত কোনো পৃথিবীব্যাপী বন্যার ভূতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বিজ্ঞানীদের মতে কিছু প্রবল স্থানীয় বন্যাই লোকগাঁথায় এরকম ধারণার উৎস। যদি পৃথিবীব্যাপী একবারও বন্যা হয়ে থাকত, তাহলে সেই বন্যার বর্ণনায় সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে একটা সাযুজ্য লক্ষ্য করা উচিত। বাস্তবে তার বিপরীতই দেখা যায়।
জাহাজে প্রাণীদের স্থান সংকুলান হল কিভাবে? প্রাচীন ভারতে মৎসপুরাণে, সুমেরীয় ও হিব্রু (আব্রাহামিক) উপকথায় বলা আছে একটি বিশাল জাহাজে পৃথিবীর বর্তমান সব প্রজাতির যুগল নিয়ে বন্যা থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে রাখার কথা। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে এত অসংখ্য প্রজাতি আছে তাদের সবাইকে একই জাহাজে স্থান দেওয়া সম্ভব নয়। সহজ হিসাব করে দেখানো যায়, এরকম জাহাজটির ধারণক্ষমতা হতে হবে কমপক্ষে ১০ মিলিয়ন কেজি। একটা জাহাজ কতটা বড় ও মজবুত হলে এত ওজন নিতে পারবে? আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে কি সেই উন্নত টেকনলজি মানুষের কাছে ছিল? শুধু তাই নয়, সব জীবকে একত্র করাও কি সহজ কাজ? পৃথিবীর সমস্ত প্রজাতির যুগল-নমুনা সংগ্রহ করতে কয়েকশ বছর লেগে যাওয়ার কথা। যদি উল্টোটাও ধরা যায়, সব প্রজাতিরা নিজেরাই জাহাজে এসেছিল, তাহলেও অনুমানে বিশেষ উন্নতি হয় না। শ্বেত-ভালুক আর হাতি একই পরিবেশে বেঁচে থাকবে এটা সম্ভব নয়, তাই একই জাহাজে একই পরিবেশে তাদের প্রাণধারণ করা প্রশ্নাতীত। খাদ্যসমস্যার কথাও ভেবে দেখার মত। বিভিন্ন প্রজাতির বিভিন্ন খাদ্যাভ্যাস – সকলকে সন্তুষ্ট করতে গেলে প্রচুর পরিমাণে এবং বিভিন্ন ধরণের খাবার দরকার। আসলে যারা অনেক বছর আগে এই ধর্মগ্রন্থগুলো লিখেছিলেন তাদের কোনো ধারণাই ছিল না যে পৃথিবীটা সত্যি কতটা বড় ও কত বৈচিত্র্যময়। তাদের জীবনে তারা যে কয়েকটি জীবপ্রজাতির সম্মুখীন হতেন, সেগুলো হয়ত একটা প্রমাণ আকারের জাহাজে স্থান করে নিতে পারত। কিন্তু ভবিষ্যতে মানুষের যত জ্ঞানের পরিধি বেড়েছে, ততই মানুষ এইসব ধারণাকে প্রশ্ন করতে শিখেছে। আজকের জগতে এই লোকগাঁথাগুলোর ইতিহাসের পাতায় ছাড়া স্থান নেই।
ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব স্বাভাবিকভাবেই এইসব ত্রুটি থাকার কারণে অনুসন্ধিৎসু মানুষের কাছে ধর্মীয় ব্যাখ্যা জনপ্রিয়তা কমে চলেছিল। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে নৌ-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি ও পৃথিবী সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণার স্বচ্ছতার কারণে এরকম অনেক অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি প্রমাণের খোঁজে বিশ্বের নানা প্রান্তে গিয়ে হাজির হলেন। এরকমই একজন ছিলেন চার্লস ডারউইন। তিনি পাঁচ বছর ধরে বিগল নামক একটি জাহাজে চড়ে বিশ্বের নানাপ্রান্তে ঘুরে জীববৈচিত্র্যের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। তারও কুড়ি বছর পরে, ১৮৫৯ সালে, তিনি ‘অরিজিন অব স্পিসিস’ নামক একটি বইতে (Origin of Species) তার পর্যবেক্ষণ ও সংগৃহীত তথ্য সহ একটি মূল তত্ত্বের আকারে প্রকাশ করেন। এই তত্ত্ব ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব নামে খ্যাত। বর্তমানে এটি হল বিবর্তনবাদের সর্বজনস্বীকৃত মতবাদ। প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব অনুসারে, একই প্রজাতির জীবগোষ্ঠীর মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতা হয়। আর প্রতিযোগিতায় যোগ্যতমই বেঁচে থেকে বংশবিস্তার করার সুযোগ পায়। জীবের যে বৈশিষ্ট্য তাকে এই প্রতিযোগিতায় সুবিধা প্রদান করে, সেই বৈশিষ্ট্য ক্রমাগত নির্বাচিত হওয়ার ফলে জীবগোষ্ঠীর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহে পরিণত হয়। প্রাকৃতিক নির্বাচনের পর্যায়গুলো হল – · জীবের প্রজননের মাধ্যমে অপত্যের সৃষ্টি হয়। · একই জীবের অপত্যের মধ্যে জন্মগত প্রকরণ (variation) বা বৈশিষ্ট্য-পার্থক্য থাকে। · জীবের যে বৈশিষ্ট্য তাকে প্রকৃতিতে মানিয়ে নিতে, বেঁচে থাকতে এবং প্রজননে (Reproduction) সাহায্য করে, সেই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী জীবের বংশবিস্তারের সম্ভাবনাও বাড়ে। · এর ফলে পরবর্তী প্রজন্মে আরো বেশী-সংখ্যক জীবের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যাবে। · এই বৈশিষ্ট্যগুলো জীবের মধ্যে একত্রিত হতে থাকবে। · ক্রমাগত পরিবর্তনের মাধ্যমে, কালানুক্রমে জীবগোষ্ঠীর সামগ্রিক ভাবে নতুন শ্রেনীর জীবগোষ্ঠীতে পরিণত হবে। · আঞ্চলিকভাবে বিচ্ছিন্ন একাধিক জীবগোষ্ঠী নিজ-নিজ পরিবেশ অনুসারে বিবর্তিত হয়ে একাধিক জীবে পরিণত হবে। · এভাবেই, পরিবেশগত বৈচিত্র্যের জন্য পৃথক জীবগোষ্ঠীর বিবর্তনের মাধ্যমে পৃথিবীতে জীব-বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে।
ক্রমপুঞ্জিত প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে জটিল থেকে জটিলতর বৈশিষ্ট্য জীবের মধ্যে প্রকাশ পায়। সেকারণে, রিচার্ড ডকিন্স তার দ্য ব্লাইন্ড ওয়াচমেকার (The Blind Watchmaker) বইতে প্রাকৃতিক নির্বাচনকে অন্ধ পরিকল্পনাকারী আখ্যা দিয়েছেন। সাম্প্রতিককালে আমেরিকান দার্শনিক ড্যানিয়েল ডেনেট ডারউইনের তত্ত্বকে ‘সর্বজনীন অ্যাসিড’ বলে বর্ণনা করেছেন, কারণ সব প্রাচীন ধর্মমতের মূল ধারণামূলে এটি আঘাত করে।
কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কি ভুল হতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে। কিন্তু প্রাকৃতিক নির্বাচন বা বিবর্তনের তত্ত্বের স্বপক্ষে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে যে অপরিসীম প্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে, কোনো নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে তাকে সেই সমস্ত প্রমাণ সহ নতুন প্রমাণগুলোর সার্থক ব্যাখ্যা দিতে হবে। আধুনিক জীববিজ্ঞানে বিবর্তনবাদ ছাড়া কোনো জটিল বিষয়ের সমাধান সম্ভব নয়। তাই এটা বললে অত্যুক্তি হয় না যে বিবর্তন ছাড়া আধুনিক বিজ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না।
সৃষ্টিতত্ত্ব বা সৃষ্টিবাদ বিবর্তনের স্বপক্ষে এত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বহু মানুষ আজও এতে বিশ্বাসী নন। তার কারণ, বিবর্তনে বর্ণিত সৃষ্টিপদ্ধতি তাদের নিজ-নিজ ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই শ্রেণীর মানুষ সাধারণত খুবই ধার্মিক এবং বিবর্তনবাদ নিয়ে সঠিক জ্ঞান এদের নেই। এদের স্বীকৃত অধিকাংশ মতের বিজ্ঞানে কোনো স্থান নেই। যেমন ধরা যাক, আমেরিকায় অধিকাংশ ধার্মিক মানুষের মতে পৃথিবীর বয়স মাত্র ছয় থেকে দশ হাজার বছর। এই মত মেনে নিলে বিবর্তন তো দূরে থাক, আধুনিক ভূতত্ত্ববিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ধারণাগুলোও পরিবর্তন করতে হবে। ভূতাত্ত্বিকরা (Geologists) মনে করেন ভূত্বক বা প্লেট (tectonic plate) সদা তার নিচের স্তরের ওপর ভাসমান এবং একটি নির্দিষ্ট গতিতে চলমান। তার ফলে কোটি কোটি বছর ধরে মহাদেশ ও মহাসাগরের মানচিত্র পরিবর্তিত হচ্ছে, জেগে উঠেছে নতুন পর্বত। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন ধরে ক্ষয়ের ফলে পর্বত থেকে তৈরি হয় মালভূমি, তৈরি হয় গিরিখাত। অপরপক্ষে ধার্মিকরা মনে করেন এসবই সৃষ্টির পর থেকে বছরের পর বছর ধরে অপরিবর্তিত আকারে বিদ্যমান। এই ধর্মকেন্দ্রিক মতবাদগুলোকেই সম্মিলিতভাবে নাম দেওয়া হয়েছে সৃষ্টিতত্ত্ব বা সৃষ্টিবাদ। এই মতবাদের চর্চা হয় বিভিন্ন সংগঠনে – যেমন সান দিয়েগোতে স্থিত ‘ইন্সটিটিউট ফর ক্রিয়েশন রিসার্চ’ (Institute for Creation Research) বা সংলগ্ন মিউজিয়াম যাতে ঈশ্বরের বিভিন্ন 'সৃষ্টি' প্রদর্শিত হয়। এদের পক্ষে ঈশ্বরের অস্ত্বিত্ত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নয়, তাই এদের মূল লক্ষ্য হল বিবর্তনবাদের মধ্যে ফাঁক খুঁজে বের করা, যাতে বিবর্তনবাদ আর সর্বজনগ্রাহ্য না হয়। কিন্তু বাস্তবে এরা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির ধূম্রজাল সৃষ্টি ছাড়া কিছুই করে না। এই শ্রেণীর বক্তারা জানেন যে বিজ্ঞনীরা বিবর্তনের স্বপক্ষে এত প্রমাণের সম্মুখীন হন, এবং তাদের এই বিষয়ে ধারণাও এত বিস্তৃত যে তাদের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে প্রত্যয় আনা সম্ভব নয়। তাই তাদের তত্ত্বের লক্ষ্য হল সাধারণ মানুষ, যারা ধার্মিক মতবাদগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে আহরণ করে। পৃথিবীতে যেহেতু বহু মানুষ আজো প্রকৃত শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, তাদের মনের মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রোথিত করে উত্তেজনা সৃষ্টি করাই এদের উদ্দেশ্য। এক নজরে এবার দেখে নেওয়া যাক বিভিন্ন সৃষ্টিতত্ত্বগুলো। এদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে জনপ্রিয়।
নবীন পৃথিবী সৃষ্টিতত্ত্ব (Young Earth Creationism) এই তত্ত্বের প্রবক্তারা মনে করেন ঈশ্বর স্বয়ং পৃথিবী এবং সকল প্রজাতির সৃষ্টিকর্তা। তাদের মতে জেনেসিস বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রায় দশ হাজার বছর আগে মহাবিশ্ব সহ পৃথিবীর সৃষ্টি। সমীক্ষামতে, আমেরিকার ৪৭% বাসিন্দা এই তত্ত্বে সহমত। সম্প্রতি সিন্সিনাটিতে এরা একটি বিশাল মিউজিয়ামের উদ্বোধন করেছে যাতে ঈশ্বরের বিভিন্ন সৃষ্টিকে তুলে ধরা হয়েছে। খ্রীষ্টধর্ম ছাড়াও ইসলাম এবং ইহুদী ধর্মাবলম্বীরাও অনেকে এই বক্তব্যের সমর্থন জানায়। প্রবীণ পৃথিবী সৃষ্টিতত্ত্ব (Old Earth Creationism) এই তত্ত্বের প্রবক্তারাও মনে করেন ঈশ্বর স্বয়ং পৃথিবী এবং সকল প্রজাতির সৃষ্টিকর্তা – তবে জেনেসিসের কয়েকটি অংশের অন্যরকম ব্যাখ্যার ফলে তাদের পৃথিবীর বিজ্ঞানসম্মত বয়স মেনে নিতে আপত্তি নেই। তারা বলেন স্বর্গ-মর্ত্য-নরক সৃষ্টির পরে অনেককাল সেখানে হয়ত কিছুই ছিলনা, মাত্র দশ হাজার বছর আগে ঈশ্বর সেখানে প্রাণ ও প্রজাতির সৃষ্টি করেন। উন্নতিশীল সৃষ্টিতত্ত্ব (Progressive Creationism) এই মতের প্রবক্তারা মনে করেন বাইবেলে (বা কোরাণে) বর্ণিত সৃষ্টি-প্রক্রিয়া পার্থিব ছয়দিনে সম্পূর্ণ হয়নি। ঈশ্বরের কাছে একদিনের অর্থ একেকটি যুগ। তবে এরাও বিবর্তনবাদ অস্বীকার করেন, এবং মনে করেন পৃথিবীর ইতিহাসে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে (যেমন মানবজাতির উৎপত্তি) ঈশ্বর সরাসরি সৃষ্টি-প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছেন। বিশ্বাসী বিবর্তনবাদ (Theistic Evolutionism) এই মতের প্রবক্তারা মনে করেন বিবর্তন হল ঈশ্বর প্রভাবিত একটি উপায় মাত্র, যার মাধ্যমে পৃথিবীতে একাধিক জীব-প্রজাতি সৃষ্টি হয়েছে। তারা মনে করেন জেনেসিস আক্ষরিক অর্থে ধ্রুব সত্য নয়, রূপকার্থে বর্ণিত। এটি হল ক্যাথলিক চার্চের অফিসিয়াল মতবাদ। এই মতে, পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি এবং পরবর্তী বিবর্তন দৈববিধি দ্বারা পরিচালিত।
অন্যান্য ধর্মে সৃষ্টিতত্ত্ব হিন্দু সংগঠন ইস্কনের প্রধান স্বামী প্রভুপদ প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তনের তত্ত্বে বিরোধী। ‘লাইফ কামস আফটার লাইফ’ বইতে তিনি এই বিবর্তনবাদের সমালোচনা করেছেন। বাইবেলের মত কোরাণে বর্ণিত উপায়ে জীব ও বিশ্ব সৃষ্টির বিরোধিতা করে বলে মুসলিম সমাজেও সৃষ্টিতত্ত্ব জনপ্রিয় হচ্ছে। আমেরিকায় এই মতবাদের মূল প্রবক্তা হারুন ইয়াহিয়া ও তার সংগঠন বি.এ.ভি। তুরস্কে এর প্রধান প্রচারক ফেতুল্লা গুলেন। এছাড়া মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াতেও এই মত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সাধারণভাবে এদের প্রচারিত বক্তব্য সুপরিকল্পিত সৃষ্টিতত্ত্ব বা নবীন পৃথিবী সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে মেলে।
সুপরিকল্পিত সৃষ্টিতত্ত্ব (Intelligent Design) ক্রমাগত প্রমাণের বিরুদ্ধে ধর্মীয় চেতনায় আঘাতের ফলে পূর্ববর্ণিত প্রায় সব সৃষ্টিতত্ত্বই এখন ম্রীয়মান। তাই, তাদের স্থান দখল করেছে একদল নতুন সৃষ্টিবাদী ‘বিজ্ঞানী’ – যাদের মূল মতবাদ হল 'সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প' বা সুপরিকল্পিত সৃষ্টিতত্ত্ব। এই তত্ত্বের দাবী হল – “মহাবিশ্ব ও জীবজগতের কিছু বৈশিষ্ট্য কেবলমাত্র কোনো বুদ্ধিমান সত্ত্বার পরিকল্পিত হস্তক্ষেপের মাধ্যমেই ব্যাখ্যা করা যায়।” বক্তব্যের স্বপক্ষে তাদের প্রমাণ হল কিছু বিচ্ছিন্ন জীববৈশিষ্ট্য, যা, তত্ত্বমতে হ্রাস-অযোগ্য জটিলতা। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন ঘটলে সরল অঙ্গ ক্রমাগত নির্বাচনের মাধ্যমে জটিল ও শক্তিশালী হবে। প্রকৃতিতে একই সাথে অঙ্গের সরল এবং জটিল রূপ পাওয়া যাবে। বিহে তার বই ‘ডারউইন্স ব্ল্যাক বক্স’-এ এরকম হ্রাস-অযোগ্য জটিলতার কিছু উদাহরণ দিয়েছেন। এই ধরণের সৃষ্টিতাত্ত্বিকেরা আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সত্য যাচাই করার কথা বললেও তারাও প্রকৃতপক্ষে ছদ্ম-ধার্মিক ধারণা গুলোকেই বিজ্ঞান বলে উপস্থাপন করার চেষ্টা চালিয়ে যান।
বিবর্তন-সৃষ্টিতত্ত্ব বিবাদ প্রকৃত বিজ্ঞানীরা স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধারণা বা তত্ত্ব গঠন করে তার স্বপক্ষে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেন, নিয়মিত পরীক্ষার ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সেই তত্ত্বের সত্যতা যাচাই করেন। তাদের তত্ত্বের দাবীও কখনো একতরফা হতে পারে না, সমসাময়িক আরো বিজ্ঞানীরা তা পর্যালোচনা করে তার ভুলত্রুটি নিরীক্ষণ করেন। সংশোধিত আকারে তত্ত্বটি বিজ্ঞানীমহলে স্বীকৃত হয়। অপরপক্ষে সৃষ্টিতাত্ত্বিকেরা, নিজেদের বিজ্ঞানী বলে দাবী জানালেও তারা এইধরণের প্রক্রিয়া মেনে চলেন না। তারা ধরে নেন যে সকলের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর। প্রমাণ অনুসন্ধান করেন কিভাবে মানুষ ও ডাইনোসর একই পথে হেঁটেছিল, কেউ বা নোয়ার জাহাজের ধ্বংসাবশেষ খুঁজতে ব্যস্ত। আসলে তারা সাধারণ মানুষের মনে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করতে চান যাতে তারা মনে করতে থাকে বিবর্তনবাদ হল একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মাত্র যার স্বপক্ষে খুব বেশি প্রমাণ নেই। অদূর ভবিষ্যতে বিবর্তনবাদ বিজ্ঞান থেকে বিতাড়িত হবে।
সৃষ্টিতাত্ত্বিকেরা বিবর্তনবাদে বিশ্বাস না করার কারণ হিসাবে এই মতবাদের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা ও প্রমাণের অনুপস্থিতির কথা তুলে ধরেন। এইরকম কয়েকটি অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করা হল।
ভুল ধারণা- এক : বিবর্তন একটি অনুকল্প (Hypothesis) বা তত্ত্ব (Theory) যা প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয় বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অনুকল্প হল এমন একটি প্রস্তাব, সরাসরি পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষার মাধ্যমে যার সত্যতা যাচাই করা সম্ভব নয়। সাধারণভাবে, তত্ত্ব হল মতবাদ যা ভবিষ্যতে প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একটি তত্ত্ব হল এমন একটি মত যা – · অনেকগুলো ধারণাকে একত্রিত করে · কোনো প্রাকৃতিক ঘটনাকে সফলভাবে ব্যাখ্যা করে · যার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই · উপর্যুপরি বিভিন্ন ধারা থেকে প্রাপ্ত প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত এই মতামত অনুসারে, বিবর্তনবাদ ও প্রাকৃতিক নির্বাচন মহাকর্ষ তত্ত্বের মতই আরো একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব – কোনোরকম অনুমানভিত্তিক নয়। আপেল মাটিতে পড়বে কিনা, বা পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে কিনা – এগুলো যেমন কোনো অনুমান নয়, বিবর্তনও সেরকম। তা সত্ত্বেও যারা বলেন – “তবুও নিশ্চিত হওয়া যায়না” – তারা আসলে দার্শনিক আপেক্ষিকতার ফাঁদে পা দেন। আমরা কখনই সর্বজ্ঞ হতে পারব না, তাই চূড়ান্ত সত্য বলে বিজ্ঞানে কিছু নেই। কিন্তু, তা সত্ত্বেও সত্য বলে বিজ্ঞান তাকেই মেনে নেয় যার স্বপক্ষে জোরালো সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে।শুধু তাই নয়, তত্ত্বটিকে ঠিক বলে ধরে নিলে যে অনুসিদ্ধান্ত পাওয়া যায় তারও প্রমাণ দরকার। সর্বোপরি, তত্ত্বটির ভবিষ্যতবাচ্যতা থাকতে হবে। বিজ্ঞানে কোনো তত্ত্ব একদিনে সত্য বলে প্রমাণিত হয় না। বিবর্তনতত্ত্ব গত ১৫০ বছর ধরে বিভিন্ন শাখায় নিজ স্বপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করে এসেছে - তবেই তা বিজ্ঞান-স্বীকৃত তত্ত্ব হয়ে উঠেছে। যেকোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে ভুল প্রমাণ করার জন্য তার বিরুদ্ধে কিছু নিশ্চিত প্রমাণ দরকার হয়। বিজ্ঞানী হালডেনের মতে, প্রিক্যাম্ব্রিয়ান যুগে যদি খরগোশের জীবাশ্ম পাওয়া যায়, তবে বিবর্তন তত্ব তৎক্ষণাৎ ভুল বলে প্রমাণিত হবে। এধরনের কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণও এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে নেই। বিজ্ঞানীমহলে বিবর্তনবাদের স্বীকৃতি সর্বজনীন। ১৯৯১ গ্যালপ পোল অনুসারে, আমেরিকায় বিজ্ঞানীদের মধ্যে ৫% সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস করেন। কিন্তু এদের মধ্যে কম্পিউটার বা মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার-রাও সামিল। শুধু জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে ১৯৯৫ সালে হওয়া সমীক্ষায় ৪,৮০,০০০ জনের মধ্যে মাত্র ৭০০ জন সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসী পাওয়া গেছে। ন্যাশনাল অ্যাকাডেমী অব সায়েন্স, (একটি সংগঠন ৭২ জন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী যার সদস্য) বিবর্তনের স্বপক্ষে একটি নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু করেছেন। বর্তমানে এই সমর্থন আরো বাড়ছে।
ভুল ধারণা- দুই : বিবর্তন একটি র্যান্ডম (Random) প্রক্রিয়া কিছু র্যান্ডম প্রক্রিয়া বিবর্তনকে প্রভাবিত করলেও, সামগ্রিক ভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচন কখনোই র্যান্ডম নয়। প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বে বিবর্তনের মূল নিয়ন্ত্রক হল প্রকৃতি ও পরিবেশ – প্রকৃতি যাকে নির্বাচন করে, সেই বংশবিস্তারের সুযোগ পায়। সেকারণে অভিপ্রয়াণ বা স্থান-পরিবর্তনের ফলে জীবগোষ্ঠী্র বিবর্তন ঘটেছে। নতুন স্থানে নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে যে বৈশিষ্ট্যগুলো বেশী কাজে এসেছে, সেগুলোই পরে প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে পরিগণিত হয়েছে – যার ফলে মূল জীবগোষ্ঠীর থেকে এরা আলাদা প্রজাতিরূপে গণ্য হয়েছে। বিবর্তনের অন্যতম অঙ্গ হল রূপান্তর বা মিউটেশন (Mutation)। এটি একটি র্যান্ডম প্রক্রিয়া। আসলে, জননের এক ধাপে DNA সজ্জা ভেঙ্গে গিয়ে এক জটিল প্রক্রিয়ায় তার প্রতিরূপ তৈরী হয়। প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন না হলে প্রতিরূপে যে ত্রুটি দেখা যায়, তাই মিউটেশনের কারণ। সমালোচকদের মতে মিউটেশনের ফলে সাধারণত বিকলাঙ্গ জীব উৎপন্ন হলেও তা বিবর্তনে কিভাবে ভূমিকা নিতে পারে। আসলে, অনেকধরণের মিউটেশন ঘটতে পারে – কিছু উপকারী, কিছু অপকারী। যেমন ধরা যাক, প্রথম যে দ্বিপদ (bipedal) ও সোজা হয়ে দাঁড়ানো মানুষ মিউটেশনের ফলে তৈরী হয়েছিল, গাছে বসবাসরত তার সমসাময়িক প্রজাতির তুলনায় তার হয়ত অসুবিধাই হত। পরবর্তীকালে, প্রকৃতিতে তার এই রূপান্তরিত বৈশিষ্ট্য তাকে বেশী ভালভাবে মানিয়ে নিতে সাহায্য করেছে। শুধু তাই নয়, প্রথম জড় থেকে জীবের সৃষ্টিও র্যান্ডম প্রক্রিয়া নয়। রাসায়নিক ধর্মের জন্যই অনু-পরমাণু নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়া করে। কার্বন পরমাণুর মধ্যে এরকম নিজেদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে বিভিন্ন আনবিক কাঠামো (Molecular structure) গঠনের ক্ষমতা আছে। প্রতিরূপ গঠনে সক্ষম একটি গঠন তৈরি হলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকৃতিতে আরো বেশীসংখ্যায় একই কাঠামো পাওয়া যাবে। প্রকৃতিতে এই ধর্ম কার্বন পরমাণুর বেশী করে আছে, তাই এটা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট নয় যে প্রাণিদেহের মূল উপাদান কার্বন, এবং শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতিরূপকও (DNA) কার্বন দিয়েই তৈরি। এই বিষয়ে মনে পড়ে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী স্টিভেন ওয়েইনবার্গের একটি তুলনার কথা। তিনি বলেন যে কেউ একজন লটারী জিতলে এরকম মনে করাটা ভুল যে কোনো দৈবপ্রভাবে সে লটারী জিতেছে। কারণ তার পাশাপাশি অসংখ্য মানুষ আছে যারা লটারীর টিকিট কেটেছিল, কিন্তু কিছুই জিততে পারেনি। সুতরাং ভাগ্যক্রমে ‘জেতা’ মানেই যে দৈবপ্রভাবে জেতা – এরকম ধারণা ভ্রান্ত। সেরকমই, পৃথিবীতে যেমন প্রাণের বিকাশ হয়েছে, তেমনই উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে পর্যবেক্ষণে আসা মহাবিশ্বের কোথাও হয়ত সেরকম বুদ্ধিমান প্রাণের সৃষ্টি হয়নি। তার কারণ পৃথিবীর মত অনুকূল পরিবেশ হয়ত কোথাও পাওয়া যায়নি।
জীবন প্রথমে কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল সৃষ্টিতাত্ত্বিকদের প্রায় সবাই মনে করেন প্রথম জীবন কোনো দৈবপ্রভাবেই শুরু হয়েছিল। তাদের দাবী, সেই কারণেই বিজ্ঞানীরা শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আজও পরীক্ষাগারে কৃত্রিম প্রাণ সৃষ্টি করতে পারেন নি, বা প্রাণ সৃষ্টির পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে পারেননি। বাস্তবে, প্রথম জীবন সৃষ্টির পরে সাড়ে তিনশো কোটি বছর পেরিয়ে গেছে, পৃথিবীর পরিবেশেও অজস্র পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে তাই জড় থেকে জীবের উৎপত্তি পরীক্ষাগারে করে দেখানো সম্ভব হয় নি। এই বিষয়ে বিশদ আলোচনার পূর্বে জেনে নেওয়া দরকার জীবনের সংজ্ঞা কি ভাবে দেওয়া হয়। অনেক জটিল সংজ্ঞার পরিবর্তে আমরা মনে করতে পারি দুটি মূল বৈশিষ্ট্যের কথা – · বহির্প্রকৃতি থেকে শক্তি আহরণের ক্ষমতা · নিজের প্রতিরূপ গঠনের ক্ষমতা বর্তমানে অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মতে প্রাথমিক জীবিত সত্ত্বাগুলো কোনো আবরণে আচ্ছাদিত কিছু প্রতিরূপ গঠনে সক্ষন প্রোটিন অনু ছিল – তা থেকেই কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের পথ ধরে আজকের বিভিন্ন জীবপ্রজাতির সৃষ্টি। এবিষয়ে প্রথম আলোকপাত ঘটে স্ট্যানলি-মিলারের বিখ্যার পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় দেখা যায়, মিথেন, অ্যামোনিয়া আর জলীয় বাষ্পের মিশ্রণে বিদ্যুতচমকের মত তড়িৎ-প্রবাহ ঘটালে অ্যামিনো অ্যাসিড ও শর্করা জাতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। আর এই দুটি উপাদানই জীবের অন্যতম গঠনমূলক উপাদান। আদি পৃথিবীতে যেহেতু পরীক্ষায় ব্যবহৃত উপাদানগুলোর কোনো অভাব ছিল না, এবং উদ্ভূত উপাদানের কোনো গ্রাহক ছিল না, তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে এই অ্যামিনো অ্যাসিড ও শর্করা রাসায়নিক মিশ্র-তরলের (Chemical Soup) আকারে পৃথিবীতে অবস্থান করত। আরেকটি পরীক্ষায় দেখানো গেছে যে একই পরিবেশে এই উপাদানগুলো নিজেদের মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে সক্ষম। খুবসম্ভব এই ধরণের শৃঙ্খলাবদ্ধ যৌগই রাসায়নিক মিশ্রণের মধ্যে প্রথম জীবনের ছাঁচ তৈরি করেছিল। সাম্প্রতিককালে আরো কিছু পরীক্ষায় দেখানো গেছে যে এই শৃঙ্খলাবদ্ধ অ্যামিনো অ্যাসিড (short chains of RNA) কোনো উৎসেচকের অনুপস্থিতিতেও প্রতিরূপ গঠনে সক্ষম। সঠিক মাত্রায় ফ্যাটি অ্যাসিডের উপস্থিতিতে RNA –এর মত শৃঙ্খলাবদ্ধ অ্যামিনো অ্যাসিডের স্বতঃ সমাবেশ ঘটে। ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে আবরক সৃষ্টি হয়, আর তার মধ্যে থাকে RNA অনু – একরকম RNA ভাইরাস বলা যেতে পারে একে। সুতরাং পদ্ধতিগত মতপার্থক্য থাকলেও বিজ্ঞানীমহলে এটা এখন স্বীকৃত যে জড় থেকেই প্রথম জীবনের সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হয় অজৈবজনি (Abiogenesis)। অজৈবজনির আরো কয়েকটি মতবাদ আছে যা আমি বিস্তৃত আকারে আলোচনা করলাম না।
তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র (Second Law of Thermodynamics) তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে, পদার্থের অন্যতম প্রবণতা হল বেশী বিশৃঙ্খল অবস্থার দিকে যাওয়া – যাকে তাপগতিবিদ্যার ভাষায় বলে ‘ইনক্রিস ইন এনট্রপি’ (Increase in Entropy)। সমালোচকদের মতে, বিবর্তনের মাধ্যমে সরল থেকে জটিল প্রাণীতে বিবর্তিত হবার অর্থ হল ক্রমাগত সুশৃঙ্খল অবস্থার দিকে যাওয়া – যা তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের পরিপন্থী। এই সমালোচনার দুই ভাবে উত্তর দেওয়া যায়। তাত্ত্বিক ভাবে বলতে গেলে, এই সূত্র কেবলমাত্র বদ্ধ (Closed) সিস্টেমের জন্যই কার্যকর। কিন্তু পৃথিবী বা জীবজগৎ কেউই বদ্ধ সিস্টেমের বাসিন্দা নয়, সূর্যের থেকে প্রতিনিয়ত শক্তি এসে পৌঁছয় – বিকিরিত হয়ে যায় কিছু শক্তি। তাই এই সূত্র জীবজগতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। শুধু তাই নয়, এই সমালোচনায় বিবর্তনকে একটি একমুখী প্রক্রিয়া বলে ধরা হয়েছে। বাস্তব কিন্তু তার বিপরীত। উদাহরণস্বরূপ, একধরণের মাছ যারা জলের তলায় গুহায় বাস করে। এই মাছেরা মূলত অন্ধ, যদিও তার পূর্বজরা যথেষ্ট জটিল চোখের অধিকারী ছিল। কিন্তু, অন্ধকার গুহায় চোখের উপস্থিতি কোনো সুবিধা দেয়না বলে নির্বাচনের ফলে এখন প্রজাতিগত ভাবে এরা অন্ধ হয়ে গেছে। বিবর্তন বহুমুখী হলেও প্রকৃতি সবসময় তাকেই নির্বাচন করেছে যার খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা বেশী। তাই, সাধারণত জটিল থেকে সরল প্রাণীতে বিবর্তিত হলেও সে নির্বাচিত না হওয়ায় বংশবিস্তার করতে পারেনি।
ক্যাম্ব্রিয়ান স্ফীতি (Cambrian Explosion) আজ থেকে ৫৪০ মিলিয়ন বছর আগে, ক্যাম্ব্রিয়ান যুগে খুব দ্রুত সরল থেকে জটিল জীবের উৎপত্তি ঘটে। ফসিল রেকর্ড অনুসারে এইসময়ে অসংখ্য বহুকোষী জীবের উদ্ভব ঘটে, যেমন – কোরাল, মোলাস্ক (শামুক জাতীয়), অ্যানথ্রপড(সামুদ্রিক আরশোলা)। পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি হয় ৩.৫ বিলিয়ন বছর আগে। তার এত বছর পরে কিভাবে হটাৎ করে পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার হল – এই বিষয়ে সমালোচকেরা প্রশ্ন তোলেন। সৃষ্টিতাত্ত্বিকরা মনে করেন, কোনো দৈব প্রভাব ছাড়া এই ঘটনা ঘটা সম্ভব নয়। তারা এমনকি এও দাবী করেন যে পৃথিবীর সব বিশিষ্ট প্রজাতি এই সময়েই আবির্ভূত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা দুভাবে এই ক্যাম্ব্রিয়ান স্ফীতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রথমত, ৫৪০ মিলিয়ন বছরেরও পুরোনো জীবাশ্ম পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। তার মধ্যে থেকে অনেক বহুকোষী জীবাশ্মগুলো থেকে প্রমাণিত হচ্ছে তারাই ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের জটিল জীবগুলোর পূর্বপুরুষ। দ্বিতীয়ত, ফসিল রেকর্ডে কোথাও সরলতর জীবের উৎপত্তি জটিলতর জীবের আগে ঘটেছে বলে পাওয়া যায়নি। শুধু তাই নয়, সমসাময়িক পরিবেশের সাথে উপযোগী করে তোলার জন্য যা বিবর্তন প্রয়োজন সবই জীবাশ্মের মধ্যে দেখা গেছে। তাত্ত্বিকভাবে, এই ঘটনা ব্যাখ্যা করা যায় বিরামযুক্ত বিবর্তনের (Punctuated Equilibrium) তত্ত্বের সাহায্যে। স্টেফান গাল্ডের এই তত্ত্ব অনুসারে বিবর্তন একটি বিরামযুক্ত প্রক্রিয়া, এর ফলে পৃথিবীতে দীর্ঘদিনের স্থিতিশীলতার পরে স্বল্প সময়ে দ্রুত বিবর্তনের ঘটনা দেখা গেছে। পরিবেশের আকস্মিক পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর মূল কারণ। ক্যাম্ব্রিয়ান স্ফীতির মূল চালিকাশক্তি ছিল বাতাসে অতিরিক্ত অক্সিজেন, যা জীবের বিকাশের অনুকূল। আজও কম অক্সিজেনযুক্ত পরিবেশে বেঁচে থাকা প্রজাতির সংখ্যা খুবই কম।
অপরিবর্তনশীল জীবদেহ সমালোচকদের মতে কাঁকড়া বা আরশোলার মত প্রাণী বহু বছর ধরে অপরিবর্তনশীল রয়ে গেছে, যা বিবর্তন তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়না। বিজ্ঞানীরা তাত্ত্বিক ভাবে বা উদাহরণের সাহায্যে এর উত্তর দিয়ে থাকেন। প্রথমত, পারিপার্শ্বিক পরিবেশের পরিবর্তন না হলে বা জীবের দেহে পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মত ক্ষমতা বিদ্যমান থাকলে জীব প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তিত হবে না, কারণ এক জীব অন্য জীবের তুলনায় বেশী সুবিধা পাবে না। পৃথিবীতে এরকম অনেক অংশে পরিবেশ বহু কোটি বছর ধরে একইরকম রয়েছে, সেই অংশে বসবাসরত জীবগোষ্ঠীর মধ্যে তাই পরিবর্তনও দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত, বিবর্তনের মাধ্যমে জীবের সব বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটবে তার তো কোনো মানে নেই, দেহের বাহ্যিক পরিবর্তন না হলেও আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে থাকতেই পারে। আরশোলা বা কাঁকড়াও বিবর্তিত হয়েছে, যদিও বাহ্যিকভাবে তার কোনো পরিবর্তন হয় নি। আরশোলার ৪০০০ প্রজাতি তৈরি হয়েছে বিবর্তনের মাধ্যমে। কাঁকড়ারও ইমিউন সিস্টেম (Immune system) আদি কাঁকড়ার একই সিস্টেমের থেকে যথেষ্টই আলাদা।
অন্তর্বর্তী জীবাশ্ম (Transitional Fossil) পর্যাপ্ত সংখ্যক অন্তর্বর্তী জীবাশ্মের অভাব বিবর্তনের বিরুদ্ধে সমালোচকদের অন্যতম অভিযোগ। এই অভিযোগের মূলে আছে অন্তর্বর্তী জীব বা জীবাশ্ম সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা। সৃষ্টিতাত্ত্বিকরা দাবি করেন, কোনো প্রধান জীববৈশিষ্ট্যই অর্ধপূর্ণ অবস্থায় প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, দুটি প্রজাতির মধ্যবর্তী জীবের অস্তিত্ত্বও খুবই কম। বাস্তবে, বিবর্তনে আমরা সবাই অন্তর্বর্তী – নিজের বৈশিষ্ট্য কমবেশি পরের প্রজন্ম কে দিয়ে চলব। সত্যিকারের এক প্রাণী থেকে আরেক প্রাণীকে আলাদা করার কোনো পদ্ধতি জানা নেই। সাধারণভাবে এক প্রজাতি আরেক প্রজাতির সাথে প্রজনন করেনা, এই ভিত্তিতে বিজ্ঞানে প্রজাতিভেদ তৈরি করা হয়। আমাদের ধারণায় বিভিন্ন জীবের মধ্যে পার্থক্য এত প্রকট, যে আমরা এরা একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত বলে ধারণাই করতে পারিনা। তাই, এই শ্রেণীবিভাগ মানুষের আরোপিত, প্রকৃতি একে মেনে চলে না। আর্কিওপ্টেরিক্সকে উড়তে দেখলে আমরা মনে করে নিই যে তা পাখির আরেক প্রজাতি, কিন্তু আসলে তার যে সরীসৃপের মত শারীরিক বৈশিষ্ট্য আছে, তা বিশ্লেষণ না করলে বোঝা যায় না। এ সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা অসংখ্য অন্তর্বর্তী জীবাশ্ম পেয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ীর বিবর্তনের পথে ১৬ ধরনের স্বীকৃত অন্তর্বর্তী জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। পৃথিবীতে যত জীব বিচরণ করে গেছে, তাদের খুব অল্পসংখ্যকেরই জীবাশ্ম পাওয়া সম্ভব, কারণ জীবাশ্ম ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশে (যেমন অগ্ন্যুৎপাতের ফলে প্রাপ্ত লাভাস্তরে) গঠিত হয়। তার মধ্যেও এতধরণের জীবাশ্মের আবিষ্কার নির্দ্বিধায় বিবর্তনের ভিত্তিকেই সুদৃঢ় করেছে।
বয়স নির্ধারণ পদ্ধতি ও পৃথিবীর বয়স বিজ্ঞানে কার্বন ডেটিং (Carbon Dating) পদ্ধতি অতিপ্রাচীন বস্তুর বয়স নির্ধারণের স্বীকৃত পদ্ধতি। কার্বনের আইসোটোপের (Isotope) তেজস্ক্রিয়-ক্ষয়ের (Radioactive decay) হার সুষম ধরে নিলে তার অর্ধজীবনকাল (Half-life) ৫৭৩০ বছর হয়। জীবিতাবস্থা জীব পরিবেশের সাথে কার্বন বিনিময় করে। মৃত্যুর পরে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ শুধু ক্ষয়িত হয়, আর সেই ক্ষয়ের হার সুষম। তাই, বস্তুতে তেজস্ক্রিয় কার্বনের অনুপাত থেকে তার বয়স নির্ধারণ করা যায়। একইভাবে ইউরেনিয়াম-লেড অনুপাত থেকেও বয়স নির্ধারণ সম্ভব। এই পদ্ধতি অনুসারে পৃথিবীর বয়স ৪.৫ বিলিয়ন বছর এবং এটাই বিজ্ঞানীমহলে স্বীকৃত। সৃষ্টিতাত্ত্বিকদের মতে তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের সুষম হার একটি অনুমান মাত্র। এই হার প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনকালে অনেক বেশী ছিল। তারা এই মতের স্বপক্ষে বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর পরীক্ষার কথাও বলেন। সৃষ্টিতাত্ত্বিকদের এই দাবীর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়না। উপরন্তু, বিজ্ঞানীরাই ইউরেনিয়াম-থোরিয়াম অনুপাত থেকেও পরীক্ষা করেও একই বয়স বের করে প্রমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন। সূর্যের ভর-ঔজ্জ্বল্যের তুলনা থেকেও বোঝা গেছে যে সৌরজগতের বয়স তেজস্ক্রিয় বয়সের কাছাকাছি।
হ্রাস-অযোগ্য জটিল জীববৈশিষ্ট্য (Irreducible Complexity) মাইকেল বিহে, তার ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত বই ‘ডারউইন্স ব্ল্যাকবক্স’(Darwin’s Black Box)-এ দাবী করেন যে জীবজগতে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলোর সরলীকরণ সম্ভব নয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলো কিছু সাধারণ অঙ্গের সামঞ্জস্যপূর্ণ সংযুক্তির ফলে কার্যকরী, যাদের যে কোনো একটিকে তাদের মধ্যে থেকে সরিয়ে নিলে তার কার্যকারিতা শেষ হয়ে যায়। তার এই দাবির পরোক্ষ ইঙ্গিত হল, কোনো দৈব প্রভাব ছাড়া শুধুমাত্র বিবর্তনের মাধ্যমে এধরণের বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ তিনি দেখিয়েছেন ব্যাক্টেরিয়ার ফ্ল্যাজেলা (flagella), একটি শুঁড়ের মত অঙ্গ, যা ব্যাক্টেরিয়াকে তরলের মধ্যে চলাফেরা করতে সাহায্য করে। তার দাবিমতে, ফ্ল্যাজেলা মূলত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত – একটি রোটর, একটি মোটর এবং একটি প্যাডল - আর এই সম্পূর্ণ সিস্টেমটির সরলীকরণ সম্ভব নয়। কিন্তু একটু গভীরে দেখলে বোঝা যায় ফ্ল্যাজেলার তিনটি অংশই নিজেরা কিছু প্রোটিন দিয়ে তৈরী। আর ফ্ল্যাজেলার প্রধান ৪২টি প্রোটিন উপাদানের মধ্যে ৪০টিই অন্যান্য ফ্ল্যাজেলাহীন ব্যাক্টেরিয়ার মধ্যেও উপস্থিত। তাই, ফ্ল্যাজেলাকে খুব সহজেই বিভিন্ন প্রোটিনের সংযুক্তির ফলে উদ্ভূত অঙ্গ বলে মনে করা যায়। ফ্ল্যাজেলা আসলে যথেষ্ট জটিল একটি অঙ্গ, প্রকৃতিতে ব্যাক্টেরিয়ার মধ্যে এর পূর্ববর্তী সরলতর অঙ্গ দেখা যায় – তার নাম টাইপ থ্রী সিক্রেসন সিস্টেম (Type III Secretion System)। এটি একটি সরু টিউবের মত অঙ্গ, যা ব্যাক্টেরিয়াকে প্রোটিন বা আয়ন বিনিময়ে সাহায্য করে। বিবর্তনের দৃষ্টিতে দেখলে, ফ্ল্যাজেলার বিবর্তনের ধাপগুলো খুব সহজেই চিহ্নিত করা যায়। ব্যাক্টেরিয়ার যেকোনো প্রবর্ধক তাকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ওপর বেশি নিয়ন্ত্রণ রাখতে সাহায্য করবে, প্রবর্ধকের আন্দোলন বেশি খাদ্যসংগ্রহে সাহা্য্য করবে। প্রবর্ধকের সাথে রোটর ও মোটর যুক্ত হলে তা সাঁতার কাটার উপযোগী হয়। আর প্রাকৃতিক নির্বাচন অনুসারে, বেশী সুবিধার কারণে বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবের বেশী হারে বংশবৃদ্ধি ঘটবে। বিহের হ্রাস-অযোগ্য জটিলতা তত্ত্বমতে, রোটর ও মোটর ছাড়া প্রকৃতিতে ফ্ল্যাজেলা-জাতীয় অঙ্গ কার্যকর হবেনা। কিন্তু জীবাণুরা বিহের কথা শুনে চলতে অভ্যস্ত নয়। তাই একধরণের অ্যামিবা (Raphidiophrys pallida) শুধু সিলিকা-নির্মিত প্রবর্ধক ব্যবহার করে চলাফেরা করতে বা শিকার করতে পারদর্শী হয়ে উঠেছে – ঠিক যেমনটা বিবর্তন তত্ত্ব অনুসারে হওয়া উচিত। একইভাবে, বিহের আরো কয়েকটি জটিলতার উদাহরণও (ইমিউনিটি, রক্ত-জমাট বাঁধার পদ্ধতি) বিজ্ঞানীরা অসার প্রমাণিত করেছেন। কেন মিলার, তার ২০০০ সালে প্রকাশিত বই ‘ফাইন্ডিং ডারউইন্স গড’ বইতে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।
সর্বজনীন জেনেটিক কোড সৃষ্টিতাত্ত্বিকদের একটি বড় অংশের ধারণা পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য এত সরল প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হতে পারেনা। বাস্তবে, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত জীব আবিষ্কৃত হয়েছে, সরল বা জটিল, সকলেই কোষযুক্ত। এককোষী বা বহুকোষী সব প্রাণীর কোষই নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় কোষে প্রোটিন উৎপাদন করে ও বংশগতি বহন করে। কোষে অবস্থিত ক্রোমোজোম গঠিত হয় DNA অনুর শৃঙ্খলা দিয়ে। জেনেটিক কোড হল একদল নিয়ম যা মেনে জীবকোষ এই DNA বা RNA শৃঙ্খলায় আবদ্ধ সংকেতকে প্রোটিন গঠনের সময় ব্যবহার করে। অন্যভাবে বলা যায়, প্রতিটি প্রোটিনের মূল উপাদান অ্যামিনো অ্যাসিড যে নীতি মেনে DNA শৃঙ্খলা থেকে গঠিত হয়, তাকেই জেনেটিক কোড বলে। এই কোড সকল জীবদেহে একই ভাবে কাজ করে। জীবকোষ গঠনের একাধিক সম্ভাব্য পদ্ধতির মধ্যে এই একমাত্র পদ্ধতিই কেন সারা পৃথিবীতে সর্বজনীন? কেন বিভিন্ন জীব বিভিন্ন উপায়ে কোষে প্রোটিন উৎপাদন করে না? কারণ হল আমরা সবাই একই পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভূত। আদি পৃথিবীর পরিবেশ ও উপাদান সমূহ এই প্রক্রিয়ার পক্ষে উপযুক্ত ছিল, তাই অন্য সবকিছু বিবর্তিত হলেও এই একটিমাত্র পদ্ধতিই সকল জীবদেহে স্থান করে নিয়েছে। আর প্রজনেনের মাধ্যমে এক জীব থেকে আরেক জীবে তা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সকল জীব তৈরি করে থাকলে তাদের মধ্যে গঠনগত বৈচিত্র্যের এত অভাব হত কি?
সুপরিকল্পিত সৃষ্টিতত্ত্ব না পরিকল্পনার অভাব? সৃষ্টিতাত্ত্বিকরা অনেকসময়েই যুক্তি দিয়ে থাকেন যে সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর না হলে এত নিখুঁতভাবে এত জটিল থেকে জটিলতর জীবদেহ গঠিত হত না। শুধু তাই নয়, ঈশ্বর সকলকে নিজ নিজ পরিবেশে বেঁচে থাকার মত উপযোগী করে গড়ে তুলেছেন, এবং তাদের প্রতিটি অঙ্গ কোনো না কোনো ভাবে কার্যকর। কিন্তু এই নিখুঁত গঠন কতটা নিখুঁত? মানুষের শারীরিক গঠন পর্যবেক্ষণ করলে বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় অঙ্গের অস্তিত্ত্ব পাওয়া যায়। যেমন অ্যাপেন্ডিক্স। এই অঙ্গগুলো কোনো কাজে আসেনা, অথচ সব মানুষের শরীরেই উপস্থিত। উপরন্তু, ক্ষেত্রবিশেষে অসুবিধার সৃষ্টি করে। নিখুঁত গঠন হলে যে এরকম কোনো অঙ্গের কোনো অস্ত্বিত্ব থাকত না মানবদেহে, তা বলাই বাহুল্য। সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী যে ভ্রূণাবস্থায় সরল থেকে জটিল প্রাণীর আকারে পরিবর্তিত হয় সেটা কিভাবে নিখুঁত হতে পারে? সাময়িকভাবে মাছের মত কানকো বা বানরের মত লেজ থাকে মানবভ্রূণের – কিন্তু এর কার্যকারিতা কোথায়? উত্তরটা স্বাভাবিক, বিবর্তনের পথে ঐ সব প্রাণী মানুষের পূর্বপুরুষ, তাদের বৈশিষ্ট্য মানুষ ভ্রূণাবস্থায় বহন করে। কিন্তু নিখুঁত পরিকল্পনার তত্ত্বে এর কোনো ব্যাখ্যা নেই।
ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপাতদৃষ্টিতে বিবর্তন ‘বলে মনে হয়’ সবথেকে ভিত্তিহীন যুক্তিগুলোর মধ্যে একটা হল ঈশ্বর এমনভাবেই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যাতে আমাদের মনে হয় পৃথিবী অনেক পুরোনো এবং জীবজগৎ বিবর্তিত হয়েছে। এই শ্রেণীর মানুষ আসলে দুই নৌকায় পা রেখে চলার একটা শেষ চেষ্টা করেন। এদের সম্পর্কে বক্তব্য রাখাও অসম্ভব।
বিকল্পের অভাবজনিত সৃষ্টিকর্তা উপরোক্ত আলোচনা থেকে একটা বিষয় সুস্পষ্ট হয়, যে সৃষ্টিতাত্ত্বিকরা সৃষ্টিকর্তার পরিবর্তে বিজ্ঞানের আবিষ্কারে ফাঁক খুঁজে বের করতেই ব্যস্ত। যুক্তিটা এরকম, যদি সমসাময়িক বিজ্ঞানের সাহায্যে বিষয়টির ব্যাখ্যা না করা যায়, তার মানে ধরে নিতেই হবে যে তা সৃষ্টিকর্তার অবদান ছাড়া কিছুই নয়। এর আদর্শ উদাহরণ হল সৃষ্টিতাত্ত্বিক দার্শনিক উইলিয়াম ডেম্বস্কির ‘ডিজাইন ফিল্টার’। এই তত্ত্ব মতে, প্রথমত যেকোনো জটিল বস্তু বা প্রাকৃতিক বিষয়কে প্রথমে প্রাকৃতিক সূত্রগুলো দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে। যদি সম্ভব না হয়, তাহলে দেখতে হবে বিষয়টি ঘটনাচক্রে ঘটে থাকতে পারে কিনা। যদি সে সম্ভাবনাও কম হয়, তাহলে ধরে নেওয়া স্বাভাবিক যে বিষয়টির পেছনে কোনো বুদ্ধিমান শক্তির গূঢ় পরিকল্পনা কাজ করছে। এরকম তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক কোনো ভিত্তি নেই। যেসমস্ত বিষয়ের কোনো ব্যাখ্যা নেই, বা প্রচলিত ব্যাখ্যায় যথেষ্ট ত্রুটি আছে, বিজ্ঞানের অন্যতম উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক বা প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দিয়েই সেই ফাঁকগুলো পূরণ করে মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট করা – যাতে প্রকৃতিকে মানুষ আরো বেশী করে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাই আজকের মানুষের ধারণা কালকে পরিবর্তন হতেই পারে। যদি কোনো বুদ্ধিমান শক্তির উপস্থিতি ধরেই নেওয়া হয়, তাহলে সেই বিষয়ে অনুসন্ধিৎসার অভাব দেখা যেতে পারে। আর এই অনুমানের সাহায্যে কি মূল ব্যাখ্যায় পৌঁছনো যাবে? কোনোভাবেই না।
অকামস রেজর অনুমানের কথা বলতে চলে আসে অকামস রেজরের কথা। চতুর্দশ শতকের ইংরেজ তর্কশাস্ত্রবিদ উইলিয়াম অব অকাম। তার বক্তব্য ছিল যেকোনো প্রাকৃতিক বিষয়ের ব্যাখ্যা ন্যূনতম সংখ্যক অনুমানের ভিত্তিতে দেওয়া উচিত। অন্যভাবে বললে – “সরলতম (ন্যূনতম সংখ্যক অনুমানের ভিত্তিতে) সমাধানই সর্বোত্তম সমাধান।” এই তত্ত্ব বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্বের ওপর প্রয়োগ করা যেতে পারে, কারণ এরা দুটি প্রতিযোগী তত্ত্ব, যারা একই প্রাকৃতিক বিষয়ের ব্যাখ্যা দেয়। বিবর্তনবাদের ক্ষেত্রে কোনো অনুমানই করতে হয়না, কারণ এই তত্ত্ব প্রাকৃতিক বিষয়কে দৃশ্যমান প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাব দিয়ে ব্যাখ্যা করে। অন্যদিকে সৃষ্টিতত্ত্ব শুরুতেই অদৃশ্য মহাশক্তিমানের অস্তিত্ব অনুমান করে নেয়। সুতরাং, সহজেই বোধগম্য যে বিজ্ঞানে বিবর্তনবাদই স্বীকৃত হবে।
সত্যের সন্ধানে বিজ্ঞান বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্বের পার্থক্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডগলাস ফুতুয়ামা বলেছেন –
বিজ্ঞান ও সৃষ্টিতত্ত্বের মূল পার্থক্য হল পদ্ধতিগত। বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত সত্যের সন্ধান করে, আর অপরদিকে সৃষ্টিতত্ত্ব বিভিন্ন ধর্মীয় লোকগাঁথা, উপকথাগুলোকে "ধ্রুব সত্য" ভেবে নিয়ে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সন্ধান করে। প্রকৃত বিজ্ঞানীরা নিজেদেরকে নিউটনের "জ্ঞানের বালুকাবেলায় ছোট নুঁড়ি কুরানোর" মত সত্যসন্ধানী মনে করে আর প্রমাণের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় আর সৃষ্টিতত্ত্বের ধারকেরা ইতিমধ্যেই (ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে) সত্য পেয়ে যাওয়া "সবজান্তা শমশের" ভেবে নিয়ে সেই সত্যের নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করেন। বিজ্ঞানের এই পদ্ধতি সময়-পরীক্ষিত, সত্য সন্ধানে এর তুলনা নেই। কোনো সময়ে মানুষ সমতল পৃথিবীর উপলব্ধিতে নিমজ্জিত ছিল, তখন বিজ্ঞানীরাই মানুষকে তা থেকে মুক্ত করেছেন। এখন আর কেউ সমতল পৃথিবীর কল্পনায় বিভ্রান্ত হয় না। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ক্রমাগত প্রমাণ ও পরীক্ষার সাহায্যে বিবর্তনবাদও জনমানসে একই ভাবে স্থান করে নেবে।
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
