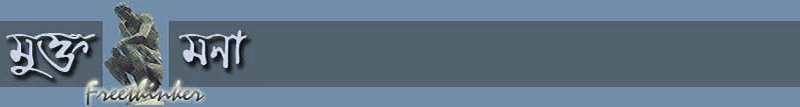
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
|
অসম্ভবের বিজ্ঞান
-‘এনার্জাইস’! গাঢ় স্বরে উচ্চারণ করলেন ক্যাপ্টেইন কার্ক।
স্পেশশিপের মাঝামাঝি এলাকায় মেঝের মধ্যে গোলাকার চাকতি আঁকা জায়গাটায় এসে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন কার্ক।
ধাতব এক ধরনের ভোতা যান্ত্রিক গুঞ্জন উঠল চারিদিকে। লেজার রশ্মির তীব্র আলোয় ঢেকে গেল গোলাকার অংশটুকু। আলোর তীব্র ঝলকানিতে ঢাকা পড়ে গেল কার্কের দেহ। এর মধ্যে ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসছে কার্কের অবয়ব স্পেশশিপপের অন্যান্য অভিযাত্রীদের কাছে। সারা কক্ষ জুরে ধাতব গুঞ্জন বাড়তে লাগলো। ফিকে হতে হতে স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে কার্কের শরীর; একসময় শূন্যে মিলিয়ে গেল কার্কের পুরো দেহটা। সাথে সাথে ধাতব শব্দ থেমে গেলো। থেমে গেলো আলোর ঝলকানিও। গোলাকার শূন্য জায়গাটায় এখন কেবল নিঃসীম স্তব্ধতা। ... প্রায় ছয় আলোকবর্ষ দূরের এক পাথুরে নিষ্প্রাণ গ্রহে অবতরণ করলেন কার্ক ...
ছবি: স্টারট্রেকের টেলিপোর্টেশন - আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণার অনুপ্রেরণা স্টারট্রেকের এ ধরনের অসংখ্য দৃশ্যের সাথে দর্শকেরা নিশ্চয় কমবেশি পরিচিত। এই অদ্ভুতুরে মামদোবাজির পেছনের তত্ত্বটা আসলে আহামরি জটিল কিছু নয়। একটা দেহকে অণু-পরমাণুতে ভেঙে ফেলে নিমেষ মধ্যে দূরবর্তী জায়গায় প্রেরণ করে দেহকে আবার ঠিক ঠাক মত জোড়া লাগিয়ে দেওয়া। বিজ্ঞানের ভাষায় এর একটা গালভরা নাম আছে – ‘টেলিপোর্টেশন’।
মজার ব্যাপার হচ্ছে স্টারট্রেকের অভিযাত্রীরা সবসময় যে টেলিপোর্টেশনকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন তা কিন্তু হলফ করে বলা যাবে না। ‘এনিমি উইদিন’ নামের একটা এপিসোডে কার্ক নিজেকে টেলিপোর্ট করতে গিয়ে ভয়ানক ভ্যারা চ্যারা লাগিয়ে দেন। টেলিপোর্ট করার পর দেখা গেল কার্কের দেহ বিভক্ত হয়ে দুটো কার্কে পরিণত হয়ে গিয়েছে। এক কার্ক ভালমানুষ আর অন্য কার্ক মহাশয়তান। এই মহাশয়তান কার্ক সারা স্পেশশিপ জুড়ে শুরু করলো নানা তেলেসমাতি কাজ কারবার। শেষ পর্যন্ত যথারীতি সিনেমার ম্যানুফ্যাকচারিং অনুযায়ী - ‘ভাল কার্ক’ ওই ‘শয়তান কার্ক’ কে পরাস্ত করে স্পেশশিপে শান্তি আনয়ন করলেন। মধুরেণ সমাপয়েৎ।
কিন্তু স্টারট্রেক তো হাজার হলেও আমুদে দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য বানানো কাল্পনিক সিনেমা। সেখানে হাজারটা ‘গাঁজাখুড়ি’ জিনিস দেখিয়ে পার পাওয়া যায়। সেখানে যাই দেখাক না কেন, বাস্তবে টেলিপোর্টেশন করা কি আদৌ সম্ভব? ওই ভাল কার্ক আর শয়তান কার্কের কেচ্ছা-কাহিনী না হয় বাদ দেই, কিন্তু টেলিপোর্ট করে কোন কিছুকে সত্যই কি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ম্যাজিকের মত পাঠিয়ে দেয়া সম্ভব?
ছবি: স্টারট্রেকের টেলিপোর্টেশন কি শেষপর্যন্ত কল্পলোকের বাস্তবতা হতে চলেছে? বিজ্ঞানীরা আজ নিশ্চিৎ করে বলছেন – সম্ভব। অস্ট্রেলিয়ান রিসার্চ কাউন্সিলের কোয়ান্টাম- অ্যাটম অপটিক্স ল্যাবের বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি আনবিক স্কেলে সফলভাবে টেলিপোর্ট করে দেখিয়েছেন। আরেক বিজ্ঞানীর দল ফোটনকে ‘টেলিপোর্ট’ করে পাঠাতে পেরেছেন দানিয়ুব নদীর এক পাড় থেকে অন্য পাড়ে। অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন কয়েক দশকের মধ্যেই ভাইরাসের মত ‘জটিল’ অনু কিংবা আমাদের ডিএনএ টেলিপোর্ট করা সম্ভব হবে। কিন্তু স্টারট্রেকে যেরকম দেখানো হয়েছে সেরকম পূর্ণ অবয়বের টেলিপোর্ট যন্ত্র বানাতে হয়ত বিজ্ঞানীদের লেগে যাবে শ’খানেক বছর। তা লাগুক। অন্ততঃ তাত্ত্বিকভাবে যে টেলিপোর্টেশন আর ‘অসম্ভব’ কোন বিষয় না তা কিন্তু বুঝতে পারা যাচ্ছে এখনই। এই ধরণের সফল টেলিপোর্টের পেছনে যে তাত্ত্বিক ভিত্তিটি দাঁড়িয়ে আছে সেটিকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন ‘কোয়ান্টাম আঁতাঁত’ (Quantum Entanglement)। আর সে জন্যই DARPA (Defense Advanced Projects Research Agency) এখন QuEST (Quantum Entanglement Science and Technology) নামে বড় সড় এক প্রজেক্ট হাতে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি স্টারট্রেকের টেলিপোর্টেশন যন্ত্রের বাস্তব রূপায়ন ঘটানোর জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন।
শুধু টেলিপোর্টেশন নয় – স্টারট্রেক, ব্যাক টু দ্য ফিউচার, এলিয়েন, হলো ম্যান কিংবা আই রোবোটের মত ছবি দেখলেই আমার মাথায় কিল বিল করা শুরু করে হাজারটা ‘অসম্ভবের প্রশ্ন’ –
- কখনো কি সময়-পরিভ্রমণ করে আমরা অতীতে বা ভবিষ্যতে ফিরে যেতে পারব? সত্যিই কি টাইম মেশিন জাতীয় কোন কিছু আমাদের পক্ষে বানানো সম্ভব?
- অনন্ত মহাবিশ্ব বা সমান্তরাল মহাবিশ্ব কি সত্যই আছে? কোনদিন কি আমরা ওয়ার্ম হোল বানিয়ে সমান্তরাল মহাবিশ্বের বাসিন্দাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারব?
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যৎ কতটুকু? রোবটেরা কি সত্যই অদূর ভবিষ্যতে মানবতাকে পরাস্ত করে এই পৃথিবীটা অধিকার করে নেবে?
- কখনো কি ‘কোয়ান্টাম টানেলিং’-এর মত কোন প্রক্রিয়ায় আমরা দেয়াল ভেদ করে ভুতের মত এক পাশ থেকে অন্য পাশে চলে যেতে পারব?
- কখনো কি কাউকে পুরোপুরি অদৃশ্য করে দেয়া যাবে?
- কখনো কি অ্যান্টিম্যাটার দিয়ে রকেট বা স্পেশশিপ চালানো যাবে?
- কখনো কি স্টার ওয়ার্স-এর মত লেজার গান দিয়ে আন্তনাক্ষত্রিক যুদ্ধ শুরু হবে?
- কখনো কি মহাজাগতিক অধিবাসীদের সাথে আমাদের মোলাকাৎ হবে?
আমার বইয়ের শেলফ থেকে আমি মুহম্মদ জাফর ইকবালের কল্পবিজ্ঞানের পুরোন কোন বই হাতে তুলে চোখ বুলাই – যেখানে বর্ণনা পাই নিওপলিমারের জামা পড়ে পঞ্চম মাত্রার মহাহাকাশযানে বসে ইবান হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে কথা বলে মর্তবাসী প্রিয়জনের সাথে, আর নিহিলিন সেবন করে রিশা না ঘুমিয়ে থাকে রাতের পর রাত, কিংবা গ্রিশিন গ্রহ থেকে ফেরার পথে স্পেশশিপ নিয়ে হাইপারডাইভ দেয় রিতুন ক্লিশ ... সেই কৈশোরের আবেগে বারে বারেই উদ্বেলিত হয়ে উঠি নিজের অজান্তেই। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করি – এগুলো কি সত্যই সম্ভব হবে কখনো?
ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! পেশাগত কারণে কাঠখোট্টা বিজ্ঞান আর নিরস জাভা প্রোগ্রামিং নিয়ে কাজ করে গেলেও কাজ লাজ-লজ্জা বিসর্জন দিয়ে এখনো অসম্ভবের বিজ্ঞান নিয়েই চিন্তা করে যাচ্ছি শয়নে স্বপনে ...। তবে, আমার মাথায় এ ধরনের প্রশ্নের সূত্রপাত কিন্তু হলিউডের মুভি দেখে কিংবা জাফর ইকবালের বই পড়ে নয়, মাথায় এই ধরনের বিদঘুটে প্রশ্নের কিলবিলানির শুরু হয়েছিলো আরো অনেক অনেক আগে।
*** প্রশান্ত মহাসাগরের গভীর সাগরতলে নটিলাস নামের সাগর দানবে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ক্যাপ্টেন নিমো, আর মাঝে মধ্যেই লিঙ্কন দ্বীপে রবিনসন ক্রুসোর মতই আটকে পড়া সাইরাস স্মিথ আর তার দলবলকে নানা বিপদ আপদ থেকে রহস্যময়ভাবে উদ্ধার করে চলেছেন একের পর এক ...।
ছোটবেলায় যখন সেবা প্রকাশনী থেকে অনুবাদ করা জুলভার্ণের ‘রহস্যময় দ্বীপ’ (Mysterious Island) প্রথম পড়া শুরু করেছিলাম বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। শুধু ‘রহস্যময় দ্বীপ’ নয় -এখনো মনে আছে কি গোগ্রাসে গিলেছিলাম Twenty Thousand Leagues Under the Sea (সাগর তলে), Around the World in Eighty Days (আশি দিনে বিশ্বভ্রমণ), From the Earth to the Moon (চাঁদে অভিযান), -এর মত সায়েন্টিফিক ফ্যান্টাসিগুলো। আমার বিজ্ঞানের প্রতি ‘প্রেম’ শুরু হয় বোধ হয় তখন থেকেই। অবাক হয়ে ভাবতাম - কী পরিমান ধী-শক্তি আর কল্পণাপ্রবণতা থাকলে কত্ত আগেকার সময়ের একটা লোক ভবিষ্যতের বাস্তবতাকে তুলে ধরতে পারেন নিখুঁত সৌন্দর্যে এবং সৌকর্যে। তিনি যখন আঠারো শতকে তার উপন্যাসগুলো লিখেছিলেন, তখন বাসায় বাসায় বিদ্যুতের হরেক রকম ব্যবহার ছিলো না - ছিলো না এই রকম ছাঁদ ফুরে বেরুনো ঝলমলে ঝাড়বাতি, কালার টিভি, কম্পিউটার, ওয়াশিং মেশিনের কোন কিছুই। অথচ জুলভার্ণ শুধুমাত্র তার Twenty Thousand Leagues Under the Sea উপন্যাসটিতেই বৈদুতিক শক্তির এমন সমস্ত ব্যবহারিক প্রয়োগ উল্লেখ করেছিলেন তা সত্যই অবাক করার মত। তিনি তখনই দেখিয়েছিলেন বৈদুতিক বাতি আর সার্চ লাইটের ব্যবহার, তার পাশাপাশি উল্লেখ করেছিলেন বৈদুতিক ঘড়ি এবং বৈদুতিক হিটারের, কল্পণা করেছিলেন ইলেক্ট্রিক প্রপেলারের, গভীর সমুদ্রে অভিযানের জন্য তৈরি করেছিলেন ডুবুরীর পোষাকের, লিপিবদ্ধ করেছিলেন সমুদ্রের নোনা জলকে সুপেয় জলে পরিবর্তনের অত্যাধুনিক প্রক্রিয়া এবং সর্বোপরি নিঁখুতভাবে অনুমান করেছিলেন সত্তুর মিটার লম্বা চুরুট আকৃতির ডুবোজাহাজ (সাবমেরিন) নটিলাসের – যাতে সওয়ার হয়ে ক্যাপ্টেন নিমো তার যাবতীয় অতিমানবীয় কারিশমাগুলো দেখাতেন।
এরকম কত ভবিষ্যদ্বানী যে জুলভার্ণ সঠিকভাবে করেছিলেন তার অন্যান্য উপন্যাস এবং গল্পগুলোতেও, তার কোন ইয়ত্ত্বা নেই। তিনি সে সময়ই কল্পনা করেছিলেন হেলিকপ্টার, ফ্লাইং মেশিন, বহুতল ভবন, প্রজেক্টর, জুক বক্সের –যেগুলো তখনকার দিনে আক্ষরিক অর্থেই ছিলো আকাশ কুসুম কল্পণা। এমনকি এপেলো অভিযানের একশ বছরেরও আগে তিনি লিখে ফেলেছিলেন – ‘চাঁদে অভিযান’ (১৮৬৫)। অবশ্য রকেটের বদলে তিনি তার উপন্যাসে চাঁদে যাওয়ার জন্য দেগেছিলেন কামান। সেই কামানের নাম ছিলো ‘কলম্বিয়াড’। কি আশ্চর্য – এর প্রায় একশ বছর পর এপেলো-১১ মিশনের জন্য যে রকেট মার্কিন বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছিলেন – তার ‘কমান্ড মডিউলের’ নাম ছিলো কলম্বিয়া – জুলভার্ণের দেয়া নামের একদম কাছাকাছি। জুলভার্ণ হিসেব নিকেষ কষে কলম্বিয়াডের জন্য যে প্রক্ষেপণ পথ বানিয়েছিলেন সেই পথও ছিলো নাকি এপেলো ১১ এর খুবই কাছাকাছি। শুধু তাই নয়, কামান দাগার জন্য জুলভার্ণ বেছে নিয়েছিলেন ফ্লোরিডাকে। তাজ্জব ব্যাপার – প্রায় একশ বছর পর চাঁদে সত্যিকার অভিযানের জন্য নাসার রকেট উৎক্ষেপণও ঘটেছিলো শেষ পর্যন্ত ওই ফ্লোরিডা থেকেই।
আর শেষ মেষ এই পান্ডুলিপি বই আকারে বের হয় এই সেদিন - ১৯৯৪ সালে।
বইটা বেরুনোর পর সকলের তাব্দা লেগে গেল। সেই ১৮৬৩ সালেই জুলভার্ণ নিখুঁতভাবে কল্পণা করতে পেরেছিলেন - বিংশ শতাব্দীতে ‘আধুনিক’ প্যারিসের রূপ কেমন হতে পারে। তিনি উল্লেখ করেছিলেন ফ্যাক্স-মেশিনের, ক্যালকুলেটরের, কল্পণা করেছিলেন বহুতল কাঁচ-দালানের, ইলেকট্রিক চেয়ারের, গ্যাস-পরিবাহিত গাড়ির, শীততাপনিয়ন্ত্রক যন্ত্রের, টেলিভিশন এবং এমনকি ইন্টারনেটের। ১৮৬৩ সালে জুলভার্ণের জন্য যেগুলো ছিল আকাশ কুসুম ‘বৈজ্ঞানিক ফ্যান্টাসি’, আজকে সেগুলোই আমাদের জন্য সহজ সরল বাস্তবতা।
প্রিয় পাঠক, অসম্ভবের বিজ্ঞান সিরিজে স্বাগতম! অক্টোবর ১৫, ২০০৮ ২য় পর্ব পড়ুন ...
ড. অভিজিৎ রায়, মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক; ‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’ ও ‘মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' গ্রন্থের লেখক। সাম্প্রতিক প্রকাশিত সম্পাদিত গ্রন্থ – ‘স্বতন্ত্র ভাবনা’। সম্প্রতি 'বিজ্ঞান ও ধর্ম : সংঘাত নাকি সমন্বয়?' শীর্ষক গ্রন্থ সম্পাদনার কাজে নিয়োজিত। ইমেইল : [email protected] |
|
|
||||
|
|
|
|
||||||
|
|
||||||||



