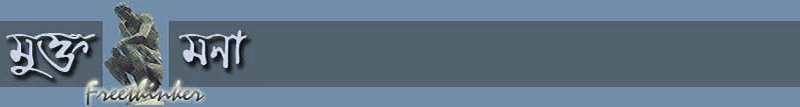
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||
|
|
|
কবে আসবে আলোকিত ঘর আবুল হোসেন খোকন (এক) প্রথম দফায় যখন জেলে যাই তখন সামরিক শাসন। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায়, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। জেলে যাওয়ার অপরাধ সামরিক শাসন নিপাত যাক বলে চিৎকার করেছিলাম, গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিতে বলেছিলাম। এটা তখন প্রধান বা সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ। এ অপরাধ মানেই রাষ্ট্রদ্রোহীতা। সুতরাং এই রাষ্ট্রদ্রোহীতায় জেলে ঢোকানো হয়েছিল একেবারে পিচ্চি বয়সে। জেলে এরকম নানান অভিযোগে বহু মানুষ ছিলেন। আমরা যে জেলখানাটিতে ছিলাম সেটি একটি জেলা শহরের জেলখানা। জেলে ক্যাপাসিটি বা ধারণ ক্ষমতা ২শ’র কিছু বেশী। কিন্তু সমর আইনের বদৌলতে এসব ধারণ ক্ষমতার ধার ধারা হয়নি। ঢোকানো হয়েছিল ৩ হাজার থেকে ৪ হাজার পর্যন্ত। গড়ে এই সংখ্যাটা থেকেছে কড়া সামরিক শাসনের সময় পর্যন্ত। কারণ চোর-ডাকাতদের ছেড়ে দেওয়া হতো, আর ঢোকানো হতো বাছ-বিচার না করে ছেড়ে দেওয়াদের চেয়ে বহুগুণে বেশী রাজনীতিক বা রাজনীতির সমর্থক ধরনের মানুষকে। নারী-শিশু-বৃদ্ধ-যুবক-তরুণ-বিকলাঙ্গ-অবিকলাঙ্গ-সামরিক-অসামরিক বলে কোন ব্যাপার ছিল না। সন্দেহ বা ইচ্ছে হওয়া মাত্রই জেলখানায় ঢোকানো। হাঁস-মুরগী-গরু-ছাগল-পেঁয়াজ-রশুন-আলু-পটলের মতো জেলখানা বোঝাই করা হয়েছে। সুতরাং ২ শ’ মানুষের জেলখানায় ৩ থেকে ৪ হাজার মানুষকে থাকতেই হয়েছে। তবে জেলখানায় একটা স্বস্তি ছিল। শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন কিংবা পুলিশের রিমান্ড ইত্যাদির ভয় ছিল। কিন্তু ফায়ারিং স্কোয়াডে প্রাণ হারাবার ভয় অনেকটাই কম ছিল। এটায় সামরিক বাহিনীর যারা আটক ছিলেন তাদের বেলায় যতোটা ভয় ছিল, বেসামরিকদের বেলায় অতোটা নয়। সে কারণে জেলখানা হয়েছিল স্বস্তির জায়গা। আসলে এ অর্থে জেলখানা যতোটা স্বস্তির জায়গা ছিল, বাইরের জায়গাটা মোটেও তা ছিল না। বাইরে তখন চলছিল কম্বিং অপারেশন নামের এ নৃশংস কিলিং মিশন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং গণতন্ত্র ও প্রগতিশীলতায় বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে চলছিল চিরুণি অনুসন্ধান। ধরা মাত্র অথবা রাতভর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে আটকে রেখে পৈশাচিক নির্যাতনের পর ভোরবেলায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মতো লাইন করে দাঁড় করিয়ে ফায়ারিং স্কোয়াড কার্যকর করা ছিল প্রতিদিনের ঘটনা। এই কিলিং মিশনকালে কারও লাশ খুঁজে পাওয়া যেতো না, যায়ওনি পরে কখনও। ফলে প্রমাণের কিছু থাকেনি, শুধু কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পৈশাচিক নির্যাতনের শিকার আলুর মোরব্বা হয়ে পড়া কিছু অবস্থানকারী ছাড়া। তাই জেলাখানায় যারা গেছেন তারা প্রাণটা রক্ষা করতে পেরেছেন। সামরিক বাহিনীর কথা এসেছে। হ্যাঁ, যারা ওই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং গণতন্ত্র ও প্রগতিশীলতায় বিশ্বাসী ছিলেন তাঁদের গণহারে আটক করা হয়েছে এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বিনাবিচারে গুলি করে হত্যা করে লাশ গুম করে দেওয়া হয়েছে। যাদের জেলে পাঠানো হয়েছিল তাদের কিছু অংশকেও কোর্টমার্শালে বিচারের নামে প্রহসন করে হত্যা করা হয়। বাকিদের দেওয়া হয় বিভিন্ন মেয়াদে সাজা। এই কোর্টমার্শাল বা গুপ্ত হত্যা, লাশগুমের ঘটনা সবচেয়ে বেশী ঘটেছে ’৭৫-এর ৭ নভেম্বরের পর। অর্থাৎ কিলিং মিশনের মাধ্যমে শুধু বেসামরিক পর্যায়ে নয়, সামরিক পর্যায়েও নৃশংস-বর্বর শুদ্ধি অভিযান চালানো হয়েছে যাতে কোথা থেকেও কখনও কেউ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, গণতন্ত্র এবং প্রগতির কথা তুলতে না পারে। দ্বিতীয় দফার জেল জীবন হয়েছে যাবার এই জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনের সময়ই। তবে প্রথমবারেরটা ছিল সামরিক শাসনের শুরুর দিক, আর দ্বিতীয়বারেরটা শেষ পর্বে। এই পর্বে মানুষ মেশিনগান উপক্ষো করে জেগে উঠছিল। তীব্র জনঅসন্তোষে সামরিক শাসনের টলটলমান অবস্থা। তখন আর সমর শাসনের বেসামরিক লেবাস না নিয়ে উপায় ছিল না। দুইদফার জেল জীবনকালে ওই জেলখানাটিতে ছিলেন ডান-বাম অনেক পরিচিত রাজনৈতিক নেতা। অবশ্য যুদ্ধাপরাধী-রাজাকার-আলবদর-জামাত-শিবিরের কাউকে জেলে যেতে হয়নি, তাদের কেও ছিলও না। এই জেলখানায় ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপরিচিতি এবং বর্তমান সরকারের হাতে আটক হওয়া শিক্ষক (কর্নেল তাহেরের ভাই) অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, ৭ নভেম্বর অভ্যুত্থান প্রচেষ্টায় জড়িত কর্নেল তাহেরের সঙ্গী নায়েক সিদ্দিকুর রহমান, বিমান বাহিনীর কর্পোরাল শামসুল হক, সিপিবি নেতা কমরেড প্রসাদ রায় ও শামসুজ্জামান সেলিম, মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী অন্যতম রাজনীতিক ও ’৭৫-এর ৩ নভেম্বরে জেলখানায় নিহত ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর পুত্র মোহাম্মদ নাসিম, আওয়ামী লীগ নেতা অধ্যক্ষ আবদুল গনি, মোজাম্মেল হক সমাজী, জাসদ নেতা আব্দুল লতিফ মির্জা, বাম নেতা প্রবীর নিয়োগী, শ্রমিক লীগ নেতা ফজলুল হক মণ্টু, কবি মোহন রায়হানসহ অনেকে। নানা কারণেই এঁরা সবাই ছিলেন আমার ঘনিষ্ট। (দুই) আমাদের সময়েও জেলখানাকে বলা হতো রাজনীতির পাঠশালা। বলা হতো এই জেলখানা থেকে যে রাজনীতি, শোষণ-শাসন, অনিয়ম-দুর্নীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতিসহ যা কিছু শিখতে পারবোÑ তাই-ই কাজে লাগবে। কারণ জেলখানা হলো একটি ছোট রাষ্ট্র, আর জেলখানার বাইরেটা বড় রাষ্ট্র। জেলে যা হয়, বাইরে তা-ই বড় করে হয়। সুতরাং জেলখানা বুঝতে পারলে দেশটাকে বুঝতে পারবো, দেশের পুরো শাসনযন্ত্রটা এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন সমস্ত কিছুকে বুঝতে পারবো। সে কারণেই রাজনীতির জন্য জেলখানা হলো পাঠশালা। আমরা যারা দেশ নিয়ে, মানুষ নিয়ে, মানুষের মুক্তি এবং অধিকার নিয়ে ভাবতাম তারা পাঠশালা হিসেবেই দেখেছি জেলখানাকে। আর এরসঙ্গে যার যার আদর্শ নিয়ে রাজনীতিও করেছি। জেলখানার কঠোর নজরদারি, বাধা-বিপত্তি, কেসটেবিলে বিচার, ডাণ্ডাবেরী-হ্যান্ডকাপ, সারাদিন ফাইল করিয়ে বসিয়ে রাখা, ডাণ্ডাপেটা করা, গাছে ঠ্যাং ঝুলিয়ে লাঠিপেটা করা, গরম পানি ঢালা, পিটিয়ে ক্ষতস্থানে মরিচের গুড়ো মাখিয়ে দেওয়া, মলদারে সেদ্ধ ডিম ঢুকিয়ে নির্যাতন করা, সেলে আটকে রাখাসহ কতো রকম বর্বরতা চলেছে কিন্তু আমাদের কারও কাজ ঠেকানো যায়নি। বরং যতো নির্যাতন হয়েছে জুলুম হয়েছে ততো আমাদের কাজের কৌশল ও গতি বেড়েছে। বেড়েছে সংঘবদ্ধতা। আমি বেশীরভাগটাই সেলে কাটিয়েছি। পাশের সেলে ছিলেন সিপিবি নেতা শামসুজ্জামান সেলিম। দু’জনে আমরা রাজনীতি নিয়ে শেয়ার করেছি। কমরেড প্রসাদ রায় থাকতেন ডিভিশনে। তারসঙ্গে শেয়ার করেছি। আরও যাদের নাম উল্লেখ করেছি তাঁদের সঙ্গেও শেয়ার করেছি। বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী হলেও আমাদের মধ্যে দারুণ একটা ঐক্য গড়ে উঠেছিল, যা জেলখানার রাজনৈতিক ঐক্যকে একসময় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী করে তুলেছিল। আমাদের ঐক্যটা কোন্ পর্যায়ে ছিল তা একটা উদাহরণ দিলে ধারণা মিলতে পারে। আমি এবং আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ নাসিমের মধ্যে তখন রাজনৈতিক আদর্শগত বিরোধটা ছিল তুঙ্গে, সাপে-নেউলের মতো। জেলখানার বাইরে এর প্রতিফলন ঘটে চলেছিল অবিরাম। অথচ মজার ব্যাপার হলো এই মোহাম্মদ নাসিমের হাত দিয়েই জেলখানায় আদান-প্রদান করিয়েছি ‘গণবাহিনীর’ কাগজপত্র, গোপন চিঠি, দালিলিকভাবে গোপন নানা খবর। তিনি প্রথম শ্রেণীর মর্যাদাপ্রাপ্ত বন্দি ছিলেন। তাই কোর্টে নেওয়ার সময় তাঁকে সার্চ করা হতো না। এই সুযোগটা কাজে লাগাতে জেলখানা থেকে চিঠি-দলিলপত্র-তথ্য প্যাকেট করে তার হাতে তুলে দিয়েছি। তিনি সেটা লুকিয়ে নিয়ে কোর্টে গেছেন। তারপর আমাদের লোক এসেছে এবং তিনি তা তার হাতে তুলে দিয়েছেন। আবার নাসিম ভাই যখন কোর্ট থেকে জেলে ফিরবেন, তখন বাইরের তথ্য সম্বলিত প্যাকেট তাঁর হাতে পৌঁছে দিয়েছেন মেসেঞ্জার। জেলে এসে তিনি তা আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। নাসিম ভাই ক্ষুণাক্ষরেও জিজ্ঞেস করেননি যে কি জিনিস তাঁর হাতে দিয়ে আদান-প্রদান হচ্ছে, তিনি আপত্তি বা সন্দেহ প্রকাশ করেননি এসব বিষয়ে। অথচ কী আশ্চর্য তাঁর হাত দিয়ে তারপক্ষেরই বিপদজনক কতো কিছু হয়েছে। আসলে আন্তরিকতা-বিশ্বাস এখানে এমনভাবে কাজ করেছে যে আমরা বাইরের রাজনীতিতে পরস্পরবিরোধী হলেও বন্দি জীবনে হয়েছিলাম একাট্টা। আর এই একাট্টা প্রেক্ষাপটই এক সময় বাইরে এনে দিয়েছিল জাতীয় ঐক্যের পরিস্থিতি। ফলে এক পর্যায়ে সবাইকে চমকে দিয়ে আওয়ামী লীগ-জাসদ প্রথম এক্যবদ্ধ হয়েছিল। পরে আরওসব দলের সমন্বয়ে সামরিক জান্তা তথা জেনারেল জিয়ার বিরুদ্ধে গণতন্ত্রিক গণআন্দোলন গড়ে উঠেছিল। আর জেলখানায় তখন তালা ভাঙা অবস্থা। সামরিক শাসনের নিগর ভেঙে শুরু হয়েছিল মিছিল, মিটিং, অনশন। জেলখানা এক অর্থে ‘স্বাধীন রাষ্ট্র’ হয়ে উঠেছিল। এটা ১৯৭৮-’৭৯-এর ঘটনা। কারারক্ষী, জমাদার, ডিপুটি জেলার, জেলার, সুপারিনটেনডেন্ট তখন করজোর করে আমাদের শান্ত হতে বলেও পাত্তা পাচ্ছিলেন না। জেলখানা তখন চলছিল আমাদের হুকুম মতো। আমরা ঠিক এমনটা আশা করছিলাম বাইরের ক্ষেত্রেও। (তিন) বাইরের প্রাপ্তিটা কবে মিলবে জানি না। ওই সেই ভয়াল ফায়ারিং স্কোয়াডের দিনগুলো, লাশ গুম করে দেওয়ার দিনগুলো, সামরিক বাহিনীর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পৈশাচিক নির্যাতনের পর ভোররাতে মেশিনগানের ব্যারেলের মুখে দাঁড় করিয়ে ভয় প্রদর্শন, সামরিক শাসন, শোষণ ইত্যাদির মতো কঠিন দিনগুলো পেরিয়ে এসেছি। কিন্তু আজও কি ফায়ারিং স্কোয়াড বা বিনা বিচারে মানুষ হত্যা করে লাশ গুম করে দেওয়ার অবস্থা থেকে মুক্ত হয়েছে? হলে ক্রসফায়ারে মানুষ হত্যা হয় কিভাবে? যদি কনসেনট্রেশন ক্যাম্প না-ই থাকবে তাহলে এতো মানুষ সাদা পোশাকের শিকার হয় কি করে? কি করে জরুরি অবস্থা বহাল থাকে? নেপথ্যে সমর শাসকদের খবরদারি চলে? কেন পাল্টায় না প্রেক্ষাপট? কেন সাধারণ মানুষ তাঁদের নেতৃত্ব নিয়ে সন্দিহান হয়, আস্থা হারায়? কেন মানুষ নেতৃত্বশূন্যতায় ভোগে? কাদের কারণে কারা দায়ী? হ্যাঁ, কেও না কেও দায়ী তো বটেই। দায়ী বলেই না জেলখানা বা বাইরের রাষ্ট্র নামের বৃহৎ জেলখানাটি আজও পর্যন্ত অস্বস্তির। এখানে স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে হলে ’৭১-এর আলোকে আরও অনেক কিছু করতে হবে, নিজের ঘরকে সাজাতে হবে, কলুষমুক্ত করতে হবে, প্রত্যেককে নিজের নিজের মতো করে হতে হবে সত্যিকার অর্থে দেশপ্রেমিক। কবে আসবে সেই আলোকিত ঘর? যতো তড়িৎ আসবে, ততোই স্বস্তি। এখানে কোন ছাড় পাবার সুযোগ নেই। আবুল হোসেন খোকন: সাংবাদিক, কলামিস্ট ও মানবাধিকার কর্মী।
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||
|
|
|
|
|