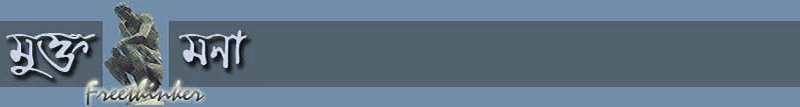
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||
|
|
|
সংশয়ীদের ঈশ্বর আহমাদ মোস্তফা কামাল একজন তরুণ শিল্পীর কণ্ঠে লালনের ‘ক্ষম ক্ষম অপরাধ’ গানটি শুনতে শুনতে আমি যখন প্রায় মোহমুগ্ধ, তখন পাশে বসে থাকা আমার এক বন্ধু বললেন, এই গানটির মধ্যে তিনি মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিকতা খুঁজে পান। আমি নিজে ওটার মধ্যে সেরকম কিছু খুঁজে পাই না বলা বাহুল্য এ আমারই মুর্খতা, নিরেট মুর্খতা; কিন্তু তিনি কীভাবে খুঁজে পেলেন তা আমাকে ভাবিয়ে তুললো। নিজের মুর্খতার জন্য নিজেকে তিরস্কার করলাম, বিনয়ে নুইয়ে গিয়ে বন্ধুটিকে জিজ্ঞেস করলাম গানটির ঠিক কোথায় এবং কীভাবে তিনি মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিকতা খুঁজে পেলেন! আমার অজ্ঞতায় তিনি অবাক হলেন না, তবে নিতান্তই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, আমি যেন গানটি মনোযোগ দিয়ে আরেকবার শুনে দেখি। একবার নয়, বহুবার শুনেও কোনো লাভ হলো না, অর্থাৎ মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিকতা আবিষ্কার করা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। মনে হলো মার্কসবাদ হয়তো আমি ঠিকমতো বুঝতেই পারি না, কিন্তু সেইসঙ্গে একটা প্রশ্ন মাথায় পাকাপাকিভাবে ঢুকে গেলো যা আমি অনেক চেষ্টায়ও খুঁজে পাচ্ছি না, আমার বন্ধুটি সহজেই সেটা পেলেন কীভাবে? আর কেনই-বা গানটিকে মার্কসবাদী নান্দনিকতা দিয়ে বিচার করতে গেলেন তিনি? সেটা না করলে এর রসাস্বাদনে কি কোনো ক্ষতি হয় তার? বলা নিস্প্রয়োজন যে, আমার বন্ধুটি গভীরভাবে মার্কসবাদে বিশ্বাস করেন এবং জীবন ও পৃথিবীর সবকিছুই মার্কসবাদের আওতায় এনে বিচার-বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন, সেই অনুযায়ী গ্রহণ বর্জনও করে থাকেন। আর সেটাই আমার ভাবনার বিষয়। যারা একটি নির্দিষ্ট দর্শনে গভীরভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে থাকেন, তারা সেখান থেকে বেরুতে পারেন না কেন, কেনই-বা সবকিছুকে সেই দর্শনের আওতায় নিয়ে আসতে চান এবং মনে করেন যে, এর বাইরে অন্য কোনো কিছু নেই, অন্য কোনো ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও গ্রহণযোগ্য নয়? তাদের মানসগঠনটি এরকম বদ্ধ কেন? গানের কথায় ফিরে আসি। যে শিল্পীর কথা বলছিলাম, তিনি বয়সে তরুণ হলেও তার কণ্ঠটি কারুকার্যময়, গলায় চমৎকার সুর আছে, কণ্ঠে দরদ আছে। সবচেয়ে বেশি আছে যে-জিনিসটি তার নাম মগ্নতা। এমন মগ্ন হয়ে গানটি গাইলেন তিনি যে, মনে হলো গান নয়, তিনি প্রার্থনা করছেন। আমরা যারা ওখানে ছিলাম সবাই-ই স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম, হয়ে উঠেছিলাম আদ্র-করুণ, এবং অস্বীকার করবো না খানিকটা ভাববাদী। আমার বন্ধুটির মতো আর কেউ মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিকতার কথা ভেবে সেরকমটি হয়েছিলেন কী না জানা হয় নি, তবে মনে হয়েছিলো একটি প্রার্থনা সংগীত (হ্যাঁ, লালনের ওই গানটিকে আমি প্রার্থনা সংগীতই বলবো) শুনলে আমরা সবাই এমন আদ্র-করুণ হয়ে উঠি কেন? আর কেনই-বা প্রতিটি মানুষেরই জীবনের কোনো-না-কোনো সময় প্রার্থনা করতে ইচ্ছে করে? তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে প্রার্থনাটা কার কাছে? প্রার্থনার কথা বললে এই প্রশ্নটি আসবেই, আর প্রশ্নের পিছে পিছে অনিবার্যভাবে আসবে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ, তাঁর অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের প্রসঙ্গ, আস্তিকতা-নাস্তিকতার প্রসঙ্গ। এই লেখাটি সেইসব প্রসঙ্গ নিয়েই। নতুন কোনো বিষয় নয়, বলাই বাহুল্য। প্রচুর কথা হয়ে গেছে পৃথিবীতে, এ নিয়ে। নতুন কথাও খুব বেশি বলা যাবে না। তবু নিজের উপলব্ধির কথা বলে যেতে দোষ কী! ২. এখন, আমাদের সময়ে, কোনো ‘আস্তিক’ স্বীকার করতে লজ্জা পান যে, তিনি আস্তিক কারণ সেক্ষেত্রে তাকে প্রতিক্রিয়াশীল অভিধা পেতে হতে পারে। অন্যদিকে ‘নাস্তিক’রা প্রকাশ্যে বলতে কিঞ্চিৎ ‘ভয়’ পেলেও আড্ডায় বা ঘরোয়া পরিবেশে বেশ গর্ব করেই বলেন যে, তিনি নাস্তিক। অর্থাৎ নাস্তিকতা গৌরবের আর আস্তিকতা লজ্জার! কিন্তু অদ্ভুত শোনালেও সত্যি যে, এর একটি যদি নেতিবাচক হয় তবে একইভাবে অন্যটিও নেতিবাচক শব্দ। আমাদের এখানে একটি ধারণা প্রচলিত আছে এই দুটো শব্দ পরস্পরের বিপরীত অর্থ বহন করে। কিন্তু সত্য হচ্ছে এই যে, আস্তিকতার বিপরীত শব্দ নাস্তিকতা নয়, এই দুটো শব্দ দুটো বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করে। একটি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, অন্যটি ঈশ্বরের অনস্তিত্বে বিশ্বাস। যিনি অনস্তিত্বে বিশ্বাস করেন তিনি আবার ঈশ্বরের পরিবর্তে প্রকৃতি বা এই ধরনের অন্য কোনোকিছুতে বিশ্বাস করেন। এই শব্দ দুটোর বিপরীত শব্দ হচ্ছে সংশয়। একজন সংশয়বাদীকে কি এর যে-কোনো একটি বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বা পক্ষে দাঁড় করানো যাবে? যে-কোনো এক পক্ষে দাঁড় করালে তার অন্য পক্ষে চলে যাবার সম্ভাবনাটিও পুরোমাত্রায় রয়ে যাবে। সংশয়বাদীদের নিয়ে না হয় একটু পরে বলি, তার আগে বরং আস্তিক-নাস্তিকদের নিয়েই কিছু চিন্তাভাবনা করা যাক। প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের দেশে আস্তিকতা-নাস্তিকতার ধারণাটি খুবই অদ্ভুত। বিষয়টি আর ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্বে বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে নেই; দাঁড়িয়ে গেছে ধর্মে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ওপর। অর্থাৎ যিনি ধর্মে বিশ্বাস করেন তিনি আস্তিক, যিনি করেন না তিনি নাস্তিক। এই কনসেপ্টটিকে পরিপূর্ণ বলা যায় না। ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ঈশ্বরের প্রতি যার বিশ্বাস নেই অথচ অন্য কোনো মহামহিম ক্ষমতাবান অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস আছে, আমাদের দেশে তাকে নিশ্চয়ই কেউ আস্তিক বলতে চাইবেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তো আস্তিকই। ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস আছে কি নেই সেটা তো কোনো প্রশ্নই নয়। অন্যদিকে ঈশ্বর সম্বন্ধে একেবারেই কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই অথচ ধর্ম-প্রণীত আচার আচরণ মহা সাড়ম্বরে পালন করেন এমন সব ব্যক্তিকে সবাই আস্তিক বলবেন, যদিও তার আস্তিক্য নিয়ে প্রশ্ন তোলার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রশ্ন উঠতে পারে ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ঈশ্বরে আস্থা নেই এমন লোককে আস্তিক বলা যায় কীভাবে? প্রচলিত দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে আস্তিক বলা যায় না বটে, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে ধর্ম মেনে চলা বা ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত মোটামুটি নিষ্ঠুর এবং ভয়ংকর একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করার পরিবর্তে একজন মানুষ তার নিজের মতো করে একজন ঈশ্বরের কল্পনা করতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে তাঁকে আস্তিক বললে খুব বেশি ভুল করা হবে না। এ প্রসঙ্গে আমরা লালনেরই আরেকটি গানের উদাহরণ দিতে পারি। পারে কে যাবি নবীর নৌকাতে আয় এই গানটির কয়েকটি পংক্তি এরকম নবী না মানে যারা মওয়া ছেদ কাফের তারা আখেরে হয় এই পংক্তি শুনে যে কেউ মনে করবেন, লালন ইসলাম ধর্মে প্রচারিত মতেরই প্রতিধ্বনি করছেন। কিন্তু এর পরের বাক্যগুলো এরকম যে মুর্শিদ সেই তো রাসুল ইহাতে নাই কোনো ভুল খোদাও সে হয় এই পংক্তি অবশ্যই ইসলামের মূল তত্ত্ব বিরোধী। কারণ এখানে মুর্শিদ অর্থাৎ একজন সাধারণ মানুষকে (হতে পারেন তিনি সাধক পুরুষ) প্রথমত রাসুলের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা হয়েছে (রাসুল নিজে কোনো সাধারণ পুরুষ নন, ইসলাম ধর্মমতে তিনি আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ মহামানব)। তবু শরীয়তপন্থী লোকেরা হয়তো এ কথাটি মেনে নিতে আপত্তি করবেন না, কারণ রসুলই বলেছেন আমি তোমাদেরই মতো সাধারণ মানুষ, পার্থক্য শুধু এই যে, আমার কাছে আল্লাহর অহি আসে তোমাদের কাছে আসে না (এটাকে অবশ্য তাঁর অপূর্ব বিনয়ের প্রকাশ বলেই মনে হয় আমার। কারণ যাঁর কাছে আল্লাহর অহি আসে তিনি সাধারণ মানুষ হন কীভাবে?)। কিন্তু লালন যখন বলেন খোদাও সে হয় তখন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীদের প্রতিবাদ স্বরূপ একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠার কথা। কারণ রসুল উপরোক্ত কথাটি বলেছিলেন যেন তার অনুসারীরা আল্লাহর সঙ্গে তাঁকে মিলিয়ে না ফেলেন এবং তাঁকেই আল্লাহ বলে ভাবার মতো ভুল না করেন। কিন্তু এখানে লালন তাই করেছেন। মুর্শিদ (সাধারণ মানুষ), রসুল (মহাপুরুষ) ও খোদা (সৃষ্টিকর্তা) কে তিনি মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে ফেলেছেন এবং পংক্তিটি পরিষ্কারভাবে এ কথাটিই বলতে চায় যে, মানুষ এবং খোদা একই রূপের দ্বিবিধ প্রকাশ অথবা মানুষের মধ্যেই খোদা বিরাজমান তাঁর আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই। এই মত মূল ইসলাম সমর্থন করে না (যদিও এর সঙ্গে সুফিবাদ কথিত মতের বেশ মিল পাওয়া যায়)। প্রশ্ন হলো লালনের খোদা তাহলে কে, এই ধারণাই-বা তিনি কীভাবে এবং কোত্থেকে পেলেন? এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথাও বলা যায়। মানব-ইতিহাসের বিভিন্ন সময়কালে যতগুলো প্রতিভা প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ তাদের অন্যতম, আর রবীন্দ্রনাথের বহুমাত্রিক প্রতিভার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটেছে তাঁর গানে। কী কথায় কী সুরে তিনি এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। পৃথিবীতে এমন ‘সংগীত প্রতিভা’ আর দেখা যায় না। মানুষের জীবনের এমন কোনো অনুভূতি নেই যা তাঁর গানে ধরা পড়ে নি। আমার তো মনে হয় মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে মানিয়ে যাবার মতো একটা না একটা গান রবীন্দ্রনাথের আছে। কিন্তু তাঁর এই বহুবিচিত্র গানগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ প্রতিভার ছোঁয়া পেয়েছে তাঁর প্রার্থনা সংগীতগুলো। মানুষের সমর্পণ ও আতœনিবেদনের এমন অসামান্য আকুতি ও আর্তি অন্তত আমার জানামতে অন্য কোনোকিছুতে ধরা পড়ে নি। তো, তার একটি প্রার্থনা সংগীতের উদাহরণ দেই, যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ রয়ে গো কভু দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর স্বামী ফিরিয়া যেওনা প্রভু। রবীন্দ্রনাথের আস্তিকতা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলবেন না, জানি, কিন্তু এই গানের প্রভু কোন ধর্মগ্রন্থের? বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত কোনো ঈশ্বর তো তার অনুরাগীর এমন অন্যায় আব্দার রাখবেন বলে মনে হয় না, এমন প্রেমময় আহ্বানে তাকে পটানো যাবে না, উল্টো দ্বার বন্ধ দেখে তিনি রেগে যেতে পারেন। প্রভুর এমন কী দায় পড়েছে যে, বন্ধ দ্বার ভেঙে অনুরাগীর হৃদয়ে প্রবেশ করবেন? শুধু কবিদের মধ্যেই নয়, বিজ্ঞানীদের মধ্যেও কখনো কখনো এমন অদ্ভুত ঈশ্বর বিশ্বাস দেখা যায়। মানব-ইতিহাসের আরেক বিস্ময়কর প্রতিভা আইনস্টাইন একবার অনিশ্চয়তা তত্ত্ব নিয়ে বিতর্কে (তিনি ঐ তত্ত্বের বিপক্ষে ছিলেন) যুক্তি দিয়ে সুবিধা করতে না পেরে দি গড ক্যান নট গ্যাম্বলিং বা ঈশ্বর জুয়া খেলতে পারেন না বলে অদ্ভুত এক অবৈজ্ঞানিক মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই মন্তব্যটি থেকেই তার মানসজগৎ সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায় : ১. তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন এবং ২. এই ঈশ্বর কোনো ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ঈশ্বর নন। বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা যাক। আইনস্টাইন ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে ইহুদি ছিলেন। ধরা যাক তাঁর ঈশ্বর বিশ্বাস ইহুদি ধর্ম প্রভাবিত। সেক্ষেত্রে বলতেই হয়, যে-কোনো ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ঈশ্বর জুয়া খেলতে খুবই পছন্দ করেন এবং প্রায়শই জুয়া খেলে থাকেন। অর্থাৎ কোনো নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা না করেই তিনি যা ইচ্ছে তা-ই করেন, এবং যা ইচ্ছে তা-ই করার ক্ষমতাও তাঁর আছে। অতএব ঈশ্বরের জুয়া খেলতে পারেন না বলে তিনি যেমন তাঁর ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে দিলেন (পারেন না শব্দটিই সীমাবদ্ধতার পরিচায়ক) অন্যদিকে ইঙ্গিত করলেন তাঁর ঈশ্বর অবশ্যই নিয়ম কানুন মেনে চলেন, বিজ্ঞানীদের কাজই সেই নিয়ম কানুনগুলো আবিষ্কার করা জুয়াড়িদের মতো কোনো অনিশ্চিত ব্যাপার স্যাপার নিয়ে কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবই নয়। এই কথাটি অনেক পরে স্টিফেন হকিংও বলেছেন। তাঁর মতে একজন ঈশ্বর যদি থেকেও থাকেন তাহলে তিনি মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময়ই কিছু নিয়ম কানুন বেঁধে দিয়েছেন এবং এইসব নিয়ম কানুনে তিনি নতুন করে হস্তক্ষেপ করেন না, কোনো পরিবর্তন করেন না, সত্যি বলতে কি সেই ক্ষমতাই তার নেই। ধার্মিকরা তো বিশ্বাস করেন ঈশ্বরের ইচ্ছে ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না, অথচ হকিং বলছেন মহাবিশ্ব সৃষ্টি করার সময় নিয়ম কানুন বেঁধে দেয়ার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের কাজ শেষ হয়ে গেছে, এর পরে তাঁর আর কোনো ভূমিকা নেই। আইনস্টাইন বা হকিং-এর এই ঈশ্বরই বা কোন ঈশ্বর? কোনো ধর্মের সঙ্গে কি তা মেলে? লালনের দয়াল/খোদা, রবীন্দ্রনাথের প্রভু কিংবা আইনস্টাইনের গড কোনো ধর্মগ্রুন্থের ঈশ্বর নন, অথচ এঁরা প্রত্যেকে ঈশ্বরের মতো কোনো একজনকে কল্পনা করেছেন। এঁদেরকে কি আমরা আস্তিক বলবো? আস্তিক বলতে তো আমরা কোনো ধর্মাবলম্বীকে বোঝাই, অথচ প্রচলিত কোনো ধর্মে এঁদের আস্থা ছিলো না। সেক্ষেত্রে তাঁরা তো আস্তিকই থাকেন না, আবার নাস্তিকও তো বলা যাচ্ছে না, তাঁরা যে বিশ্বাস করেন! আমি এতক্ষণ ধরে তাঁদেরকে আস্তিকই বলেছি, কিন্তু এখন সম্ভবত বলা যায় এঁরা প্রত্যেকেই সংশয়ী। প্রচলিত ঈশ্বর ধারণার প্রতি এঁদের সকলেরই সংশয় ছিলো বলে তাঁরা নতুন এমন একজন ঈশ্বরের প্রকল্প দাঁড় করিয়েছেন যেটা তাঁদের দার্শনিক প্রতীতির সঙ্গে মেলে। ৩. এই ঈশ্বরের স্বরূপটা কিরকম? এঁরা এই ঈশ্বরের ধারণাই-বা পান কোত্থেকে? কেউ হয়তো লালনের ওপর সুফিবাদের প্রভাব খুঁজে পাবেন, অথবা ভারতবর্ষের প্রেম ভক্তিবাদের এবং বৌদ্ধ সহজিয়াবাদের প্রভাবও খুঁজে দেখতে চাইবেন। রবীন্দ্রনাথের ওপর তো লালন, কবীর প্রমুখ মরমীদের প্রভাব প্রায় স্পষ্ট। কিন্তু যে প্রভাবই থাকুক না কেন, ধর্মগ্রন্থের ঈশ্বরের সঙ্গে যে তাঁদের ঈশ্বরের মিল প্রায় নেই একথা সবাই বোঝেন। এমন কি ইসলাম ধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে সম্পর্কিত সুফিবাদের ঈশ্বরও ইসলামী ঈশ্বর নন! সুফিরা মনে করেন মানুষ হচ্ছে ঈশ্বরেরই একটি প্রকাশ মাত্র এবং মানুষ সাধনার মাধ্যমে নিজেকে এমন এক স্তরে উন্নীত করতে পারে যখন মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না, তাঁরা একই সত্ত্বায় পরিণত হন। এ প্রসঙ্গে মনসুর হেল্লাজের উদাহরণ টানা যেতে পারে। কথিত আছে তিনি সাধনার এমন এক উচ্চতর স্তরে আরোহন করেছিলেন যে, নিজেকে আল্লাহ থেকে পৃথক করতে না পেরে ‘আমিই সত্য’ (আনাল হক) বলে দাবি করেছিলেন। শরিয়তের দৃষ্টিতে গর্হিত এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে মনসুর হেল্লাজকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিলো (শরিয়তপন্থীদের মতে, নিজেকে বা অন্য কাউকে, এমনকি নবীকেও, আল্লাহর সঙ্গে তুলনা করা যাবে না, আল্লাহর শরীক বা অংশ হিসেবে বর্ণনা করা যাবে না। নিজেকে আল্লাহ হিসেবে দাবি করা তো ভয়াবহ অপরাধ। জ্ঞানত বা অজ্ঞানত আল্লাহর কোনো শরীক করা মৃতুদণ্ডের মতো শাস্তিযোগ্য অপরাধ)। তো, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর তাঁর রক্ত থেকেও আনাল হক ধ্বনি বেরিয়ে আসতে থাকে, অতঃপর তাঁর সারাশরীর কেটে টুকরো টুকরো করা হয়, কিন্তু প্রত্যেকটি টুকরো থেকে আনাল হক শব্দটি ধ্বনিত হতে থাকলে টুকরোগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়। কিন্তু মাংস-পোড়া ছাই থেকেও একই ধ্বনি নির্গত হতে থাকলে শরিয়তপন্থীরা ভয় পেয়ে ঐ ছাই সাগরে নিক্ষেপ করেন, এবং পরিণামে সাগরের পানি ফুলেফেঁপে উঠে আনাল হক ধ্বনিতে সমস্ত শহর ভাসিয়ে নিতে উদ্যত হয়। মনসুর হেল্লাজ নিজের এই পরিণতি আগে থেকেই জানতেন, (যিনি নিজেকেই খোদা বলে দাবি করেন, তিনি যে আগে থেকেই নিজের পরিণতি জেনে ফেলবেন সে আর বিস্ময়কর কী!) তাই তাঁর এক অনুসারীকে এরকম পরিস্থিতিতে কী করতে হবে সেটা আগেভাগেই বলে গিয়েছিলেন, ফলে সেবারের মতো শহরটি রক্ষা পায়। যাহোক, সুফিবাদের এই আল্লাহর সঙ্গে মূল ইসলামের আল্লাহর ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। মূল ইসলামেরর কনসেপ্ট অনুযায়ী আল্লাহ একটি ইউনিক (একক/অদ্বিতীয়) সত্ত্বা, অন্য সবকিছু তাঁর সৃষ্টি। অর্থাৎ সম্পর্কটা এখানে স্রষ্টা ও সৃষ্টির। আর সুফিবাদ বলছে আলাহ এবং তাঁর সৃষ্টজগতের মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য নেই, কারণ আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন মাত্র। এই ধারণা এখন আর আমাদের কাছে বৈপ্লবিক বলে মনে হয় না, কিন্তু সুফিবাদের জন্মকালে এসব কথাবার্তা কী ভয়ানক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলো ভেবে দেখুন! ইসলামের পরিকাঠামোর মধ্যে থেকে, ইসলাম সৃষ্ট আল্লাহকে মেনে নিয়ে এবং নবীকে এবং ঈমানের অন্যান্য অনুষঙ্গগুলোকে স্বীকার করে নিয়েই তাঁরা আল্লাহর ভিন্নতর একটি রূপ দাঁড় করিয়েছিলেন। এই যে প্রচলিত ধর্মমতসমূহের বাইরে গিয়ে ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি নতুন ধারণা সৃষ্টি বা নিজের জন্যই ঈশ্বরের একটি রূপ তৈরি করেন মনীষীরা, তার কারণ কি? সঠিক কারণটি নির্ণয় করাটা খুবই দুরূহ; সম্ভাব্য কারণটি হয়তো এই যে, তারা অনুভব করেন নিজেকে সমর্পণের জন্য, নিবেদনের জন্য এমন একজনের অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন। কেমন একজন? প্রেমময়, দয়াময়, ক্ষমাশীল একজন। এমন একজন যিনি কথায় কথায় নরকের ভয় দেখান না, স্বর্গের লোভও দেখান না, শাস্তি দেবার জন্য উদ্যত হস্তে যিনি দাঁড়িয়ে থাকেন না, অনুরাগীর অপরাধকে তিনি দেখেন ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে, যাঁর কাছে দাবি করা যায়, যাঁর ওপর অভিমান করা যায়, রাগ করা যায়, এমন কি তাঁর কোনো নিষ্ঠুরতার জন্য তাঁকে অভিযুক্তও করা যায়। প্রেম নিবেদনে যিনি আনন্দিত হন, অনুরাগীর সমর্পণ যাঁকে খুশি করে তোলে। প্রেমের মাত্রাটা বেশি হয়ে গেলে যিনি নিজের বিরাটত্ব ভুলে গিয়ে অনুরাগীর বন্ধ দুয়ার খুলে ঢুকে পড়েন, নিজেকে প্রকাশ করেন অনুরাগীর প্রেমের মধ্যে দিয়ে, প্রমাণ করেনÑ তিনি ভয়ংকর নন, বীভৎস নন, বিদ্বেষপরায়ণ নন, শাস্তিদাতা নন, ভীতিকর নন তিনি প্রেমময় এবং সুন্দরের পুজারী, সমর্পণ আর নিবেদনই তাঁর কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কিছু নয়। ৪. কিন্তু এমন একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব কেন স্বীকার করে নেন মনীষীরা? প্রচলিত কোনো ধর্মে যাঁদের আস্থা নেই, তাঁরা কেন এরকম একেকটি নতুন নতুন ঈশ্বর-ধারণার জন্ম দেন, তিনি না থাকলে তাঁদের এমন কি যায় আসে? এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া কঠিন, কারণ, উত্তর জানতে হলে এঁদের মনোজগৎটি বুঝতে হবে। একজন সৃষ্টিশীল মানুষের মনোজগৎ বোঝা সহজ কাজ নয়। লেখকের সাহিত্যকর্ম, শিল্পীর শিল্পকর্ম, বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ইত্যাদি দিয়ে সংশ্লিষ্টদের দার্শনিক উপলব্ধির জগৎটি খানিকটা বোঝা গেলেও মনোজগৎ বোঝা দুস্কর। এর কারণ দুটো। প্রথমত : সৃষ্টিশীল মানুষটি যতই প্রতিভাবান হন না কেন, তাঁর উপলব্ধির খুব কম অংশই তিনি শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করে যেতে পারেন অধিকাংশটুকুই রয়ে যায় অপ্রকাশিত অবস্থায়। প্রকাশ করার মতো সময়, উপযুক্ত ভাষা বা প্রকরণ খুঁজে পান না তাঁরা। কিন্তু এসবের চেয়ে সত্যি কথাটি হয়তো এই যে, সেই উপলব্ধিকে যথার্থভাবে প্রকাশ করতে পারাটাই এক অসম্ভব ব্যাপার। যে সুগভীর মগ্নতার ভেতর এঁদের কাছে সেই মহামহিম রূপটি ধরা দেয়, সচেতন হলেই তিনি হারিয়ে যান, কেবল রয়ে যায় তাঁর রেশটুকু। এখানে সেই মগ্নতার কথাটিও একটু বলা দরকার। মানব-ইতিহাসের যেসব মহামানবের সৃষ্টিকর্ম দেখে আমরা বিস্মিত ও অভিভূত হই, তার অধিকাংশই ওই মগ্নতা থেকে উৎসারিত। সাহিত্যশিল্পীর সাহিত্যকর্ম, বিজ্ঞানীর তত্ত্ব, সংগীতজ্ঞের কথা ও সুর এসবকিছুর মধ্যে যেগুলো কালজয়ী হয়, যুগ যুগ ধরে আমাদের আপ্লুত, বিমোহিত ও অভিভূত করে যায় সেগুলোর জন্ম যেন কোনো স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় হয় নি বলে মনে হয় আমাদের, যেন কোনো অজানা-অচেনা সূত্র থেকে সেগুলোর আবির্ভাব ঘটেছে। দু-একটি উদাহরণ দেয়া যাক। শহীদ সংগীতজ্ঞ আলতাফ মাহমুদের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি হচ্ছে আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্র“য়ারি গানটি সুর করা। এই সুরটি যখন বেজে ওঠে তখন শ্রেণী-পেশা-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ কিছুক্ষণের জন্য হলেও থমকে দাঁড়ায়, তাদের মন একবারের জন্য হলেও কেঁদে ওঠে; এমনকি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস জানা না থাকলেও সুরটির কারুকার্য মানুষের মনকে এক অজানা বেদনাবোধে আক্রান্ত করে। আমার মনে হয় এদেশের মানুষের কাছে একুশে ফেব্র“য়ারি এমন আদরণীয় হয়ে ওঠার পেছনে এই সুরটির একটি অত্যন্ত গভীর প্রভাব আছে। এর কারণ হয়তো এই যে, এই সুরের মধ্যে দিয়ে এই জাতির কান্না মূর্ত হয়ে উঠেছে, আর আলতাফ মাহমুদ হয়তো সেটিই করতে চেয়েছিলেন। বাঙালি জাতি স্মরণাতীত কাল থেকে নিপীড়িত, নির্যাতিত হয়ে এসেছে কিন্তু কোনোদিনই তেমন কোনো কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে নি। আর তা পারে নি বলেই এই নিরীহ জাতিটি এক সুগভীর বেদনায় নিমজ্জিত হয়েছে, কান্নায় গুমরে মরেছে আলতাফ মাহমুদ একটি সুরের মধ্যে দিয়ে সেই বেদনা দুঃখ কষ্ট কান্না এবং নিপীড়িত-নির্যাতিত হবার ইতিহাসকে মূর্ত করে তুলতে চেয়েছিলেন, এবং বলাবাহুল্য, তিনি সফল হয়েছেন। এ যে কী বিশাল প্রতিভার পরিচয় দেয় তা ভাবা যায় না। এই গানটির কথা কিন্তু তেমন শক্তিশালী বা হৃদয়স্পর্শী নয়, সত্যি বলতে কি কথাগুলো যে আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয় সেটা বোঝা যায় এই ঘটনা থেকে যে, আলতাফ মাহমুদ সুর করার আগে গানটি আবদুল লতিফের সুরে প্রায় এক যুগ ধরে গীত হয়েছে কিন্তু মানুষের মনে সেটি তেমন কোনো অভিঘাত তৈরি করতে পারে নি। বোঝা যায় আবদুল লতিফের সুরে আলতাফ মাহমুদ সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং তিনি নিজেই এটিতে সুর করার কথা ভেবেছিলেন। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই গানটি রচিত হবার এবং প্রথমবার সুর হয়ে যাবার পর তিনি নতুন সুর করতে এক যুগেরও বেশি সময় নেন। আগেই বলেছি, তিনি এমন এক সুর খুঁজছিলেন যা দিয়ে হাজার বছরের বাঙালির চেপে রাখা কান্নাটাকে মূর্ত করে তোলা যায় এবং তেমন একটি সুর সহসা পাওয়া যায় না তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়, সাধনা করতে হয় এক যুগ ধরে হয়তো তিনি সেটাই করছিলেন এবং অবশেষে কাক্সিক্ষত সুরটি তাকে ধরা দেয়। এই অসামান্য সুরটি তিনি পেয়েছিলেন কোথায় এ-কি তাঁর সচেতন সৃষ্টি নাকি গভীর কোনো মগ্নতার ফল যে মগ্নতা তাঁকে সুরটি উপহার দিয়েছিলো! আরেকটি উদাহরণ দেয়া যায়। আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত স্পেশাল থিয়োরি অব রিলেটিভিটি প্রণয়ন করেন ১৯০৫ সালে যখন তাঁর বয়স মাত্র ২৩! এই তত্ত্ব মহাবিশ্ব সম্বন্ধে মানুষের প্রচলিত ধারণাগুলোকে আমূল বদলে দেয়। শুধু বিজ্ঞানেই নয়, এর প্রভাব পড়ে সাহিত্যে, দর্শনে, মনোবিজ্ঞানের আলোচনায়, সংস্কৃতিতে এমনকি অর্থনীতি এবং রাজনীতিতেও। মানব ইতিহাসে এমন যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আর আসে নি। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জায়গা এটি নয়, আমি শুধু দু-একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করবো। এই তত্ত্বের শুরুতেই তিনি দুটো স্বতঃসিদ্ধ (postulates) দেন। এর প্রথমটি আলোর বেগ সংক্রান্ত, যা পুরো উনিশ শতক জুড়ে চলতে থাকা ইথার সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক বিতর্কের অবসান ঘটায়। একটি মাত্র বাক্যে যে-যুবক একশো বছরের বিতর্কের অবসান ঘটান তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করাটাও সাহসের কাজ সে-সাহস আজ পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞানকর্মী করে উঠতে পারেন নি। দ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলোকে পৃথিবীর সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে মুক্তি দিয়ে মহাবিশ্বের অসীম পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে দেন। তিনি বলেন পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলো পৃথিবীর মতোই মহাবিশ্বের সর্বত্র একইভাবে প্রযোজ্য হবে। এই দুটো স্বতঃসিদ্ধ তাঁর মূল কাজের কণামাত্র নয়, অথচ তিনি যদি কেবল এই দুটো কথা লিখেই মরে যেতেন তাহলেও বিজ্ঞানের জগৎ চিরকাল তাঁকে শ্রদ্ধাভারে স্মরণ করতো এমনই ছিলো এর গুরুত্ব। তাঁর মূল তত্ত্ব ছিলো অভূতপূর্ব সব ধারণার সমন্বয় যা মানুষের প্রচলিত ধারণাকে চিরকালের জন্য পাল্টে দেয়। এর মূল কথাটি হলো পরম বলে কোনোকিছূ নেই, সবকিছুই আপেক্ষিক; কোনোকিছুকে বিচার করা যায় কেবল অন্য কোনোকিছুর সাপেক্ষে। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মের মধ্যে থেকে গাণিতিক শৃঙ্খলা মেনে তিনি যে তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন তা ঝামেলা পাকালো দর্শনের আলোচনায়। সেখানেও চলে এলো আপেক্ষিকতা। সবকিছুই আপেক্ষিক এ কথাটি যেন বেদবাক্যের মতো হয়ে উঠলো। এমনকি ঈশ্বরও। অর্থাৎ ঈশ্বর কোনো পরম সত্ত্বা নন, পরম সত্যও নন। তিনিও আপেক্ষিকভাবে সত্য। বিশ্বাসীদের কাছে তিনি সত্য, অবিশ্বাসীদের কাছে মিথ্যা। আপেক্ষিকতত্ত্বের জন্য ঈশ্বরের এই পরিণতি দেখে আইনস্টাইন ব্যথিত হয়েছিলেন কী না জানি না, কিন্তু বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সমস্ত তত্ত্বই গিয়েছিলো ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ঈশ্বরচিন্তার বিরুদ্ধে। ১৯১৭ সালে জেনারেল থিয়োরি অব রিলেটিভিটি তত্ত্বে তিনি আলোর গতিপথ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে গিয়ে বলেছিলেন আলো সবসময় সরল রেখায় চলে না, কখনও কখনও বাঁকা পথও অনুসরণ করে। এটিও ছিলো একটি অবিশ্বাস্য, আশ্চর্য প্রস্তাব। কারণ, এর আগে পর্যন্ত মানুষ বিশ্বাস করে এসেছে আলো কেবল মাত্র সরলরেখাতেই চলে। তাঁর কথা প্রথমে মেনে নেয়া হয় নি। পরে যখন পরীক্ষা করে তাঁর কথার সত্যতা পাওয়া গেলো তখন তিনি বলেছিলেন ‘আলো যদি না বাঁকতো তাহলে ঈশ্বরের জন্য দুঃখ করা ছাড়া আমার কিছু করার ছিলো না, কারণ আমি জানতাম আলো বেঁকেই আসবে, তিনি না বাঁকালে আমি কী করবো!’ অর্থাৎ ঈশ্বরকে চলতে হবে আইনস্টাইনের নিয়ম মেনে! এ কেমন ঈশ্বর! আগেই বলেছি, আইনস্টাইনের সমস্ত তত্ত্বই ছিলো প্রচলিত ঈশ্বর ধারণার বিরুদ্ধে, অথচ তিনি নিজে ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন। এর মানে কী? তিনি কোন ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন? এ কি তাঁর নিজের বানোনো ঈশ্বর? তাঁর কথাবার্তা থেকে বোঝা যায় তাঁর ঈশ্বর বেশ নিয়মকানুন মেনে চলেন এবং কোন কোন নিয়ম তিনি মেনে চলেন বা চলবেন সেটা মানুষের পক্ষেই বলে দেয়া সম্ভব। অর্থাৎ ঈশ্বরের কথা তিনি নিজে বলবেন না, বলবে মানুষ। তাহলে যেসব গ্রন্থকে ঐশ্বরিক বলে দাবি করা হয় সেসবের আর মর্যাদা রইলো কোথায়? রইলো না। আইনস্টাইন সেগুলোর তোয়াক্কাও করেন নি। তবু যে তিনি একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা করেছিলেন তার কারণ হয়তো এই যে, তাঁর সচেতন মন ও অভিব্যক্তি তাঁর তত্ত্বগুলোর জন্ম-প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে পারতো না। একজন অল্পবয়সী যুবক যেসব কথাবার্তা বলেছিলেন, কীভাবে তা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো সেটা বলা সত্যিই দুস্কর। বিজ্ঞানীরা আত্মভোলা হন, আইনস্টাইন সম্বন্ধেও এমন গল্প অনেক ছড়িয়ে আছ তার কারণ হয়তো এই যে, এক সুগভীর মগ্নতা তাঁদেরকে দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। আর ওই মগ্নতা, সাধনা, ধ্যানই জন্ম দেয় ওরকম অভূতপূর্ব সব বৈজ্ঞানিক ধারণা, অসামান্য সুর, ব্যাখ্যাতীত সাহিত্য ইত্যাদির। মগ্ন থাকেন বলে এঁরা বিচ্ছিন্ন থাকেন দৈনন্দিন বাস্তবতা থেকে, তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রাত্যহিকতা থেকে আর এই শিল্পীরা মনে করেন তাঁদের সৃষ্টিকর্মের জন্ম হয়েছে কোনো অজানা উৎস থেকে, এসবের পেছনে যেন কারো হাত আছে। এসব যেন তাঁরা সৃষ্টি করেন না, তাঁদেরকে ধরা দেয় (এদেশের একজন অন্যতম প্রধান কথাসাহিত্যিক আমাকে একবার বলেছিলেন, নিজের লেখাগুলো পরে পড়তে গিয়ে মনে হয় লেখার সময় আমি যেন অন্য কারো করতলে ছিলাম, মনে হয় ওগুলো আমি লিখি নি, আমাকে দিয়ে অন্য কেউ লিখিয়ে নিয়েছে!)। যে উৎস থেকে এসব আসে তাকেই তাঁরা দয়াল বলেন, প্রভু বলেন, গড বলেন প্রচলিত ঈশ্বরের সঙ্গে যাঁর মিল নেই বললেই চলে। এই ঈশ্বর তাঁদের নিজস্ব ঈশ্বর যিনি তাঁদেরকে সৃষ্টিকর্ম উপহার দেন, তাঁর সঙ্গে তাই সম্পর্কটি ভয়ের নয়, প্রেমের ও কৃতজ্ঞতার। আর এই প্রেম ও কৃতজ্ঞতা থেকেই জন্ম নেয় সমর্পণ। বিশ্বাসীরাই শুধু তাদের ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত হন কথাটি ঠিক নয়, অবিশ্বাসী এবং সংশয়ীরাও জীবনের কোনো-না-কোনো সময়ে সমর্পিত হন কারো-না-কারো কাছে; হয়তো কোনো সুনির্দিষ্ট ঈশ্বরের কাছে নয়, তবু তিনি কোনো-না-কোনো অর্থে সমর্পিত ব্যক্তিটির চেয়ে অনেক বড়, মহান এবং দয়াময়। প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক বা সংশয়ীদের এই সমর্পণ অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তাদের কোনো সংজ্ঞায়িত ঈশ্বর নেই। আমার তো মনে হয় বিশ্বাসীরা কোনোদিনই আপাদমস্তক সমর্পিত হতে পারেন না, তাদের ঈশ্বর ধারণা সুনির্দিষ্ট এবং সংজ্ঞায়িত বলেই ঈশ্বর সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার সময় তাদের নেই, তারা তাই ধর্মের কতগুলো আচার মেনেই সন্তুষ্ট থাকেন। ফলে তাদের নিয়মিত ধর্মচর্চা নিছক আচারসর্বস্বতায় পরিণত হয়। ৫. লালন, ওমর খৈয়াম, মির্জা গালিব, হাফিজ, রুমি, রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন এঁরা কেউই হয়তো প্রথম জীবনে প্রচলিত কোনো ধর্মে পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করেন নি; আবার তারা যে নাস্তিক ছিলেন এমন কোনো প্রমাণও পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে এঁরা ছিলেন সংশয়ী। নিজেদেরকে তাঁরা রেখেছিলেন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝখানে। ফলে তাঁদের জীবনে যখন এক ধরনের সমর্পণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো নিজেদের মতো করে একজন ঈশ্বরের ধারণা তাঁরা তখন তৈরি করে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কথা বলা যাক : প্রেমের হাতে ধরা দেব তাই রয়েছি বসে অনেক দেরি হয়ে গেল দোষী অনেক দোষে। বিধিবিধান-বাঁধন-ডোরে ধরতে আসে, যাই যে সরেÑ তার লাগি যা শাস্তি নেবার নেব মনের তোষে তাই রয়েছি বসে।
লোকে আমায় নিন্দা করে, নিন্দা সে নয় মিছেÑ সকল নিন্দা মাথায় ধরে রব সবার নীচে। শেষ হয়ে যে গেল বেলা ভাঙল বেচা-কেনার মেলা ডাকতে যারা এসেছিল ফিরল তারা রোষে প্রেমের হাতে ধরা দেব তাই রয়েছি বসে। বলাবাহুল্য এ হচ্ছে আচারসর্বস্ব ধর্মের প্রতি একটি সূক্ষ বিদ্রুপ। অন্যদিকে এই কবিতাটিকে সংশয়ীদের সমর্পণ সম্বন্ধে একটি চমৎকার উপলব্ধির প্রকাশ বলেও ধরে নেয়া যায়। বিধিবিধান যখন তাদেরকে ধরতে আসে তখন তারা সরে যান, অনেক দোষে দোষী হন, অনেকভাবে নিন্দিত হন এসব তারা মেনেও নেন, তবু প্রেমের হাতে ধরা দেবার জন্যই বসে থাকেন। আরেকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে সকল দেহ লুটিয়ে পড়–ক তোমার এ সংসারে। হয়তো সংশয়ীদের সমর্পণ এমনই, তাঁরা যখন সমর্পিত হন তখন একবারে লুটিয়ে পড়েন, এমন গভীর তাদের সমর্পণ। ৬. এত কথার অবতারণা করতে হতো না যদি আমার বন্ধুটি লালনের ঐ গানটি নিয়ে ওরকম একটি মন্তব্য না করতেন। প্রিয় পাঠক, আমি আপনাদের সামনে গানটি তুলে ধরছি। আপনারাও একটু দেখুন এর মধ্যে মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিকতা খুঁজে পান কী না। ক্ষম ক্ষম অপরাধ, দাসের পানে একবার চাও হে দয়াময়। বড় সংকটে পড়িয়া দয়াল বারেবার ডাকি তোমায় ॥ তোমারই ক্ষমতায় আমি যা কর তাই পার তুমি রাখ মার সে নাম-নামি তোমারি এ জগৎময় ॥ পাপী অধম তরিতে সাঁই তোমার পাবন নাম শুনতে পাই সত্য মিথ্যা জানব হে সাঁই তরাইতে আজ আমায় ॥ কসুর পেয়ে মার যারে আবার দয়া হয় তাহারে লালন বলে এ সংসারে আমি কি তোর কেহই নয় ॥ আগেই বলেছি, আমি ব্যক্তিগতভাবে এই গানের মধ্যে কোনো দ্বান্দ্বিকতা খুঁজে পাই নি, পেয়েছি সমর্পণ, তুমুল সমর্পণ। দয়ালের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা। বড় সংকটে পড়েছেন তিনি সে তো বলছেন-ই, পড়ে দয়ালকে ডাকছেন তাঁর অজানা অপরাধ ক্ষমা করার জন্য। এই গানের মধ্যে আছে প্রেম, আছে ভালোবাসার দাবি আমি কি তোর কেহই নয় কিন্তু দ্বান্দ্বিকতা কোথায়? এমন অসামান্য এক সমর্পণের মধ্যে আমার বন্ধু তাহলে সেটা খুঁজে পান কেন? কেন গানটিকে একটি গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেন? এর কারণ নিহিত আছে আস্তিক ও নাস্তিকদের মানসলোকের মধ্যে। পৃথিবীর সবকিছুকে মার্কসবাদের আওতায় নিয়ে এসে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা আর সবকিছুকে ধর্মের আওতায় নিয়ে এসে ব্যাখ্যা করা একই ধরনের রোগ বলে মনে হয় আমার। এই দুই ধরনের মানুষই জীবন ও পৃথিবীর সবকিছুকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি ফ্রেম তৈরি করেন আর ওই ফ্রেমকেই তিনি স্ট্যান্ডার্ড বলে মনে করেন। পৃথিবীর সবকিছুকেই ওই ফ্রেমে বন্দী করে ফেলাটা তার একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায়, একান্তই কোনো বিষয় যদি সেই ফ্রেমের মধ্যে না পড়ে তাহলে সেটাকে তীব্রকণ্ঠে অস্বীকার করেন। আস্তিকদের জন্য নাস্তিকতা আর নাস্তিকদের জন্য আস্তিকতা হচ্ছে ফ্রেমের বাইরের ব্যাপার ফ্রেমে ফেলে বিষয়টিকে তারা ব্যাখ্যা করতে পারেন না বলেই অস্বীকার করেন। অন্যদিকে সংশয়ীদের এমন কোনো সুনির্দিষ্ট ফ্রেম থাকে না, ফলে তারা যে কোনো বিষয়কেই স্বীকার বা অস্বীকার না করে বিবেচনায় নেন, সংশয় প্রকাশ করেন, বিষয়টির ভালো-মন্দ, ইতি ও নেতি খতিয়ে দেখেন আর এইদিক থেকে বিচার করলে মনে হয় সংশয়ীরা দার্শনিকভাবে অন্যান্যদের চেয়ে এগিয়ে আছেন। তাদের বিবেচনার আকাশটি অনেক বড়, তাদের ভাবনা-চিন্তার জগৎটি ফ্রেমবন্দী নয়, আর তাছাড়া কে না জানে আকাশকে কখনো ফ্রেমবন্দী করা যায় না! ৭. কিন্তু সংশয়ীদের নিয়ে একটি বড় সমস্যাও আছে। সেটি হচ্ছে দার্শনিকভাবে তাঁদের ওপর কোনো আস্থা রাখা যায় না। তাঁরা যে কখন কোন দলে যাবেন সে ব্যাপারে আগাম কিছুই বলা যায় না। আপনি আস্তিকদের ওপর আস্থা রাখতে পারেন, পারেন নাস্তিকদের ওপরেও কারণ তাদের সুনির্দিষ্ট বিশ্বাস আছে। আপনি ধর্মপন্থিদের ওপর আস্থা রাখতে পারেন, পারেন মার্কসবাদীদের ওপরেও কারণ তাদের মনোজগতের প্যাটার্নটি আপনার মোটামুটিভাবে জানা। কিন্তু সংশয়ীরা কোনদিকে যাবে তা আপনি বুঝবেন কীভাবে? না, বোঝার উপায় নেই। অতএব আপনি যদি কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে চান তাহলে ভুলেও সংশয়বাদীদের কথা শুনতে যাবেন না। লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে সংশয়বাদী দর্শন এক বিরাট প্রতিবন্ধক। এ জন্যই বলেছি, আস্তিকদের শত্র“ নাস্তিকরা নয়, নাস্তিকদেরও শত্র“ নয় আস্তিকরা কারণ এরা পরস্পরের স্বরূপ জানে, এরা বড়জোর পরস্পর বিরোধী। প্রকৃতপক্ষে শত্র“ হচ্ছে সংশয়ীরা, কারণ এঁদের স্বরূপ কেউ জানে না। এঁদের মোকাবেলা করতে হলে আপনাকে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট আকারের ফ্রেম তৈরি করতে হবে, সবকিছুকে সেই ফ্রেমে বন্দী করে বিচার করতে হবে এবং ফ্রেমের বাইরের সবকিছুকে নির্মমভাবে ছেঁটে ফেলতে হবে, যদিও এরকম করলে আপনি হয়ে উঠবেন একজন ছাঁচে ঢালাই করা মানুষ তাতে ক্ষতি নেই যদি আপনার লক্ষ্যটি অর্জিত হয়। সংশয়ীদের ওপর যদি আস্থা না-ই রাখা যায় তাহলে তাঁদের বিশাল আকাশ থেকে লাভটা কি হলো? তাঁরা তো সর্বদা পরিত্যাজ্য। না, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো লক্ষ্য অর্জন বা জাতীয় জীবনের কোনো লক্ষ্য অর্জনেও সংশয়ীরা তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারেন না, তাঁরা বরং পরিত্যাজ্যই, কিন্তু জীবন তো শুধু ব্যক্তিগত কিংবা জাতীয় জীবনের বৈষয়িক লক্ষ্য অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর মহত্তম কোনো দার্শনিক লক্ষ্যও থাকতে পারে। সেরকম কোনো মহত্তর উপলব্ধি অর্জন করতে হলে আপনাকে সংশয়ীই হতে হবে। একটা উদাহরণ দেয়া যাক। আমাদের দেশে যারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করেন, কিংবা ইসলামী হুকুমত কায়েমের স্বপ্ন দেখেন এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করেন তারা বলতে পারেন না যে, এই লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গেলে তাদের পরবর্তী করণীয় কাজটি কী হবে! চিন্তাটিকে আরেকটু বৃহত্তর পরিসরে নিয়ে যাওয়া যাক। ধরা যাক, সারা বিশ্বই একদিন সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে রূপান্তরিত হলো বা সারাবিশ্বেই একদিন ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়ে গেলো, এরপর মানুষ কী করবে? ওরকম কোনো অবস্থা যদি সত্যি সত্যি তৈরি হয় তাহলে সেই পৃথিবী কি আর বসবাসযোগ্য থাকবে? পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ আল্লাহর ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে কান্নাকাটি করছে, কিংবা পৃথিবী জুড়ে মানুষ একটি অভিযোগহীন জীবনযাপন করে যাচ্ছে এরকম পৃথিবী তো ভয়াবহ। ওরকম বৈচিত্র্যহীন পৃথিবীতে আত্মহত্যা করা ছাড়া মানুষের মুক্তির আর কোনো পথ খোলা থাকবে বলে তো মনে হয় না। মুশকিল হলো এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে কেউ-ই সহজে মুখ খুলতে চান না, বরং আগে তো সেই সমাজ অর্জিত হোক এরকম কথা বলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন। ইসলামপন্থিদের মধ্যে দার্শনিক খুঁজে পাওয়া আর এক সমুদ্র জলে একটি সুঁই খুঁজে পাওয়া একই কথা তাই তাদের কাছ থেকে এর সদুত্তর পাওয়ার আশা করাই বৃথা। কিন্তু বামপন্থি দার্শনিকরা কেন এটা নিয়ে কথা বলেন না? কেন তারা বলেন আগে তো সেই সমাজ অর্জিত হোক তারপর দেখা যাবে! কেন পরে দেখা যাবে? কেন এখনই বলা যাবে না? এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে না চাওয়া বা প্রশ্নটি এড়িয়ে যাবার কারণটি হয়তো এই যে, এই দার্শনিকরা জানেন ওরকম একটি সমাজ অর্জিত হওয়া পর্যন্তই কেবল মাত্র তাদের দর্শন ক্রিয়াশীল থাকতে পারে এরপর তার আর কোনো ভূমিকা থাকবে না। জেনেশুনেও কেন তারা অমন একটি অলঙ্ঘনীয় ফ্রেম তৈরি করেন বলা মুশকিল। ব্যক্তিগতভাবে আমি মার্কসবাদকে মানব-ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্শন বলে মনে করি এবং এই দর্শন মানুষের জন্য যে ধরনের সমাজ কামনা করে সত্যি সত্যি যদি তা অর্জিত হয় তাহলে সেটা হবে এই দর্শনের বিরাট সাফল্য, এরপর এর মৃত্যু ঘটলেও কিছু যায় আসে না। তবে এমন একটি অসামান্য দর্শনের মৃত্যুর পরও সংশয়ীরা ক্রিয়াশীল থাকতে পারেন। সংশয়ীদের কৌতূহলের শেষ নেই, প্রশ্নেরও শেষ নেই আর তাই অনুসন্ধানেরও শেষ নেই। শেষ নেই বলেই সংশয়ীরা কোথাও দাঁড়ান না, অবিশ্রান্তভাবে এগিয়ে চলেন। ঈশ্বরবিহীন পৃথিবীতে তাঁরা নতুন ঈশ্বরের জন্ম দিতে পারেন হয়তো এভাবেই কোনো এক সুদূর অতীতে কোনো এক সংশয়ী মানব সমাজে ঈশ্বর ধারণার সূচনা করেছিলেন। একইভাবে ঈশ্বরময় পৃথিবীতে তাঁরা সংশয়ী প্রশ্ন করে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে পারেন। অর্থাৎ কোনো অবস্থাই তাঁদের জন্য শেষ অবস্থা নয়। অন্য সব দর্শন যেখানে হেরে যায়, থেমে যায় সংশয়ীরা তখনও থাকেন চলমান। এই একটি জায়গায় সংশয়ীরা অন্য সবার থেকে শ্রেষ্ঠ।
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||
|
|
|
|
|