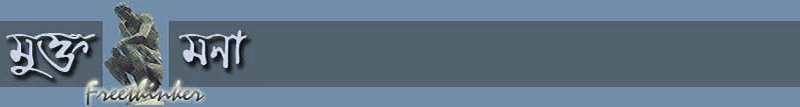শাহ মোহাম্মদ হান্নানের বক্তব্যে আমার প্রতিক্রিয়া ১
শাহ মোহাম্মদ হান্নান নামক ব্যাক্তিকে ব্যাক্তিগত ভাবে চেনার সুযোগ হয় নি আমার। তবে একুশে টেলিভিশনে প্রচারিত অনুষ্ঠানে তার বক্তব্য শুনবার দুর্ভাগ্য হয়েছে আমার। তিনি ইসলামি চিন্তাবিদ এটাও জানতে পারলাম আলোচনার সময়ে। তিনি মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সচিবালয়ে কর্মরত ছিলেন এ তথ্যটাও জানতে পারলাম আলোচনার সময়।
তার বক্তব্য প্রসঙ্গে এবং প্রসঙ্গিক বক্তব্যে তিনি যেসব তথ্য এবং মতাদর্শের কথা বলেছেন তা তার একক মতাদর্শ নয় বরং জামাতে ইসলামি নামক দলটিও কাছাকাছি একটা রাজনৈতিক মতাদর্শ বিশ্বাস করে। তিনি ১৯৭১ সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধকে যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন একই বিশ্লেষণ আমরা পাই ঘোরতর জামাত সমর্থকের কাছে। তারা ১৯৭১এ জামাতের ভুমিকাকে সমর্থন করে , জামাতকে যুদ্ধাপরাধীর কাতারে নিয়ে আসেন না তারা। বরং তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে জামাতের অবস্থান সঠিত বিবেচিত হতে পারে এমন একটা বিভ্রান্তি তৈরি করতে চান।
মুলত বিতর্কটা সৃষ্টি হয়েছে মুজাহিদের নির্বাচন কমিশনে দেওয়া বক্তব্যের ভিত্তিতে যেখানে মুজাহিদ বলেছে বাংলাদেশে কোনো যুদ্ধাপরাধি নেই এবং বাংলাদেশে কখনই স্বাধীনতাবিরোধি কেউ ছিলো না। খুব আশ্চর্যান্বিত হতে হয় মৃজাহিদের বক্তব্য শুনে। ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণার পরে যখন আলোচনাটা ছিলো মুলত চিহ্ণিত শত্র“র বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এবং যখন স্বাধীনতা পক্ষের শক্তি হিসেবে চিহ্ণিত মুক্তিযোদ্ধারা সম্মিলিত ঐক্যের ডাক দিয়ে বলেছিলো যারা পাক বাহিনীর দোসর হিসেবে কর্মরত তারা ইচ্ছা করলেই মুক্তিবাহিনীতে যুক্ত হয়ে স্বাধীনতার লড়াইয়ে সামিল হতে পারে, পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সাথে লড়াই করে বাংলাদেশ স্বাধীন করবার জন্য যখন লিফলেট বিলি করা হয়েছিলো তখন স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো আমরা কার সাথে কিসের লক্ষ্যে লড়ছি।
২৬শে মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা এবং লিফলেট বিলির পরে আসলে পক্ষ বিভাজনে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কারা স্বাধীনতা বিরোধি ভুমিকা নিয়েছিলো সেদিন এটা স্পষ্ট হয়ে যায় এরপরেই। জামাত ১৬ইা ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবার পরে আজ স্বাধীন বাংলাদেশে যখন এ কথা বলবার ধৃষ্টতা দেখায় যে কেউই স্বাধীনতা বিরোধি ছিলো না তখন ১৯৭১ সালটাই উবে যায় বাংলাদেশের মানুষের ভেতর থেকে। সংবিধানের সুচনায লেখা বাংলাদেশের অভ্যুদয় সংক্রান্ত তথ্যটাও মিথ্যে হয়ে যায়।
আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো বড় মাপের কোনো ঘটনা সংঘটিত হয় নি এমন উপসংহারে পৌঁছে দিয় আমাদের। অর্থ্যাৎ মুজাহিদের উক্তিতে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অস্বীকার করবার উপাদান আছে, তার ঔদ্ধত্ব্য বিষয়ে আলোচনার আগে আরও অনেক কিছু নিয়ে কথা বলা হবে, তবে প্রেক্ষাপট এটাই যে মুজাহিদের বক্তব্যের সাথে শাহ মোহাম্মদ হান্নানের বক্তব্য মিলিয়ে পড়লে স্পষ্ট হবে জামাতের ৭১ বিষয়ক ভাবনা এবং ৭১ বিষয়ে তাদের মুল্যায়ন এবং ৭১এ তাদের ভুমিকাকে সমর্থন করবার জন্য তারা কিরকম রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করবে ভবিষ্যতে।
তিনি বেশ বড়াই করে বলেছেন তিনি বাংলাদেশেব খাদেম ছিলেন এবং অন্যান্য খাদেমদের তুলনায় তার অবদান মোটেও ন্যুন নয় বরং অনেকের চাইতে বেশী। বিভিন্ন মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে একটা ধারণা জন্মেছে আমার। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সচিবালয়ে কর্মরত এবং উচ্চপদে আসীন বিধায় প্রাথমিক অনুমান তিনি পাকিস্তানের সময়ে পিসিএসের কর্মচারি হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। যখন বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে তখন তিনি বেশ পদস্থ কর্মচারি পাকিস্তান প্রশাসনের।
তার ছাত্র জীবন কেটেছে পাক সার জমিন গেয়ে এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়েও তিনি পাকিস্তান সরকারের অনুগত কর্মী। পাকিস্তান রাষ্ট্রের যৌক্তিকতা এবং অপরিহার্যতা বিষয়ে নিসংশয় বিধায় তিনি অন্যান্য সরকারি কর্মচারি যারা ১লা মার্চ থেকেই পাকিস্তান সরকারের অধীনে কাজ করা থেকে বিরত ছিলেন এবং যারা এর পরবর্তী সময়েও পাকিস্তান রাষ্ট্রের অধীনে কাজ করাকে নিজ গৌরবের পক্ষে অসম্মানজনক ভেবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করা শুরু করেন এবং যারা প্রসাশনিক কর্ম থেকে বিরত ছিলেন তাদের কাতারে যোগ দেন নি তিনি।
তিনি পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের অপরিহার্যতা এবং ভারতীয় কাফের আগ্রাসনের ভয়ে ভীত একজন মানুষ যিনি পরবর্তীতে ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে খ্যাত(!)। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে বিশ্বস করেন মুক্তিযুদ্ধকে আদতে সিভিল ওয়ার হিসেবে বিবেচনা করা যায় এবং তিনি এ মতবাদের অনুসারি।
১৯৭১এ তৎকালীন পুর্ব পাকিস্তানে যা ঘটেছে সেটা গৃহযুদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করা যায়- এ বক্তব্য আদতে কোন রাজনৈতিক বিশ্বাস সমর্থন করতে পারে। যদিও তার এ বক্তব্য এবং মনোভাব আমার বিতৃষ্ণা বাড়িয়েছে এবং জিঘাংসা জাগ্রত করেছে তবে এ বিষয়ে নিজস্ব অনুভবকে হত্যা করেই তার বক্তব্য সমাপ্ত করতে চেষ্টা করি।
তিনি এটা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এটা সিভিল ওয়ার হিসেবে দেখা হয়েছে। তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন একজন পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র হিসেবে। এবং তার বিজ্ঞতা তাকে ভাবতে শিখিয়েছে এটা আদতে গৃহযুদ্ধই ছিলো। তবে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র এবং এই রাষ্ট্রের সংবিধানে বিষয়টা চিহ্ণিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে এবং সংবিধানের সুচনায় বলা হয়েছে এই রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। তবে এ বিষয়ে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রে কোনো সংশয় নেই। সংবিধানের কোথাও ১৯৭১এর ঘটনাবলী বিষয়ে এমন কোনো বিকল্প ধারণা দেওয়ার চেষ্টা নেই যে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকে বিবাদমান দুই রাজনৈতিক শক্তির আভ্যন্তরীণ কোন্দল থেকে সৃষ্ট সহিংস সংঘাত এবং গৃহযুদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।
তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের অংশ হিসেবে এর নীতিনির্ধারনী পর্যায়ে তার অবদান রেখেছেন তবে তিনি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের এই মূলনীতিতে বিশ্বাসী নন। এবং তার নিজস্ব বিশ্বাস ধর্মীয় রাজনীতি এবং ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার একটি গণতান্ত্রিক অধিকার। তবে তিনি যে আদতেই বাংলাদেশের গঠনতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না এবং এটাকে অপ্রয়োজনীয় এবং অবজ্ঞা যোগ্য ভাবেন তার প্রমাণ এই বক্তব্য। বাংলাদেশের প্রথম গৃহীত সংবিধানে ধর্মেও রাজনৈতিক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো। এবং এটা মেনে নিয়েই তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মচারি হিসেবে কাজ করেছেন।
মুজাহিদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে নানাবিধ বিতর্কের জন্ম হয়েছে এবং নানা রকম মত আলোচনার টেবিলে এসেছে। নিষিদ্ধ ঘোষিত ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারকে বৈধতা দেওয়া এবং বিএনপির সৃষ্টি বিষয়ে এবং গোলাম আজমের নাগরিকত্ব বাতিলের পর মানবিক বিবেচনায় তাকে বাংলাদেশে ঢুকতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বিষয়েও বিতর্ক উঠেছে। ১৯৭১ সালের ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এসব কিছু। শেরে বাংলার মৃত্যুর পরে নখদন্তহীন কৃষক পার্টি বাংলাদেশের রাজনীতিতে কোন প্রভাব রাখতে ব্যর্থ ছিলো। মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠা এবং পাকিস্তান সৃষ্টিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিকদের অবদান বিবেচনা করে বলা যায় ১৯৭০ সালে নির্বাচনে ব্যপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পরেও মুসলীম লীগের সমর্থক সংখ্যা আওয়ামি লীগের কাছাকাছি ছিলো। এবং অনেক মুসলীম লীগের কর্মী সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করেছেন এবং অনেক মুসলীম লীগ নেতাই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সহানুভুতিশীল ছিলেন। তারা পরোক্ষ ভাবে মুুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছেন।
ভোট সংখ্যা বিচারে এর পরের অবস্থানে ছিলো নেজামি ইসলামি এবং এর পরে ছিলো জামাতে ইসলামি- যদি ভোট সংখ্যা হিসেব করা হয় তবে ভোটারদের ৩ শতাংশও জামাতে ইসলামিকে ভোট দেয় নি। মাত্র ১টা আসনে জয় পেয়েছিলো জামাত বাংলাদেশে। তাই রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে জামাতে ইসলামি কখনই আওয়ামী লীগের প্রতিদন্ডী ছিলো না। বরং যদি দাবি করা হতো মুসলীম লীগ এবং আওয়ামী লীগের ভেতরে একটা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছিলো এবং তা একটা সহিংস সংঘাতে পরিনত হয় সেটা হয়তো গৃহযুদ্ধের ধারণাকে সামান্য হলেও সমর্থন করতো। ৯৮ শতাংশ আসন পাওয়া একটি দলের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে এমন একটা রাজনৈতিক দলের নাম প্রস্তাব করা যারা জনপ্রিয়তার বিচারে যোজন যোজন দুরত্বে নেহায়েত কষ্টকল্পনা। কিংবা নির্জলা মিথ্যাচার, কুতর্ক তৈরি করবার চেষ্টা।
যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের ইতিহাসের গল্প বাদ দিয়ে ১৪ই ডিসেম্বর এর পর থেকে পরিস্থিতি সম্পুর্ন বদলে যায়। শুধুমাত্র ঢাকা এবং এর কাছাকাছি এলাকা তখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দখলে, তাদেও সম্পুর্ন অন্তরীন করে ফেলা হয়েছে। কোনো পন্য বা অস্ত্রচালান এমন কি সৈন্যরাও ঢকিতে পারছে না ঢাকায়। বুদ্ধিজীবি হত্যার তালিকা থেকে বেছে বেছে মানুষকে বধ্যভূমিতে নিছে যাওয়া হচ্ছে, এবং এ কাজের তদারকি করছে আল বদর ও আল শামস বাহিনী। এরপরে পরাজয় নিশ্চিত জেনে ১৫ই ডিসেম্বর থেকে পাকিস্তানগামী ফ্লাইটে চেপে দেশ ছাড়ছে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এবং কর্মকর্তাদের স্ত্রী পুত্র কন্যা এবং একই সাথে এ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে উচ্চ পর্যায়ের জামাত নেতারা।
১৬ই ডিসেম্বরের পর থেকে দেশের কারাগারগুলোতে উপচে পড়া ভীড়, জনরোষ থেকে বাঁচতে দলে দলে রাজাকার বাহিনীর সদস্য এবং আল বদর- আল শামস সংগঠনের কর্মী ও নেতারা স্বেচ্ছায় কারাবন্দীত্ব নিচ্ছেন। প্রাণভয়ে ভীত এসব মানুষের উপচে পড়া ভীড়ে কারাগারে স্থান সংকুলান হচ্ছে না এরপরও সবাই গাদাগাদি করে ঢুকতে চাইছে জেলে।
সবাই যে কারাগারের নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পেরেছিলো এমন নয়, যারা সময় মতো লুকিয়ে পড়তে পারে নি, যারা ভোল পাল্টে মুক্তিযোদ্ধাদের দলে ভীড়তে পারে নি তাদের সংক্ষিপ্ত বিচারে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হচ্ছে এবং তা তৎক্ষণাত কার্যকরী হচ্ছে। এমন চিত্র সর্বত্রই ছিলো। যারা স্বাধীনতা বিরোধী তাদেও বিচারের দাবি উঠেছে তখনকার সাপ্তাহিক পত্রিকা বাংলার বানীতে, ১৮ই ডিসেম্বর থেকে ২রা জানুয়ারী, সকল সম্পাদকীয়তে এদের বিচারের উদ্যোগ নেওয়ার জোড়ালো দাবি উত্থাপিত হয়েছে।
স্বাধীনতাবিরোধী হিসেবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে সেসব মানুষেরা যারা ২৬শে মার্চের পর থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদত দিয়েছে এবং বাংলাদেশের নাগরিকদেও জান ও মালের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত হয়েছে এবং যারা ছিলো সেনাবাহিনীর এ দেশীয় মদতদাতা। ভাষাগত পরিচয়ে এরা অধিকাংশই ছিলো বাংলা ভাষাভাষি এবং এদেও অধিকাংশই ছিলো জামাতের কর্মী।
রেজাকার বাহিনী এবং শান্তি বাহিনীতে যোগদান করা অন্য রাজনৈতিক বিশ্বাসের মানুষের তুলনায় আল বদর এবং আল শামস বাহিনী ছিলো চরম নৃশংস। শান্তি বাহিনীর সদস্যরা অধিকাংশই ছিলো মুসলীম লীগের নেতা কর্মী। তবে জামাতে ইসলামির নেতা কর্মীরা যোগদান করেছিলো মুলত রেজাকার বাহিনীতে এবং অধিকাংশই আল বদর ও আল শামসের সদস্য হিসেবে নৃশংস হত্যায় ও মানবতাবিরোধী কাজে লিপ্ত ছিলো।
তাদের
পরিকল্পনায় সমাপ্ত হয় বুদ্ধিজীবি হত্যা এবং পরিচিত আওয়ামি লীগ
কর্মীদের উপরে এরা যে নির্মম অত্যাচার চালায় তা কল্পনাতীত।
যুদ্ধাপরাধের সংজ্ঞা ও পরিধি নিয়ে আগেও লেখা হয়েছে তাই
পুনারাবৃত্তি নি¯প্রয়োজন। তবে যুদ্ধাপরাধীর সংজ্ঞা নির্ধারণের
প্রাথমিক পর্যায়ে পাকিস্তান প্রশাসনে কর্মরত সকল কর্মকর্তাই
যারা ২৬শে মার্চ এবং এর পরবর্তী সময়ে বিদ্রোহ কওে বের হয়ে
গেছেন তাদের বাদ দিয়ে অন্য সবাই ছিলো পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর
মদতদাতা।
১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বরের পর এক অদ্ভুত জটিলতা ছিলো, তখনও
প্রসাশনে কর্মরত ছিলো অনেক বাঙালী , পাকিস্তানী বংশোদ্ভুতরা
চলে যাওয়ার পওে একটা প্রশাসনিক শুণ্যতা দেখা দেয়।
প্রশাসনিক কাজে দক্ষ জনশক্তির অভাব ছিলো, এবং অনেকেই নিহত হয়েছিলেন যুদ্ধে, মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী দিনগুলোতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরে শেখ মুজিবর রহমান অনেক অযোগ্য লোককে প্রশাসনে নিয়োগ দেওয়ার পরেও এই শুণ্যতা কাটিয়ে উঠা যায় নি। রাষ্ট্রিয় চাহিদা বিবেচনা করে প্রশাসনের কর্মকর্তারা যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে কাজ করেছেন এবং যাদেও বিরুদ্ধে সহযোগিতার স্পষ্ট অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তাদের বাদ দিয়ে সবাই পুনরায় নিয়োগ পায়।
তবে এদেও অধিকাংশই অনুগত কর্মচারি ছিলো না। এমন কি যখন যুদ্ধ পরবর্তী পুনর্গঠনের কাজ চলছে এবং লোকজন ভারত থেকে ফিরছে এবং ধর্ষিতাদেও শাররীক এবং মানসিক নির্যাতনের প্রতিকারের চেষ্টা চলছে তখন এদেও কেউ কেউ ছিলো অতিশয় নিরুৎসাহি। তারা কোনো রকম প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা দেয় নি।
১৯৭৩এ যুদ্ধাপরাধীদেও বিচারের জন্য আইন প্রণীত হলো, সর্বনিম্ন ২ বছর থেকে মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত নানা রকম শাস্তির বিধান ছিলো অপরাধের গুরুত্ব ও ব্যপকতা বিচার করে এসব শাস্তি নির্ধারিত হয়েছিলো।
যারা সরাসরি যুদ্ধাপরাধের সাথে যুক্ত- সেসব প্রশাসনিক কর্মকর্তা যারা পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বাংলাদেশের নাগরিকদেও জান-মালের নিরাপত্তা বিঘিœত করেছে সেনাবাহিনীর নির্দেশে এবং যারা এই ঘৃনিত কাজে সরাসরি নিয়োজিত ছিলো তারা প্রত্যক্ষ যুদ্ধাপরাধী এবং তাদেও ১০ বছরের কারাদন্ড থেকে শুরু করে মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত শাস্তিও বিধান ছিলো।
যারা পরোক্ষ মদতদাতা তাদের জন্য ২ থেকে ১০বছরের কারাদন্ডের বিধান ছিলো।
১৯৭৪ সালে আরও শিথিল করা হলো এই আইন , তখন সারাদেশে এই আইনে আটক অপরাধীর সংখ্যা ছিলো প্রায় ৩৭০০০। তবে সাধারন ক্ষমা ঘোষিত গওয়ার পরে ২৬০০০ মানুষ অব্যহতি পায়, কিন্তু তখনও ১১০০০ চিহ্ণিত যুদ্ধাপরাধীর বিরুদ্ধে স্পষ্ট অভিযোগ থাকায় তারা মুক্তি পায় নি। ১১০০০ যুদ্ধাপরাধী যাদের বিচারকাজ চলছিলো এবং ৫০০ অপরাধি যাদের অপরাধ নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছিলো তারা কারান্তরীণ ছিলো। সুতরাং যতই উদ্ভট দাবি উত্থাপিত হোক না কেনো ঐতিহাসিক বাস্তবতা হলো অন্তত ৫০০ জন অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধী ছিলো কারাগারে। সাধারন ক্ষমার আওতায় না আসা আরও ১০৫০০ জনের অভিযোগের মীমাংসা হয় নি-
প্রায়শই অভিযোগ আসে ৭২এ নির্বাচিত সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিষয়ে উদাসীন ছিলো- তবে কথাটা মোটেও সঠিক না।
যারা অহেতুক কুতর্কে লিপ্ত হতে চায় তারা প্রতিনিয়ত বলতে চায় এমন কি কারান্তরীন যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত মানুষের সন্তানেরাও বলে ১৯৭৪এ সাধারন ক্ষমা ঘোষনা আওতায় ছিলো সবাই, দালাল আইনে আটক সবাই সাধারণ ক্ষমার আওতায় আসে নি। জামাতে ইসলামির নিজস্ব স্বার্থ আছে এখানে তবে অন্য যারা এ দাবি করে তারা কোন স্বার্থ বাস্তবায়িত করতে চায়?
এই বাক্যটা লিখতে রীতিমতো ভাবতে হচ্ছে, আমাদের ঐতিহাসিক ভাষ্য সবই প্রায় রাজনৈতিক রিরংসাপূর্ণ এবং আমাদের এখানে এমন নির্মোহ ঐতিহাসিক নেই যে বলবে আদতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে নয় বরং সত্যই এমন ঘটনা ঘটেছিলো।
প্রশ্নটা সাধারণ, কারা কিংবা কে আগ্রনী ভুমিকা পালন করেছইলো এই
যুদ্ধাপরাধে আটক ব্যক্তিদের মুক্ত করতে-
খন্দকার মোশতাক হোসেন নাকি জিয়াউর রহমান? তবে প্রচলিত প্রথা
মেনে লিখছি-
মুলত ১৯৭৫ এ ২২ বার ক্যু হওয়ার পরে স্থিরতা আসলে জেনারেল
জিয়াউর রহমান তাদের মুক্তি প্রদান করেন।
সৌজন্যঃ সচলায়তন