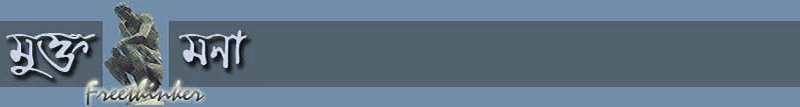যাই হোক, দ্বিতীয়
বিশ্বযুদ্ধের মারণলীলা শেষ হতেই ইউজেনিক্সের দাপটও শেষ হল। কিন্তু ধাক্কা
খেল না জিন-বিজ্ঞান। নতুন নতুন আবিষ্কার থেমে থাকল না। মরগ্যান সমাধান করে
দিয়ে গেছেন যে ক্রোমোসমের মধ্যেই থাকে বংশগতির চাবিকাঠি, সেই চাবিকাঠি এবার
হাতে তুলতে মানুষ মরিয়া হল। কিন্তু তার জন্য জানা চাই বংশগতির রাসায়নিক
তত্ত্ব - যা রাসায়নিক আকারে বলে দেবে বংশগতি ঠিক কি ভাবে প্রবাহিত হয়।

যখন ডারউইন তার
বিবর্তনবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হিমসিম খাচ্ছে
ন, সেই সময়ে
ফ্রেডেরিক মিশার নামে এক সুইস জীববিজ্ঞানী পুঁজ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে
দেখলেন এর মধ্যে নিউক্লিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। পরে তিনটি শ্বেতকণিকার
ক্রোমোজোমকে নিউক্লিক অ্যাসিডের উৎস হিসাবে সঠিকভাবে চিহ্নিত করেন। উনি এর
নাম দেন নিউক্লেইন। মিশার সঠিকভাবে ধারণা করতে পেরেছিলেন যে বংশগতি কোনো
রাসায়নিকের মাধ্যমেই প্রবাহিত হয়। উনি নোবেল পুরষ্কার পাওয়া অবধি বেঁচে
থাকতে না পারলেও আরেক বিজ্ঞানী এরপরে নিউক্লিক অ্যাসিড নিয়ে কাজ করে নোবেল
পুরষ্কার পান। তিনি হলেন
অ্যালব্রেখট কোসেল (ছবিতে)। ১৯১০ সালে প্রোটিন আর নিউক্লিক অ্যাসিড
নিয়ে কাজ করার জন্য তাঁকে এই সম্মান দেওয়া হয়। নিউক্লিক অ্যাসিড নিয়ে কাজ
তখন সবে শুরু। নিউক্লিক অ্যাসিডের গঠন নিয়ে এর পরে কাজ করলেন
ফিবাস লেভেন,
নিউ ইয়র্কে রকফেলার ইন্সটিটিউটে। ইনি কোষে পাওয়া নিউক্লিক অ্যাসিডের
রাসায়নিক উপাদানগুলোকে আলাদা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নিউক্লিক অ্যাসিডের চার
উপদান - অ্যাডেনিন(A), থিয়ামিন(T), সাইটোসিন(C) আর গুয়ামিন(G)। কিন্তু উনি
ক্রোমোজমের নিউক্লিক অ্যাসিডের সঠিক কাঠামো বলতে পারেন নি। ১৯২৯ সালে
ডি-এন-এ বা ডি-ওক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড আবিষ্কার করার পরে উনি দাবী
করেন যে এটি মাত্র চারটি নিউক্লিওটাইড নিয়ে গঠিত (ছবিতে লিভানের প্রস্তাবিত
গঠন)।

লেভেনের এই আবিষ্কার ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটা ব্যাপার তখন বিজ্ঞানীদের
কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে বংশগতির বাহক যাহেতু খুবই জটিল বার্তা বহন
করে, তাই তার রাসায়নিক কাঠামোও জটিল হবে। লেভেনের আবিষ্কারের পরে বোঝা গেল
ডি-এন-এ এর কাঠামো এই জটিল বার্তা ধারণের পক্ষে উপযোগী হবে না। তাই
বিজ্ঞানীরা মনে করতে থাকলেন প্রোটিনই হবে সেই বার্তাবাহক। ২০ রকমের বিভিন্ন
অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরী বলে প্রোটিনের বিভিন্ন রূপ ধারণ করা সম্ভব আর
বার্তা বহনের কাজও করা সহজ। অপরদিকে, মাত্র চারটে ভিন্ন ধরণের রাসায়নিক
দিয়ে তৈরী চার শৃঙ্খলার অণু কিছুতেই অত জটিল বার্তা বহন করতে পারে না।
এই ভুল ধারণা আরো অনেক দিন রয়ে যেত, যদি না আরেক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী
পরীক্ষাগারে এক অঘটন না ঘটিয়ে ফেলতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে নিউমোনিয়ার
প্রতিষেধক আবিষ্কারের চেষ্টায় ফ্রেডেরিক গ্রিফিথ
গবেষণা করছিলেন নিউমোকক্কাস ব্যাকটেরিয়া নিয়ে। এই ব্যাকটেরিয়া দুধরণের
- একটা মারাত্মক ধরণের আরেকটা নির্বিষ। প্রথম ধরণের ব্যাকটেরিয়াকে বলা হত
S(Smooth) আর দ্বিতীয়টিকে R(Rough)। এই S ব্যাকটেরিয়া ইঁদুরের শরীরে প্রবেশ
করালে তার দ্রুত মৃত্যু হত। কিন্তু R ব্যাকটেরিয়া কোনো ক্ষতিই করতে পারত
না। দেখা গেল, S ব্যাকটেরিয়ার কোষের বাইরের দিকে উপস্থিত একটি বিশেষ
পদার্থের আচ্ছাদন কোষকে রক্ষা করত, R ব্যাকটেরিয়ার কোষে এরকম কিছু ছিল না।
এবার উনি কিছু মৃত S ব্যাকটেরিয়া ঢুকিয়ে দেখলেন ইঁদুর মরে না। সবশেষে মৃত S
ব্যাকটেরিয়ার সাথে সাথে R ব্যাকটেরিয়া ঢুকিয়ে দিয়ে দেখা হল। কিন্তু
গ্রিফিথকে অবাক করে দিয়ে ইঁদুরটা মরে গেল (ছবিতে)। কি ভাবে মৃত
ব্যাকটিরিয়াগুলো বেঁচে উঠে ইঁদুরটাকে মেরে দিল? দুই ভিন্ন ধরণের
ব্যাকটেরিয়া কি ভাবে ষড়যন্ত্র করে মেরে ফেলল ইঁদুরটাকে? মৃত ইঁদুরের শরীর
থেকে সংগৃহীত ব্যাকটেরিয়াগুলো দেখা গেল সব S ব্যাকটেরিয়া। এর মানে জিনগত
ভাবে বদলে গেছে ব্যাকটেরিয়া। কিন্তু কি ভাবে এরকম হল? মানবসভ্যতার ইতিহাসে,
চোখের সামনে প্রজাতির রূপ পরিবর্তন করা আগে দেখা যায় নি। গ্রিফিথই প্রথম সে
সৌভাগ্য অর্জন করলেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, কি ভাবে এটা ঘটে? মৃত ব্যাকটেরিয়া
থেকে কি এমন উপাদান সংগ্রহ করে জীবন্ত ব্যাকটেরিয়াগুলো যাতে তারা রূপ
পরিবর্তন করতে পারে?

সেই সূত্র উদ্ঘাটন করলেন
অসয়াল্ড আভেরী, অনেক পরে, ১৯৪৪ সালে সেই রকফেলার ইন্সটিটিউটেই (ছবিতে)।
উনি বিজ্ঞানী ম্যাকলয়েড আর ম্যাককার্টির সাথে মিলে প্রমাণ করে দিলেন যে
উপাদান সংগ্রহ করে এই রূপান্তর ঘটে তা হল ডিএনএ।
 গ্রিফিথ
যে কাজটা মৃত S ব্যাকটেরিয়া দিয়ে করেই বিস্মিত হয়েছিলেন, সেটাকেই এই
বিজ্ঞানীরা কয়েক ভাগে ভেঙে নিলেন। প্রথমে মৃত S ব্যাকটেরিয়াগুলোর বাইরের
আচ্ছাদন সরানো হল আর তারপরে আগের প্রক্রিয়া চালানো হল - তাতেও রূপান্তর হল।
তার মানে বাইরের আচ্ছাদনের কোনো ভূমিকা নেই রূপান্তরে। একই ভাবে উনি এর পরে
একে একে মৃত S ব্যাকটেরিয়াগুলো থেকে প্রোটিন ও আর-এন-এ সরিয়ে দিয়ে দেখলেন
রূপান্তর হচ্ছে। সবশেষে ডি-এন-এ কোষ থেকে সরিয়ে দিতেই দেখা গেল আর কোনো
রূপান্তর হচ্ছে না। তার মানে গল্পটা এরকম দাঁড়ালো - মৃত S ব্যাকটেরিয়াগুলোর
ডি-এন-এ জীবিত R ব্যাকটেরিয়াগুলো গ্রহণ করে পরিবর্তিত হচ্ছে - নতুন রূপ
ধারণ করছে। তার মানে, ডি-এন-এই হল জীবের বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক - অন্য
কথায় ডি-এন-এ জিনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।
গ্রিফিথ
যে কাজটা মৃত S ব্যাকটেরিয়া দিয়ে করেই বিস্মিত হয়েছিলেন, সেটাকেই এই
বিজ্ঞানীরা কয়েক ভাগে ভেঙে নিলেন। প্রথমে মৃত S ব্যাকটেরিয়াগুলোর বাইরের
আচ্ছাদন সরানো হল আর তারপরে আগের প্রক্রিয়া চালানো হল - তাতেও রূপান্তর হল।
তার মানে বাইরের আচ্ছাদনের কোনো ভূমিকা নেই রূপান্তরে। একই ভাবে উনি এর পরে
একে একে মৃত S ব্যাকটেরিয়াগুলো থেকে প্রোটিন ও আর-এন-এ সরিয়ে দিয়ে দেখলেন
রূপান্তর হচ্ছে। সবশেষে ডি-এন-এ কোষ থেকে সরিয়ে দিতেই দেখা গেল আর কোনো
রূপান্তর হচ্ছে না। তার মানে গল্পটা এরকম দাঁড়ালো - মৃত S ব্যাকটেরিয়াগুলোর
ডি-এন-এ জীবিত R ব্যাকটেরিয়াগুলো গ্রহণ করে পরিবর্তিত হচ্ছে - নতুন রূপ
ধারণ করছে। তার মানে, ডি-এন-এই হল জীবের বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক - অন্য
কথায় ডি-এন-এ জিনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।
কিন্তু দুঃখের বিষয় আভেরীর মত সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হল না। আভেরী,
ম্যাকলয়েড আর ম্যাককার্টি - কেউই কোনোদিনও নোবেল পুরষ্কার পেলেন না। (অনেক
পরে বাংলাদেশে কলেরা নিয়ে গবেষণাকেন্দ্রের প্রধানরূপে নিযুক্ত হলেন
ম্যাকলয়েড । বাংলাদেশের সেই কলেরা গবেষণা কেন্দ্র এখন পরিচিত
ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডায়েরিয়া ডিসিসেস রিসার্চ নামে।) ততদিনে প্রোটিন
নিয়ে বংশগতির ধারণা বিজ্ঞানীদের মধ্যে এতটাই গেঁথে গেছে যে অনেক বিজ্ঞানীই
তার মত পাত্তাই দিলেন না। এই পাত্তা না দেবার দলে ছিলেন সুইডিশ রসায়নবিদ
এইনার হ্যামারস্টেনও। কিন্তু হ্যামারস্টেন আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে
বসলেন (সূত্র - জেমস ওয়াটসনের ডি-এন-এ বইটি), নোবেল কমিটিতে আভেরীর
নমিনেশনের বিরোধিতা করলেন। পঞ্চাশ বছর পরে নোবেল আর্কাইভ থেকে জানা গেল এই
নির্মম সত্য। মজার কথা, হ্যামারস্টেন নিজেও কিন্তু ডি-এন-এ নিয়েই কাজ করতেন।
অথচ তিনি ঘুণাক্ষরেও টের পাননি এর কি মহিমা হতে পারে। উনি আর বেশীরভাগ
বিজ্ঞানীর মত মনে করলেন প্রোটিনই হবে বোধহয় বংশগতির বাহক। আর এর ফলে নোবেল
পুরষ্কার থেকে বঞ্চিত হল একটি মৌলিক গবেষণা ও গবেষক। ডি-এন-এ-এর প্রকৃত
কাঠামো জানা যাবার কয়েক বছরের মধ্যেই উনি মারা যান। জেমস ওয়াটসন তার বইতে
লিখেছেন - হয়ত আর কয়েক বছর বাঁচলে উনি নোবেল পুরষ্কার পেয়েই যেতেন। আরেক
নোবেলজয়ী জীববিজ্ঞানী আর্নে টিসেলিয়াসের মতে নোবেল না জেতা বিজ্ঞানীদের
মধ্যে আভেরীই ছিলেন সবথেকে যোগ্য বিজ্ঞানী।
অনেকসময়েই বিজ্ঞানের একাধিক শাখা একে অপরের সাথে জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে
সমৃদ্ধ হয়। কিন্তু আজকের স্পেশালাইজেশনের যুগে দেখা যায় ক্রস-ডিসিপ্লিন
নলেজ বা একাধিক শাখায় দক্ষ লোকের সংখ্যা কমেই চলেছে। তবে যখনকার কথা বলছি,
তখন এই সমস্যাটা এত গভীর ছিল না। তাই জ্ঞান বিনিময়ের জন্য বিজ্ঞানীদের অভাব
হত না। তাও কিছু কিছু বিজ্ঞানী এদের মধ্যে আলাদা করে জায়গা করে নিতে পারেন।
আর কেউ কেউ পারেন এক শাখার বিজ্ঞানীদের অন্য শাখায় উৎসাহিত করে তুলতে।
শেষোক্ত কাজটিই করেছিলেন অস্ট্রিয়ান নোবেলজয়ী পদার্থবিদ
এরুইন শ্রোডিংগার।
 শ্রোডিংগার
কিন্তু সম্পূর্ণরূপে একজন নিবেদিতপ্রাণ পদার্থবিদই ছিলেন। ১৯৪৩ সালে
ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে উনি বক্তৃতা দিতে গিয়ে জানালেন যে বিষয়বস্তু
পদার্থবিদ-দের অতি পরিচিত গাণিতিক সমীকরণের খুব একটা ধার ধারে না। এই
বক্তৃতাটিতেই উনি প্রথম জীবন ও তার অর্থ বোঝার জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা
বলেন। এরপরে, ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত "হোয়াট ইস লাইফ" নামক তার বইতে তিনি
লিখেছিলেন যে জীবনের উদ্দেশ্য হল কিছু তথ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ আর প্রবাহ। এভাবে
ক্রোমোসম হল এই তথ্যের ধারক। বংশানুক্রমিক ভাবে আসা এই তথ্য ক্রোমোসমের
জটিল অণুদের বিন্যাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। তাই জীবন কি সেটা বুঝতে গেলে আগে
ওই বিন্যাস বুঝতে হবে। এটাই ছিল তার মূল বক্তব্য।
শ্রোডিংগার
কিন্তু সম্পূর্ণরূপে একজন নিবেদিতপ্রাণ পদার্থবিদই ছিলেন। ১৯৪৩ সালে
ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে উনি বক্তৃতা দিতে গিয়ে জানালেন যে বিষয়বস্তু
পদার্থবিদ-দের অতি পরিচিত গাণিতিক সমীকরণের খুব একটা ধার ধারে না। এই
বক্তৃতাটিতেই উনি প্রথম জীবন ও তার অর্থ বোঝার জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা
বলেন। এরপরে, ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত "হোয়াট ইস লাইফ" নামক তার বইতে তিনি
লিখেছিলেন যে জীবনের উদ্দেশ্য হল কিছু তথ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ আর প্রবাহ। এভাবে
ক্রোমোসম হল এই তথ্যের ধারক। বংশানুক্রমিক ভাবে আসা এই তথ্য ক্রোমোসমের
জটিল অণুদের বিন্যাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। তাই জীবন কি সেটা বুঝতে গেলে আগে
ওই বিন্যাস বুঝতে হবে। এটাই ছিল তার মূল বক্তব্য।
এদিকে একই সময়ে পদার্থবিদেরা কোয়ান্টাম তত্ত্বের মত জটিল তত্ত্ব দিয়ে
পরমাণুর গঠন ও তাদের আচার আচরণ নিয়ে গবেষণা করছেন। অথচ, যা পরমাণুর চেয়েও
অনেক বেশী জরুরী তা হল আমাদের জীবন-কে বোঝা। তা নিয়ে গবেষকের আকাল।
ট্র্যাডিশনাল জীববিজ্ঞানীরা অধিকাংশই পর্যবেক্ষণ নিয়েই মগ্ন থাকেন, গাণিতিক
হিসাবনিকেশ করে দেখেন না বা পরিসংখ্যানেও ততটা দক্ষ নন। শ্রোডিংগারের বই
অনেক পদার্থবিদ ও রসায়ন-বিজ্ঞানীকেই এই জীবনের তথ্য উদ্ঘাটনের পথে আনতে
সক্ষম হল। মজার কথা, ডি-এন-এ আবিষ্কারের নাটকের কুশীলবদের অধিকাংশই এই বই
পড়েই জীবন নিয়ে গবেষণার পথে আসেন।
যেমন ধরা যাক
মরিস উইল্কিন্সের কথা। এই পদার্থবিদ পরমাণু বোমা তৈরীতে ম্যানহাটান
প্রজেক্টের সাথে জড়িত ছিলেন। বোমার আসল রূপ হিরোশিমা-নাগাসাকিতে দেখে তার
বোধোদয় হল। তিনি একরকম পাগল হয়েই প্যারিসে চলে যাবেন ভাবছিলেন - চিত্রকর
হবার শখে। এই সময়েই তার হাতে এসে পড়ে শ্রোডিংগারের বইটি। বই পড়ে উনি
উৎসাহিত হন জীবন সংক্রান্ত গবেষণায় আসতে। তিনিই সর্বপ্রথম এক্স-রে
ডিফ্রাকশন টেকনলজি ব্যবহার করে ডি-এন-এর গঠন পর্যবেক্ষণ করার কথা বলেন।
একজন পদার্থবিদ ছাড়া এই চিন্তা মাথায় আসা সাধারণ জীববিজ্ঞানীদের কাছে
অসম্ভব। আরেকজন ছিলেন
ফ্রান্সিস ক্রিক। যিনি মূলত ছিলেন পদার্থবিদ্যার ছাত্র কিন্তু তার
পদার্থবিদ্যার মত যুক্তিনির্ভর ও মডেল-ভিত্তিক গবেষণার অভ্যাসও এই ডি-এন-এর
গঠন আবিষ্কারে বড় ভূমিকা রাখে।