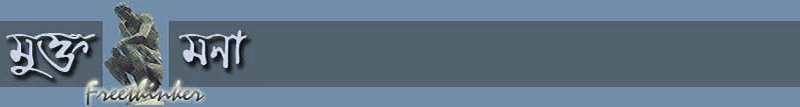
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||
|
|
|
ঈশ্বর ও বিজ্ঞান - "আছে" ও "নাই" প্রমাণের কথিত দ্বন্দ্ব নাস্তিকের ধর্মকথা আজকাল একটি কথা বেশ জোরে শোরে শুনা যায়। আস্তিকতার মত নাস্তিকতাও নাকি একধরণের বিশ্বাস। বিজ্ঞান যেমন বলে না “ঈশ্বর আছে” তেমনি সে এটাও বলে না যে “ইশ্বর নেই”। নাস্তিকরা যখন জিজ্ঞেস করে “ঈশ্বর আছে যে দাবী করছো, কর দেখি তার প্রমাণ”, তখন আস্তিকেরা পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দেয়, “ঈশ্বর নেই এটা দেখি কেমন প্রমাণ করতে পারো?” যেমন সেদিন একজনের সাথে আলোচনা হচ্ছিলোঃ ::“নাস্তিকতাও তো একটা বিশ্বাস, নাকি?” ::এখানে বিশ্বাসকে কি অর্থে আপনি ব্যবহার করেছেন সেটির উপর নির্ভর করছে। (a+b)2 সমান যে a2+2ab+b2 হয়, এটিকেও যদি বলেন বিশ্বাস, তবে সে ধরণের বিশ্বাসের অর্থে বলতে রাজী আছি যে নাস্তিকতাও এক ধরণের বিশ্বাস। বৃষ্টির কারণ হিসাবে পানিচক্রের কথা বললে যদি বলেন এটাও বিশ্বাস- তবে সে ধরণের বিশ্বাসের অর্থে নাস্তিকতাকেও বিশ্বাস বলতে পারেন। আর, যদি বলেন ভুত-পেত্নীতে বিশ্বাস, বা তুকতাকে বিশ্বাস বা রাহু গিলে খাওয়ায় চন্দ্রগ্রহণ হয় এটাতে বিশ্বাস বা গ্রীক মিথের জিউসের কারণে বা মুসলিমদের মিকাইলের কারনে বৃষ্টি হয় এটাতে বিশ্বাস- এসব বিশ্বাসের অর্থে বলেন, তবে বলবো- নাস্তিকতা এ ধরণের বিশ্বাস নয়। আস্তিকতা হলো এ ধরণের বিশ্বাস, যার জন্য কোন যুক্তি প্রমাণ লাগে না এবং এটা একধরণের অন্ধত্বজনিত বংশানুক্রমিক বা যুগানুক্রমিক বিশ্বাস। ::বৃষ্টির কারণ পানিচক্র সেটা প্রমাণিত সত্য। নাস্তিকতা বা আস্তিকতা কোনটাই প্রমাণিত সত্য না, যদি হত তাহলে বিশ্বের সকল মানুষ পাণিচক্রের মত নাস্তিকতা/আস্তিকতাকে মেনে নিত। :: দেখুন আজ পানিচক্রকে প্রমাণিত সত্য বলছেন, কিন্তু একসময় কিন্তু মানুষ জানতো না বৃষ্টি কিভাবে হয়। কিন্তু মানুষ এর উত্তর জানতে চেষ্টা করেছে বারেবারে। একদিকে কৃষিজীবনে বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা, অন্যদিকে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষকে বৃষ্টির কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করেছে। ফলে, কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে কল্পনায় তৈরী করে নিয়েছে নানা মিথ। গ্রীক বা রোমান মিথে তাই দেখি দেবতারাজ জিউস বা জুপিটর নিজেই এই বৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করে। আবার ভারতীয় পুরাণে আমরা দেখি সূর্যকেই দেবতা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই সূর্যদেবের কারণে বৃষ্ট হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মে তেমনি মিকাইল নামক ফেরেশতা বৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই যে এসব নানারকম মিথ বা কল্পকাহিনী মানুষ ততদিনই বিশ্বাস করেছে যতদিন মানুষের কাছে বৃষ্টির কারণ হিসাবে পানিচক্রের কথা প্রমাণিত সত্য হিসাবে প্রতীয়মান হয় নি। এখনো হয়তো অনেকেই নানারকম কল্পকাহিনী বিশ্বাস করে, এখনো গ্রামে গঞ্জে অনাবৃষ্টি দূর করতে আল্লাহ মেঘ দে পানি দে বলে দলবেধে গেয়ে বেড়ায় গ্রাম্য মেয়েরা, এখনো দুনিয়ার অনেক স্থানে বৃষ্টির জন্য সূর্যের উদ্দেশ্যে বিশেষ পুজার ব্যবস্থা আছে; কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তাদের স্ব স্ব বিশ্বাস অনুযায়ী গান গেয়ে বেড়ালেই বা সূর্যদেবের বিশেষ পুজা করলেই বৃষ্টি আসবে। এখনো এ ধরণের বিশ্বাস টিকে থাকার কারণ মূলত দ্বিবিধঃ প্রথমত তাদের বড় অংশই এখনো জানে না বৃষ্টির প্রকৃত কারণ, এবং দ্বিতীয়ত দীর্ঘদিনের বংশানুক্রমিক অনুশীলন ও বিশ্বাস অনেক গভীরে গিয়ে বাসা বেঁধেছে। এখন প্রশ্ন হলো নাস্তিকতাও সে ধরণের কোন বিশ্বাস কি না? সে উত্তরে যাওয়ার আগে এর পক্ষে যুক্তি দেয়া কিছু আলোচনা দেখিঃ ::”আল্লাহ, তাঁর সৃস্ট জ্বিন, ফেরেশতা, বেহেস্ত, দোজখ কিছু আছে কি নেই সেই প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক উত্তরও “আছে” হওয়ার চেয়ে “নাই” হওয়া অধিকতর কঠিন। কারণ নাই বলতে হলে থাকার সম্ভাব্য সবগুলি দিক ও বিভাগ পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে তার পর বলতে হবে নেই। এজন্য আমাদের জানতে হবে বিলিয়ন বিলিয়ন আলোকবর্ষব্যাপী ছড়ান বস্তুজগত, আমাদের চতুর্মাত্রিক জগতের বাইরে অন্য মাত্রার কোন জগত আছে কি না, থাকলে সেই জগত এবং এ’সব জানতে গিয়ে আরো যত অজানা জগতের সন্ধান পাওয়া যাবে তার সব। তার আগে যদি কেউ “নেই” বলে তাহলে সেটা বিজ্ঞান হবে না হবে একটা বিশ্বাস“।
“যদি বিষয়টা এমন হত যে বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত যা জানে তাই সব-এর বাইরের সবকিছু নেই এবং এটাই বৈজ্ঞানিক সত্য- তাহলে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা বহু আগেই থেমে যেত। কারণ বিজ্ঞান সেই বিষয় নিয়েই গবেষনা করে যা আজও বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে প্রতিস্ঠিত হয়নি। কাজেই বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে পারেনি বলেই - বেহেস্ত, দোযোখ, জ্বিন, ফেরেস্তা কিছুই নেই এমনকি আল্লাহও নেই এ’কথা বলা নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক। বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে নেই বলতে হলে এই সৃস্টিজগতের সকল রহস্য-সকল জ্ঞান মানুষের আয়ত্বে আসতে হবে এবং সেই জ্ঞানের ভিত্তিতেই কেবলমাত্র সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে স্রষ্টা আছে কি নেই”। আশা করি ধীরে ধীরে এ আলোচনা অগ্রসর হতে হতে এসমস্ত প্রশ্নের একটা গ্রহণযোগ্য জবাব বা উত্তর পাওয়া যাবে।
বিজ্ঞানঃ খুব সংক্ষেপে বিজ্ঞান সম্পর্কে বলতে গেলে এভাবেই বলা যায়, প্রকৃতির তথা বস্তুজগতের নিয়ত পরিবর্তনের নিয়ম বা কার্যকরণ সূত্র সম্পর্কিত বিশেষ জ্ঞানই হলো বিজ্ঞান। আবার, বিজ্ঞানের একটি বিশেষ কর্মপদ্ধতিও আছে, যার মূল হলো যুক্তি ও প্রমাণ। এবারে সে আলোকেই দেখি আল্লাহ-ভগবান, ভুত-প্রেত, জ্বিন-পরী, দেব-দেবী, শয়তান-খোক্ষস এসব বিজ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত বিষয় কিনা? খুব ছোট করে এর উত্তর হলো “না”। বিজ্ঞান সেসমস্ত বিষয়েরই আলোচনা যা প্রমাণিত, বা যুক্তিতে অনুশীলনযোগ্য। সেই বৃষ্টির ঘটনাতেই আবার আসি। বৃষ্টি কেন হয়? বিজ্ঞানের একজন ছাত্রকে লিখতে হবে পানিচক্রের কথা। গাছ থেকে টুপ করে আপেলটি কেন নীচে পড়লো? এরো উত্তরে বলতে হবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা। চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ কেন হয়? এখানে বলতে হবে চন্দ্রের উপর পৃথবীর ছায়া বা সূর্য ও পৃথবীর মাঝখানে চন্দ্রের অবস্থানের কথাই বলতে হবে। মানব শিশুর জন্ম কিভাবে হয়? এর উত্তরে বলতে হবে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনে সৃষ্ট ভ্রূণের কথা। এভাবে বিজ্ঞানের সমস্ত শাখাই, পদার্থ, রসায়ন, উদ্ভিদ, প্রাণিবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান সমস্ত কিছুই এভাবে কার্যকরণ সূত্র বের করে গিয়েছে বা বের করার চেষ্টায় লিপ্ত। বিজ্ঞানের কোন শাখায় কোন অতিপ্রাকৃত কারণের কোন স্থান নেই। একজন হিন্দু ধর্মালম্বী বিশ্বাস করতে পারে যে রাহুর গ্রাসের কারণেই গ্রহণ হয়, কিন্তু বিজ্ঞানের ক্লাসে সে যদি সে তত্ত্ব জানায়, তবে তাকে কি বলা হবে? একজন বিশ্বাসী মুসলমান ভাবতেই পারে যে আল্লাহর নির্দেশে আযরাইল এসে জান কবজ করাতেই অমুক মারা গেছে। কিন্তু বিজ্ঞানের ছাত্র তার পরীক্ষার খাতায় সে কথা লেখলে শূণ্য ছাড়া কিছু পাবে না। কেননা, কোন মানুষ কি বিশ্বাস করে না করে, তার সাথে বিজ্ঞানের কোন যোগাযোগ নেই। মানুষের কল্পনাশক্তি ও এর সীমাবদ্ধতা মানুষের অসাধারণ দুটি গুণ হলো প্রশ্ন করার ক্ষমতা ও তার কল্পনা শক্তি। আইনস্টাইন বলেছেন, “ইমাজিনেশন ইজ মোর ইমপর্ট্যান্ট দ্যান নলেজ”। মানুষ তার চারপাশের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে জানতে চায়। জানতে চায় এর এসব ঘটনার পেছনের কারণ। শুধু জানতে চাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ সে থাকে না, এসব ঘটনার সাম্ভাব্য কারণও সে ভাবার চেষ্টা করে। এই ভাবনার মধ্যে সে তার কল্পনাশক্তির প্রয়োগ ঘটায়। এই চিন্তা বা ভাবনা থেকে যে বিষয়টি বেরিয়ে আসে, সেটি দিয়ে আবার সে তার চারপাশের ঘটনাসমূহকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে। আবার তৈরী হয় প্রশ্নের। আবারো ভাবনা এবং কল্পনাশক্তির প্রয়োগ। এভাবেই মানুষ এগুতে থাকে। বারেবারে তার চিন্তাশক্তিকে যাচাই বাছাই করে, বাস্তবতার নিরীখে মেপেজোকে আরো শানিত করে, শানিততর করে। এই তো মানুষের এগিয়ে চলা। কিন্তু মানুষের চিন্তাশক্তির তথা কল্পনাশক্তির একটা সীমাবদ্ধতাও আছে। তা হলো, সে তার একটা সীমার মধ্যে থেকেই কল্পনা বা চিন্তা করতে পারে। এই সীমা নির্ধারিত হয় তার অভিজ্ঞতা বা তার জ্ঞান দ্বারা। একটি উদাহরণ দিলে কিছুটা পরিষ্কার হতে পারে। কোন শিশুকে যখন একটা দৈত্যের চিত্র আঁকে, তখন সে ছবি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে দেখলে পাওয়া যাবে সেখানে চোখ-নাক-মুখ-কান-শিং-দাঁত সবই শিশুর পরিচিত গণ্ডীর উপাদান নানাভাবে সাজিয়েই তার দৈত্যটি এঁকেছে। দৈত্য তার কাছে বিমূর্ত বিষয়, প্রচণ্ড ভয়ের কিছু। তাই তার ভয় ছবিতে রূপান্তরিত হয় বের হয়ে আসা বড় বড় তীক্ষ্ণ দাঁত (যা রক্ত পান করে), বড় দুটি শিং, চোখ থাকলেও বড় বড়- রঙ্গের ব্যবহার থাকলে টকটকে লাল। এসমস্তই কিন্তু তার পরিচিত জগৎ থেকে ধার করা। অন্যভাবে বললে বলা যায় শিশুটি বিমূর্ত দৈত্যের ছবিটি আঁকতে গিয়ে যে কল্পনাশক্তির সমাবেশ ঘটালো সেখানে এমন একটি উপাদানও পাওয়া যাবে না যা তার অভিজ্ঞতায় নেই বা জ্ঞানে নেই। তাহলে এখানে এমাজিনেশনের পাওয়ারটা তাহলে কোথায় ব্যবহৃত হলো? ঐ যে, বিভিন্ন উপাদান গুলোকে মনের মতো করে গ্রহণ-বর্জন করতে ও সাজানোতে; পরিচিত উপাদানগুলোকে পরিচিত আকার থেকে একটু ভিন্ন রকম দেখাতে। এই যে ঘটনাটি, এটি শুধু শিশুদের সীমাবদ্ধতা নয়, এটি হলো সমগ্র মানুষেরই কল্পনাশক্তির লিমিটেশন। আপনারা যারা পড়ছেন, তারাও বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবেন। আপনারা এমন একটি কোন কিছুর কথা ভাবুন তো একটা জন্তু, বা দানব বা ভূত, ঈশ্বর, শয়তান বা এমন কিছু একটা, যার কোন একটি উপাদান আপনার পরিচিত গণ্ডীর বাইরে আছে। পারবেন না। এটা পারা সম্ভব না। যা পারবেন তা হলো চেনা গণ্ডীর নানা উপাদানকে বিন্যাস-সমাবেশে দারুন সব ইমাজিনেশন তৈরী করতে। এটি আরেকটি উদাহরণ দিয়ে শেষ করছি। একজন জন্ম বধির মানে যে কোনদিন কোন শব্দ শুনেনি- সে কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক বাকযন্ত্র থাকার পরেও কথা বলতে পারে না, মানে সে জন্ম থেকেই মুক। কারণ, যেহেতু সে কখনো শব্দ শুনেনি, শব্দ সংক্রান্ত কোন অভিজ্ঞতাও তার নেই। এক্ষেত্রে সে তার অভিজ্ঞতার বাইরে ইমাজিনেশন দিয়ে কোন শব্দ বা বাক্য উদ্ভাবন করতে পারে না। একজন জন্মান্ধ কি কখনো আলো সম্পর্কে, অন্ধকার সম্পর্কে, বিভিন্ন রঙ্গ সম্পর্কে কোনরূপ ইমাজিনেশন তৈরী করতে পারে? না। একেই বলা হচ্ছে, কল্পনাশক্তির সীমারেখা। মানুষের ঈশ্বর ভাবনা সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মানুষের যেমন অসাধারণ গুণ হলো সে এককটি সীমার মধ্য থেকে অনেক কিছুই ইমাজিন করতে পারে, তেমনি তার সীমাবদ্ধতা হলো এই সীমার বাইরে সে কিছুই চিন্তা করতে পারে। ফলে, সে যখন তার ঈশ্বর, দেব-দেবীকেও কল্পনা করে, সেটিও তার সেই সীমারেখাকে অতিক্রম করতে পারে না। ফলে, ঈশ্বর বা দেবদেবীও হয়ে ওঠে মানুষের চিরচেনা গণ্ডীর মধ্যে একজন আপনজন। শয়তানের ক্ষেত্রেও তাই। এভাবেই ঈশ্বর, দেবদেবী, শয়তানকে সেকারণে আমরা দেখি মনুষ্য ভাবাপন্ন। আরজ আলী সেটিকেই চমৎকার ভাবে জানান দেন, মানুষের মতই আল্লাহ দেখেন, শুনতে পান, মানুষের মতই তারও আসন আছে, তিনি সন্তুষ্ট হন, অসন্তুষ্ট হন। আরো আগে গেলে বাইবেলে দেখা যাচ্ছে ঈশ্বরের একটি সংসারো আছে, স্ত্রী মেরী ও পুত্র যীশু নিয়ে সুখের সংসার। আরো আগে গেলে দেবতারা অবিকল মানুষের মতই সমস্ত দোষ-গুণের অধিকারী, পার্থক্য শুধু তারা মরণশীল নন এবং প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করেন। দেবতারাজ্য যেন মনুষ্য রাজ্যেরই অপরনাম, সেখানে দেবতারাজও আছেন। দেবতাদের মানুষের মত যুদ্ধ-বিগ্রহ, সংসার-যৌনতা, সন্তান-সন্ততি সবই সম্ভব। গ্রীক/রোমান মিথলজি বা এখানকার ভারতীয় পুরানের দেবতারা মর্তেও অহরহ নেমে আসতেন এবং মানুষের সাথে বন্ধুত্ব, শত্রুতা, যুদ্ধ, প্রেম-ভালোবাস সবই করেছেন। রাবনের যে দশ মাথা বা দেবী দুর্গার যে দশহাত কল্পনা করেছে মানুষ, সেখানেও কিন্তু অতিকল্পন নেই। একজন শিশু যেমন তার কল্পনায় ভয়ঙ্কর কিছু আঁকতে গেলে দাঁতটি অনেক বাড়িয়ে দেয় ও তীক্ষ্ণ করে, তেমনি মানুষও কল্পনায় অত্যন্ত বুদ্ধিসম্পন্ন কল্পনা করতে গিয়ে দশ মাথা কিংবা অত্যন্ত কর্মঠ-কর্মপটিয়সী কল্পনা করতে গিয়ে দশহাত চলে এসেছে। মানুষের ইতিহাসে মানুষের এই অতিপ্রাকৃত চিন্তা বা কল্পনাগুলোকে একের পর এক সাজালে একটি ধারাবাহিকতা পাওয়া যায়। সে ধারাবাহিকতায় দেখি দেবতা-ইশ্বর-শয়তান এসবের ক্ষমতা, অতিপ্রাকৃততা এসব দিনে দিনে বেড়েছে। অর্থাৎ দিনে দিনে মানুষের চিন্তাজগৎ যত উন্নত হয়েছে, তার কল্পনাশক্তিও ততই বিকশিত হয়েছে। প্রথমদিকের ধর্মাচরণে মানুষকে দেখা যায় স্থানীয় বা লোকালাইজড এক বা একাধিক (অল্প সংখ্যায়) দেবদেবীর উপাসনা করতে, এক এলাকার সাথে পাশের এলাকার হয়তো উপাস্যের ভিন্নতা কিংবা দুটি এলাকার একই উপাস্যের গুনাগুনের ভিন্নতাও উল্লেখযোগ্য। আজো আমরা এখানে দেখি কোন অঞ্চলে দুর্গা পুজা, কোথাও কালী পুজার আবার কোথাও বা লক্ষী পুজার চল বেশী। এরপরে মানুষের মধ্যে যখন আদান-প্রদান বাড়ে, মানুষ যখন এলাকা থেকে এলাকান্তরে নানাকারণে একেঅপরে যোগাযোগ শুরু করে, তখন পারষ্পরিক দেবদেবীর আদান-প্রদান, গ্রহণ-বর্জনের কাজটিও ঘটতে থাকে। এভাবেই মানুষের কল্পনায় দেবদেবীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। এসব দেবদেবীই কিন্তু একেকজন ঈশ্বর। ইংরেজীতে দেবতা হলেন গড আর দেবী হচ্ছেন গডেস। ভারতীয় মিথ পড়লেও দেখা যায়, মহাভারতে সামনাসামনি বিভিন্ন দেবতা তো বটেই এমনকি মুনী ঋষিদেরও ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়েছে। কখনো রাজাকে প্রজারা ভগবান সম্বোধন করেছে, আবার রাজন্যবর্গ ব্রাহ্মণ মুনীকে ভগবান সম্বোধন করেছেন। আবার দেবতারা দেবরাজ ইন্দ্রকে, ইন্দ্রসহ দেবদেবীরা ব্রহ্মাকে বা নারায়নকে বা বিষ্ণুকে ভগবান সম্বোধন করেছে। যাহোক, যেটা বলছিলাম প্রাচীণ এসব দেবদেবী বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার অংশ হিসাবেই কিন্তু তৈরী হয়েছে। জিউস (জুপিটর) নভোমণ্ডল, বৃষ্টি ও মেঘের দেবতা, পোসাইডন (নেপচুন) সাগরের দেবতা, হেডিস (প্লুটো) ঘর-গৃহস্থালির দেবী, হেরা (জুনো) বিয়ে ও জন্মের দেবী, অ্যারেস (মার্স) যুদ্ধের দেবতা, অ্যাথেনা (মিনার্ভা) জ্ঞান, যুক্তি, শিল্প ও শুদ্ধতার দেবী, আফ্রোদিতি (ভেনাস) প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী। এখন আমরা যদি দেখি এই যে দেবদেবীর বর্ণনা সমস্তই কিন্তু মানুষের জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে। দেবতারাজ জিউস কিন্তু মহাকাশ ও মেঘ-বৃষ্টির অধিপতি, জন্ম-সৃষ্টির নন। এর মানে এই যে, সে আমলে মানুষের কাছে মেঘ-বৃষ্টির গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। (প্রাচীণ গ্রীসে জিউস ও রোমে জুপিটর সবচেয় বেশী পুঁজিত হতেন, পরবর্তী শিল্পে-সাহিত্যে ভেনাস/আফ্রোদিতি, অ্যাপোলো, অ্যারেস এসব দেবদেবীকেও গুরুত্বের আসনে বসানো হয়)। একইভাবে ভারতীয় মিথে আমরা ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু, ইন্দ্র বা মহামায়া দুর্গা, কালী, লক্ষী, সরস্বতী, গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীকেও আমরা মানুষের বিভিন্ন বিষয়-আশয়কে নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে দেখি। এক সময়কার মানুষ গ্রীক রোমান এসব মিথের দেবদেবীর প্রতি সম্পূর্ণ আনতই ছিল, বিশ্বাসের এতখানি কমতি ছিল না, এখনো কেউ কেউ এসবে বিশ্বাস রাখতে পারে, ভারতীয় দেবদেবীর উপর বিশ্বাস এখনো অনেকেই পোষণ করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আসলেই কি এসব দেবদেবী বলে কিছু আছে বা ছিল? না-কি মানুষ এসবকে তাদের কল্পনায় তৈরী করে নিয়েছে? সম্ভবত একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, মানুষই এসব দেবদেবীকে চিন্তায় বা কল্পনায় তৈরী করে নিয়েছে। শুরুতে এই কল্পনায় এসব দেবদেবীকে সৃষ্টি করাটা ছিল মানুষের চিন্তাশক্তিরই বহিপ্রকাশ। বৃষ্টি কিভাবে হয়, যুদ্ধে জিতবো-না হারবো, ফসল হবে কি হবে না, ধন-সম্পদ বাড়বে কি না, জন্ম হয় কিভাবে এসব নানা প্রশ্নের জবাব মানুষ এইসব কল্পনাতে পেয়েছে। কিন্তু এই কাল্পনিক দেবদেবী উদ্ভবেরো আগের পিরিয়ডটি হলো প্রকৃতি-পুঁজার। সেখানে ঈশ্বর হচ্ছে স্বয়ং সূর্য, বিশাল ও পুরাতন কোন বৃক্ষ, বড় পাথর, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র, তারা প্রভৃতি। সেখানেও আছে কল্পনার মিশেল ও মানুষের প্রশ্নের জবাব খোঁজার আকাঙ্খা। একই সূর্য কখনো উত্তাপ দিয়ে সব পুড়িয়ে ফেলে, কখনো তার অভাবে সবকিছু কেমন বরফ শীতল হয়ে যায়, এই যে একসূর্যের নানা রূপ এর কারণ কি? কিভাবে সূর্যের নিয়মিত রৌদ্রজ্জল দিনগুলো পাওয়া সম্ভব? সূর্যকে খুশী করতে হবে। শুরু হলো সূর্য পুঁজা। এই যে সূর্যকে খুশী করতে হবে এই কল্পনা কিন্তু এসেছে, মানুষের পারষ্পরিক সম্পর্কের ধারণা থেকেই। এভাবেই প্রথমে প্রকৃতিকেই ঈশ্বর জ্ঞান করা, তারপরে প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনার কারণ ও মানুষের জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে দেবদেবীর ধারণা, তারোপরে দেবদেবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেব-দেবী নির্বাচন বা দেবরাজা, দেবীরানী নির্বাচন এসবই কিন্তু ধারাবাহিক। মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কাঠামোর সাথে এসব কল্পজগতের পরিবর্তনের একটা সরাসরি সম্পর্ক আছে। মানুষ যখন অপর মানুষের উপর কর্তৃত্ব/নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে তারপরেই সে দেবদেবীর কল্পনা করতে পারে, তার আগে সে প্রকৃতি বিভিন্ন উপাদানেরই উপাসনা করতো। মানুষের মধ্যে যখন গোত্রপ্রধান, রাজ্য প্রধান বা রাজা এসব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই সে দেবতাদের মধ্যে রাজার তথা দেবরাজের কথা কল্পনা করতে পারে। কিন্তু শুরুর দেবরাজ দেখা যায়, সর্বশক্তিমান নয়। সে যুদ্ধে যেমন জিতে তেমনি হারেও। এরপরে ধীরে ধীরে মানুষের রাজ্যপ্রধান বা রাজা যতই শক্তিশালী হতে থাকে, সাম্রাজ্যের পর্যায়ে যায়, সম্রাটের অধীনে অনেক রাজা সম্রাটেরই অনুগত- তখন দেখা গেলো দেবতাদের মধ্যেও একজন দেবরাজ হয়ে উঠে অনেক শক্তিশালী, সর্বশক্তিমান। যে জিউস একসময় আকাশ নিয়ন্ত্রণ করতো, মানুষের জন্য মেঘ-বৃষ্টির ব্যবস্থা করতো; একসময় তাকে দেখা গেলো দেবরাজ হতে, কিন্তু একটা সময় পর্যন্ত তাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে পাওয়া যায়নি- হেরা সহ বিভিন্ন দেবদেবীর কাছে তাকে পরাভূত হতে দেখা যায়; কিন্তু আরো পরে একসময় দেখা গেল সেই জিউসই হয়ে উঠে সর্বশক্তিমান, অপ্রতিরোধ্য, ইলিয়াডে তাই আমরা দেখি জিউস পরীবর্গকে বলেন, “আমি সর্বশক্তিমান। একটি স্বর্ণের রজ্জু বেঁধে দাও স্বর্গের সাথে এবং তা ধরে রাখুক সকল দেব-দেবী। কেউ জিউসকে টেনে নামাতে পারবে না। কিন্তু আমার যদি ইচ্ছা হতো কাউকে টেনে নামানোর তবে তা আমি করতেই পারতাম”। এভাবে মনুষ্যরাজত্বের সাথে মিলিয়ে মানুষের ঈশ্বর চিন্তা নিয়তই পাল্টিয়েছে। আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্য, টলেমির সাম্রাজ্য প্রভৃতির একচ্ছত্র বিস্তৃতি মানুষের ঈশ্বর চিন্তায় বড় পরিবর্তন ঘটায়। সেই দেবরাজ এখন দেবতারাজ হয়েই শুধু থাকেন না, তার সাথে অন্য দেবদেবীর স্পষ্ট পার্থক্য তৈরী হয়। এই দেবরাজ এখন বিশ্বপ্রকৃতি ও মানুষই নিয়ন্ত্রণ করে না, অন্য দেবতাদেরো নিয়ন্ত্রণ করেন। এভাবেই একেশ্বরের ধারণার শুরু। নতুন এই দেবরাজ বা ঈশ্বর এখন অনন্য, অন্য দেবতাদের গুরুত্ব কমতে কমতে তারা দেবতা নামও হারিয়ে হয়ে যায় এনজেল, ঈশ্বরের সহযোগী, সাহায্যকারী। যদিও আগের মতই তারা এখনো বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করে, মৃত্যু ঘটায়, ফসল ফলায় ইত্যকার নানাকাজে নিয়োজিত থাকে; তারপরেও আগের তুলনায় একটি মৌলিক পরিবর্তন ঘটে যায়, তা হলো এসমস্ত কর্ম এখন তারা করে ঈশ্বরের ইচ্ছায়, নির্দেশে। যেমন করে একজন সম্রাটের বিভিন্ন বিভিন্ন পাইক-পেয়াদা, সভাসদ, মন্ত্রী-আমলা সম্রাটের ইচ্ছায় সাম্রাজ্য পরিচালনার নানাকাজে অংশ নিয়ে থাকে। মানুষের চিন্তাজগতের আরো কিছু পরিবর্তনও দেখা যায়। ঝড়-বৃষ্টির ঘটনা, জোয়ার-ভাটা, দিবা-রাত্রি সংগঠন এসবের কিছু কিছু কারণও সে উদ্ধার করা আরম্ভ করে; উল্টোদিকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ, মানব জন্ম এসব অনেক বড় রহস্য হিসাবে মানুষের জীবনে এসে দেখা দিল। ফলে, আগে যেমন দেবতারাজ জিউস ছিল মেঘ-বৃষ্টির দেবতা; এখনকার ঈশ্বর হয়ে গেল সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। আমি এ আলোচনাটি করছি খৃষ্টপূর্ব ৫০০ থেকে খৃস্টপূর্ব ৩০০ পর্যন্ত সময়কালটির কথা। সে সময় গ্রীসে পীথাগোরাস, পার্মেনিডিস, ডিমোক্রিটাস, হিপক্রেটিস, সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল প্রমুখ চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানী, দার্শনিক নানাভাবে মানুষের চিন্তাজগতকে প্রভাবিত করেন। প্লেটোর গাণিতিক ভাববাদ, এরিস্টটলের অধিবিদ্যা ও থিওলজি যে যুক্তির উপর ভিত্তি পায়, সেটিই ক্রমশঃ মজবুত হয়ে ও কিছু পরিবর্তিত-পরিবর্ধিত হয়ে পরবর্তী আবির্ভুত ধর্মসমূহে স্থান পায় বা পরবর্তী ধর্মসমূহের ঈশ্বরকেন্দ্রিক ধারণা গড়ে তুলতে সহায়তা করে। ঈশ্বর বিশ্বাসের বংশানুক্রমিকতাঃ
এতক্ষণের
আলোচনায় আশা করি মানুষের ঈশ্বর ভাবনার
উৎপত্তি
ও বিবর্তন সম্পর্কে কিছু ধারণা পেয়েছেন।
এবারে
দেখি সেই ভাবনাগুলো কিভাবে
মানুষ
ধীরে ধীরে আকড়ে ধরে।
মানুষ
এই ঈশ্বর ভাবনাগুলো তার কল্পনাশক্তি অনুযায়ী
সৃষ্টি
ও পরিবর্তন যে করে,
সেটি
কিন্তু সবসময়ের সমস্ত মানুষের জন্য সাধারণ ঘটনা নয়।
একটা
সময়ে মানুষ কোন বিশেষ ধারণাকে গ্রহণ করার পরে,
সেটার
প্রসার ও প্রচার ঘটে।
কোন
একটা
অংশের মানুষ যখন এটিকে আকড়ে ধরে,
তখন
ধীরে ধীরে সেটি বংশানুক্রমিকভাবে
প্রজন্মান্তরে ভ্রমণ করতে থাকে।
নতুন
নতুন শিশু এরপরে জন্মের পর থেকে সে ধারণার
মধ্যে
বেড়ে ওঠে,
ফলে
সেই ধারণা তার মধ্যে বিশ্বাসের রূপ নেয়।
এভাবে
একসময় যে ঈশ্বর
চিন্তা
ছিল মানুষের কল্পনাশক্তির বহিপ্রকাশ কালে তাই হয়ে পড়ে বিশ্বাস বা অন্ধ
বিশ্বাসের আরেক নাম।
সেখানে
আর যাচাই বাছাই গ্রহণ-বর্জনের কোন উপায় থাকে না।
আর,
মজার
ব্যাপার হলো এ এমন এক চক্র যে,
এক
প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম এভাবেই এই
ধারণাটিকে বয়ে নিয়ে চলে,
কেউ
জানেনা এই ধারণাটির পক্ষে কোন যুক্তি আছে কি না,
প্রমাণ
আছে কি না;
তারপরেও চলতে থাকে অবিরাম।
গৌতম
বুদ্ধ তাই বলেছেন, অজ্ঞতা, অসহায়তা, দুর্বলতা বনাম ঈশ্বরঃ এর আগের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, ঈশ্বরের ধারণা মানুষের অজ্ঞতা থেকে শুরু। মানুষ যখন কোন ঘটনার ব্যাখ্যা জানে না, কার্যকারণ সূত্র কি সেটা জানে না- তখন একজন কল্পিত ঈশ্বর বা কল্পিত কারণ কল্পনা করে নিয়ে নিজেকে প্রবোধ দিতে চেয়েছে। মানুষ যখন অসহায়-দুর্বল অবস্থায় পড়ে এবং সেখান থেকে বেড়ুনোর পথও সে খুঁজে পায় না তখনই সে কাল্পনিক ঈশ্বরে নির্ভর করে মানসিক বল পেতে চায়। মানুষের স্বাভাবিক কথোপকথনেও এটি দেখা যায়। যখন মানুষ কোন কিছু না জানে, তখন বলে ফেলে আল্লাহই জানে। যখন অসহায়, দুর্বল এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, তখন শেষ ভরসা হিসাবে ইশ্বরকে জপ করা আরম্ভ করে দেয়। হঠাৎ চমকে উঠলে, ভয় পেলে- বলে ওঠে “হায়! আল্লাহ!” বা “ওহ! মাই গড!” কিংবা “রাম! রাম!” ইত্যাদি। শিশুকে ঘুম পাড়ানোর জন্য অনেকেই ভূতের গল্প শোনান, ফিস ফিস গলায় জানানঃ “বাইরে এক ভূত আছে, সে রাতের বেলা ঘুরে ঘুরে বেড়ায় আর বাচ্চাদের খুঁজে বেড়ায়। যখনই কোন বাচ্চা না ঘুমিয়ে কান্নাকাটি করে বা জোরে কথা বলে, সেই ভূত টের পেয়ে যায় আর বাচ্চাটাকে ধরে নিয়ে যায়”। কোথায় ধরে নিয়ে যায়, ধরে নিয়ে কি করে এ প্রশ্নগুলো করার মতো সাহসটুকুও আর ঐ শিশুটির থাকে, দম বন্ধ করে চুপচাপ থাকে, একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। ঈশ্বরে বিশ্বাস সেরকমই শিশুসুলভ বিশ্বাস, যা পরকালের কথিত শাস্তির ভয় দেখায়, মানুষ প্রশ্নটুকু করার সাহস হারিয়ে ফেলে। তাইতো আইনস্টাইন ১৯৫৪ সালে Eric Gutkind কে লিখিত এক পত্রে জানাচ্ছেন, “The word God is for me nothing more than the expression and product of human weaknesses, the Bible a collection of honourable, but still primitive legends which are nevertheless pretty childish.” বিজ্ঞান সৃষ্টি করে না, করে উদ্ভাবনঃ অনেকেই বলে থাকেন, বিজ্ঞান কিছু সৃষ্টি করে না, সৃষ্ট জিনিসগুলো উদ্ভাবন করে মাত্র। এটা ঠিক। বিজ্ঞানের কাজ সৃষ্টি করা নয়, সৃষ্টি করার দরকারো নেই। বিজ্ঞান হলো মানুষের আহরিত জ্ঞান। বিজ্ঞান আমাদের জানায় প্রকৃতির নিয়মাবলী, বস্তুজগতের পরিবর্তনের নিয়মাবলী, কার্যকরণ সূত্র। সে নিত্য এই বিশ্বজগতের অভ্যন্তরীন নিয়ম উদ্ভাবনের চেষ্টায় লিপ্ত। এ ধরণের ব্যাখ্যা ধর্মসমূহও দেয়ার চেষ্টা করেছে, সে জায়গা থেকে নানাবিধ দেবতত্ত্ব তথা ঈশ্বরতত্ত্বও তৈরী হয়েছে এবং একটা সময় পর্যন্ত সেগুলো মানুষের চিন্তাজগতে রাজত্বও করেছে। কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে সেসবের কানাকড়ি গুরুত্ব আজ নেই। “আছে” ও “নাই” এর দ্বন্দ্বঃ
ধরেন,
এক ওঝা
দাবী করলো যে তার সাথে এক ভূত থাকে।
অপর
ব্যক্তি সেটা বিশ্বাস করলো না। এই ওঝার মত করে অনেকে এইরকম যুক্তি করতে থাকে। ফলে, বুঝুন এইভাবে যুক্তি করে কত সহজেই ভূত-প্রেত, দেও-দানব, আল্লাহ-ভগবান, ফেরেশতা-জ্বিন, পরী-হুর সবকিছুই আছে দাবী করা যায়! একে বলে বাঁকা যুক্তি। আসলে, আস্তিকেরা জানে যে, তার ঈশ্বর বিশ্বাসের পেছনে কোন যুক্তি নেই, সেটা শুধু বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাসের জোরেই তারা দাবী করে যে ঈশ্বর আছে। তাই আস্তিকেরা নাস্তিকদেরও সেটার পাল্টা দিতে চায়ঃ “আমাদের অন্ধ মানছি, কিন্তু তোমরাও তো অন্ধ”। মনে পড়ে যায় এক লোকের কথা, শিক্ষাভবনে চাকরী করতো, খুব ঘুষ খেতো। ঘুষ কেন খান, এটা জিজ্ঞেস করায় তিনি নির্বিকারভাবে বলেছিলেন, আজকের দুনিয়ায় কে ঘুষ খায় না? যাহোক আস্তিকেরা এভাবে নিজেদের অন্ধত্ব স্বীকার করছে, এটাও কম অর্জন নয়। যাহোক, “বিজ্ঞান “নেই” প্রমাণ করতে পারে না বিধায় আল্লাহ, ফেরেশতা, বেহেশত, দোযখ এসবকে নেই বলাটা অবৈজ্ঞানিক” -এমন দাবী যেহেতু করা হয়, সেহেতু এখানে বিজ্ঞান ভাবনাটি কিরূপ সেটি আলোচনা করিঃ প্রথমত, বিজ্ঞান মনে করে একমাত্র প্রমাণ সাপেক্ষেই কোন কিছু আছে দাবী করা যেতে পারে। প্রমাণ যেহেতু নেই সুতরাং জোর গলায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব “আছ” এটা বলা অবৈজ্ঞানিক। দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞান অতিপ্রাকৃত বিষয়, অর্থাৎ যা প্রকৃতির বিভিন্ন নিয়মকে মানে না, তা অস্বীকার করে। অর্থাৎ, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর যদিও “আছে” বলেও কেউ ধরে নেয়, তবে সেই ঈশ্বরকেও প্রকৃতির সমস্ত নিয়ম মেনেই চলতে হবে। এ প্রসঙ্গে আইনস্টাইনের একটি চমৎকার আলোচনা আছেঃ “What I am really interested in, is knowing whether God could have created the world in a different way; in other words, whether the requirement of logical simplicity admits a margin of freedom.” এটি বুঝলেই আশা করি বিজ্ঞানের ঈশ্বর সম্পর্কে আগ্রহের জায়গাটি পরিষ্কার হবে। বিজ্ঞানের মূল কাজ হচ্ছে প্রকৃতির বিভিন্ন নিয়মকে উদঘাটিত করা। প্রকৃতির কোন একটি ঘটনা কোন একজন ঈশ্বরের কারণেও যদি হয়েও থাকে, তবে সেই ঈশ্বরেরও প্রকৃতির নিয়মকে অস্বীকার করার কোন ক্ষমতা নেই। আর এ কারণে একজন বিজ্ঞানী যখন কোন বিষয়ে গবেষণারত, প্রকৃতির নিয়ম উদঘাটনই তার মূল উদ্দেশ্য, ফলে তখন মাথা থেকে ঈশ্বরকে ছুড়েই ফেলতে হয়, কেননা প্রকৃতির নিয়ম ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন নয়- বরং ঈশ্বর যদি থেকেই থাকেন তবে তিনিই প্রকৃতির নিয়মাধীন। এভাবেই ঈশ্বরতত্ত্ব বিজ্ঞানের আওতামুক্ত সাবজেক্ট।
সূত্রঃ
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||
|
|
|
|
|