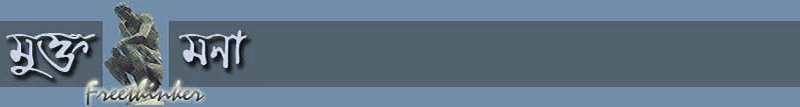
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||
|
|
|
কেন সমাজতন্ত্র? মূলঃ আলবার্ট আইনস্টাইন স্বাক্ষর শতাব্দ [এই লেখাটি প্রথম ১৯৪৯ সালে Monthly Review তে ছাপা হয়] অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে অদক্ষ কারো কি সমাজতন্ত্র বিষয়ে ধারণার প্রকাশ করা উচিত? অনেকগুলি কারণে আমি মনে করি করা উচিত। প্রথমত, প্রশ্নটিকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে দেখা যাক। এটা মনে হতেই পারে যে, জোতির্বিদ্যা এবং অর্থনীতির মধ্যে পদ্ধতিগত কোনো পার্থক্য নেইঃ উভয় বিষয়ের বিজ্ঞানীরা সাধারণভাবে নির্দিষ্ট কিছু ঘটনার ব্যাখ্যার্থে গ্রহণযোগ্য কতগুলি সুত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করেন, যাতে এই সব ঘটনাগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধের ব্যাপারগুলি বোঝা যায়। কিন্তু আসলে এদের মধ্যে পদ্ধতিগত অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। অর্থনীতির ক্ষেত্রে সাধারণ সুত্র আবিষ্কার অনেক কঠিন কারণ অর্থনৈতিক ঘটনাসমূহ প্রায়শই এত বেশি নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত হয় যে তাদেরকে আলাদাভাবে পরিমাপ করা যায় না। তাছাড়া মানব ইতিহাসের তথাকথিত সভ্যপর্যায়ের শুরু হতে আজ পর্যন্ত যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে, তা এমন কিছু নিয়ামকের দ্বারা নির্ধারিত ও প্রভাবিত যেগুলি কোনোভাবেই স্রেফ অর্থনৈতিক নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইতিহাসের বেশিরভাগ জাতি তার অস্তিত্বের জন্য যুদ্ধজয়ের উপর ঋণী। বিজয়ী জনগোষ্ঠী আইনগত এবং অর্থনৈতিকভাবে বিজিত দেশের সুবিধাভোগকারী অবস্থানে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। নিজেদের জন্য সৃষ্টি করেছে ভূ-সম্পত্তির উপর একচেটিয়া অধিকার এবং স্ব-শ্রেনী হতে যাজক সম্প্রদায়কে নিয়োগ করেছে। এই যাজক সম্প্রদায় শিক্ষাব্যস্থাকে কব্জা করার মাধ্যমে সামাজিক শ্রেনীভাগকে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের রূপ দিয়েছে, এবং এমন এক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করেছে, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অসচেতনভাবেই মানুষের সামাজিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। কিন্তু ঐতিহাসিক ভাবে আমরা বিগতকালের কথাই বলি, আমরা কোনোভাবেই মানব প্রবৃত্তির উন্নয়নের সেই স্তর থেকে বের হয়ে আসতে পারিনি যাকে থোর্স্টেইন ভেব্লেন “the predatory phase” বলে আখ্যায়িত করেছেন। যত ধরণের অর্থনৈতিক ঘটনাসমূহ প্রত্যক্ষ হয় সবই এই কালের এবং এর থেকে প্রাপ্ত সুত্রসমূহ কালান্তরে গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু সমাজতন্ত্রের আসল উদ্দেশ্য হলো মানব উন্নয়নের এই predatory phase কে সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়া, তাই বর্তমানের অর্থনৈতিক বিজ্ঞান ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক সমাজকে খুব বেশি স্পষ্ট করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সমাজতন্ত্র মূলত সামাজিক-নৈতিক একটি পরিণতির দিকে উদ্দিষ্ট। বিজ্ঞান কোনোভাবেই কোনো পরিণতির সৃষ্টি করে না, এমনকি ধীরে ধীরে সঞ্চারিতও করতে পারেনা, বড়জোড় পরিণতিতে পৌছানোর জন্য উপাদানের যোগান দিতে পারে। কিন্তু এই পরিণতিসমূহ কল্পিত হয় সুউচ্চ নৈতিক আদর্শের কিছু ব্যাক্তির দ্বারা। আর যদি এসব অপরিহার্য ও প্রচন্ড পরিণতিগুলি ইতোমধ্যে অর্জিত না হয়ে থাকে তবে,কিছু মানুষ এগুলোকে আত্মস্থ করে এবং সামনের দিকে নিয়ে যায়। এসব মানুষেরাই সমাজের সুস্থির বিবর্তনকে অর্ধসচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এসব কারণেই আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যতে মানবিক সমস্যার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহকে অতিশায়িত করা না হয়, এবং এটা মনে করা উচিত নয় যে শুধু মাত্র সুদক্ষ লোকেরাই সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিতকারী বিষয়াদি নিয়ে বক্তব্য দেয়ার আধিকার রাখে। অনেকদিন ধরেই অসংখ্য মানুষ এই দাবি করে আসছেন যে সমাজ একটা সংকটের মধ্যে দিয়ে পার হচ্ছে, সমাজের স্থিরতা বা ভারসাম্য প্রচন্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। এটা এমন এক সময়ের বৈশিষ্ট যেখানে প্রত্যেক মানুষ তার সম্প্রদায় বা সংগঠনের প্রতি উদাসীন এবং ক্ষেত্র বিশেষে বৈরী হয়ে উঠে। আমার কথাকে বোঝানোর জন্য আমার ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতার উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। সম্প্রতি আমি একজন বুদ্ধিমান ও বিদ্বান মানুষের সাথে আরেকটা যুদ্ধের সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলছিলাম। আমার মত ছিলো যে, আরেকটা যুদ্ধ মানুষের অস্তিত্বকে মহাসংকটে ফেলে দেবে এবং এই মন্তব্য করেছিলাম যে শুধুমাত্র কোনো আন্তর্জাতিক মহাসংস্থাই পারে এই মহাবিপদ থেকে সুরক্ষা দিতে। তখন ঐ ব্যাক্তি বলে উঠলেন, “মানবজাতির পরিণতি ধ্বংস, এটা থেকে আপনি এত বিপরীতে কেন?”। আমি নিশ্চিত যে মাত্র এক শতাব্দী বা তারও কম সময় আগে কেউ এ ধরণের কোনো মন্তব্যই করতে পারতো না। যারা নিজের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে ব্যর্থ এবং সফল হবার কোনো আশাই রাখেন না তারাই এ ধরণের মন্তব্য করেন। এর উৎস এমন এক ধরণের বিষাদপূর্ণ একাকীত্ব ও বিচ্ছিন্নতা, যাতে এ সময়ের বেশিরভাগ মানুষই ভুগছে। এর কারণ কি? এর থেকে মুক্তির কোনো উপায় কি আছে? এ ধরণের প্রশ্ন উত্থাপন করা সহজ হলেও কোনো প্রকার নিশ্চয়তার সাথে এর উত্তর দেয়া কঠিন। যদিও আমি এটা সম্বন্ধে অবগত যে আমাদের চিন্তা ও চেষ্টাগুলো প্রায়শই অসংগতিপূর্ণ এবং অস্পষ্ট, তাদেরকে সহজ ও সাধারণ সুত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় না, তবুও আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। মানুষ হলো একই সাথে বিচ্ছিন্ন ও সামাজিক। বিচ্ছিন্নভাবে সে নিজের ও তার আশেপাশের সবার অস্তিত্বকে রক্ষা করার চেষ্টা করে, নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছাগুলোকে পূরণ করার চেষ্টা করে, তার সহজাত সামর্থ্যের উন্নয়ন করে। আর সামাজিকভাবে সে তার আশেপাশের মানুষের স্বীকৃতি ও সম্প্রীতিলাভের চেষ্টা করে, তাদের সাথে আনন্দকে ভাগ করার চেষ্টা করে, তাদের দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করে, এবং তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের চেষ্টা করে। শুধুমাত্র এসব বিবিধ পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই মানুষের বিশেষ চরিত্র গড়ে উঠে। আর এসবের বিশেষ সন্নিবেশ নির্ধারিত করে একজন মানুষ তার অভ্যন্তরের ভারসাম্য কি মাত্রায় অর্জন করতে পারবে, সমাজের কল্যাণে কতটুকু অবদান রাখতে পারবে। এটা খুবই সম্ভব যে এই দুই পৃথক প্রচেষ্টার আপেক্ষিক শক্তি জন্মসূত্রে নির্ধারিত হতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে তা বহুলাংশে তৈরী হয় মানুষ যে পরিবেশে বেড়ে উঠে তার দ্বারা, সে যে সমাজে বেড়ে উঠে তার কাঠামোর দ্বারা, ঐতিহ্যের দ্বারা, এবং কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের মূল্যায়নের মাধ্যমে। “সমাজ”এর বিমূর্ত ধারণাটি একজন ব্যক্তির কাছে তার সমসাময়িক ও পূর্বতন সবকিছুর সাথে তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্কের সমষ্টি। ব্যক্তি নিজে নিজে চিন্তা-চেষ্টা-অনুভব করতে পারে ও কাজ করতে পারে, কিন্তু তার শারীরিক, বৌদ্ধিক ও আবেগিক অস্তিত্বের জন্য সমাজের উপর এত বেশি নির্ভর করে যে, সামাজিক কাঠামোর বাইরে তাকে চিন্তা করা বা বোঝা সম্ভব নয়। সমাজই তাকে সারা জীবন ধরে খাদ্য,বস্ত্র,বাসস্থান,যন্ত্রপাতি,ভাষা,চিন্তার পদ্ধতি ও চিন্তার বিষয়ের যোগান দেয়; তার জীবন ধারণ সম্ভব হয় অতীত ও বর্তমানের নিযুত-লক্ষের শ্রমের দ্বারা, যারা এই “সমাজ” নামের ছোট শব্দের পেছনে উহ্য। ফলে এটা নিশ্চিত যে, সমাজের উপর নির্ভরতা প্রকৃতিতে পিঁপড়া ও মৌমাছির জন্য যেমন সত্য ও অলঙ্ঘ্য, তেমনি মানুষের ক্ষেত্রেও। পিঁপড়া ও মৌমাছির ক্ষেত্রে তাদের সমগ্র জীবন প্রক্রিয়াকে সুক্ষ্ণতম ভাগ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করা যায় কিছু নির্দিষ্ট, জন্মসুত্রে প্রাপ্ত সহজাত প্রবৃত্তির মাধ্যমে, আর মানুষের ক্ষেত্রে সামাজিক বিন্যাস আর পারস্পরিক সম্পর্কগুলি নির্দিষ্ট নয় এবং পরিবর্তনশীল। নতুন নতুন কল্পনার সৃষ্টিকারী মানুষের মস্তিষ্ক, ভাষিক যোগাযোগের আশীর্বাদের ফলে এমন উন্নয়নের সম্ভব হয়েছে যা জৈবিক প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এই উন্নয়ন সুচিত হয় ঐতিহ্য, প্রতিষ্ঠান, সম্প্রদায়, ভাষা, বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশল অর্জনসমূহ এবং শিল্পকর্মসমূহের দ্বারা। এভাবে বোঝা যাচ্ছে মানুষ কিভাবে তার জীবনকে নিজের কর্মের দ্বারা প্রভাবিত করে এবং এই প্রক্রিয়ায় সচেতন চিন্তা-চাহিদার ভূমিকা রয়েছে। মানুষ জন্মের সময় উত্তরাধিকারসুত্রে যে শরীরতন্ত্র লাভ করে, আমরা একে অবশ্যই অপরিবর্তনীয় ধরে নেবো, এমনকি বিভিন্ন জৈবিক তাড়নাসমূহ যা মনুষ্য প্রজাতির বৈশিষ্ট্য। সেই সাথে তার জীবদ্দশায় সে লাভ করে মননতন্ত্র, যা সে আয়ত্ত করে সমাজের সাথে তার যোগাযোগ ও অন্য ধরণের প্রভাবের মাধ্যমে। এই মননই সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় এবং অনেকাংশে সমাজের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ককে নির্ধারণ করে। আদিম রীতি-পদ্ধতিসমূহের তুলনামূলক অনুসন্ধানের মাধ্যমে আধুনিক নৃবিদ্যা আমাদের জানিয়েছে যে, মানুষের সামাজিক আচরণ বিভিন্ন রকম হতে পারে, এবং এটা নির্ভর করে সমাজে আধিপত্যকারী সংগঠনের উপর এবং বিরাজমান সাংস্কৃতিক মননের উপর। এর ফলে যারা মানবজাতির বৃহৎ অংশের উন্নতির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন তাদেরকে আমি আশাবাদী হতে বলবো কারণ, মানব অস্তিত্ত্বকে বাতিল ঘোষণা করা যায় না, নিজের শারীরিক অস্তিত্বেরর জন্য হলেও নিজেরা একে অপরকে হত্যা করবে না অথবা নিজেকে ধ্বন্স করার মত নির্মম পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে না। যদি আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি যে, জীবনকে আরামদায়ক করার জন্য এই সামজিক কাঠামো এবং মানুষের সাংস্কৃতিক আচরণ কিভাবে পরিবর্তিত হবে, আমাদের সবসময় কিছু বিষয় সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে কারণ কিছু কিছু নিয়ামক আমরা কখনোই বদলাতে পারি না। আগেই বলা হয়েছে যে জৈবিক গঠনতন্ত্রের কোন কিছুই কোন ব্যবহারিক কারনেই পরিবর্তন করা যায় না। উপরন্তু বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে সংগঠিত প্রযুক্তি ও জনসংখ্যায় যে পরিবর্তনের ফলেও যে অবস্থার তৈরী হয়েছে তা টিকে থাকবে। তুলনামুলকভাবে ঘনবসতিপূর্ণ স্থানে কোন জনগোষ্ঠীকে যদি অপরিহার্য দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয় তাহলে এক ধরণের উৎপাদন যন্ত্র কেন্দ্রিক শ্রমবিভাগ আবশ্যক। সে অলস সময়ের অবসান ঘটেছে যখন ছোট গোষ্ঠীগুলোও নিজেরা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলো। এটা খুব বেশি বাড়িয়ে বলা হবে না যে, মানবজাতির আজ তৈরী হয়েছে সমগ্র গ্রহজুড়ে উৎপাদক শ্রেণী ও ভোক্তাশ্রেণী। এ পর্যায়ে আমি এখন সংক্ষেপে বলতে পারি এই সংকটের মূল ব্যাপারটা আমার কাছে কি মনে হয়? এ সংকট ব্যক্তির সাথে সমাজের সম্পর্কের সাথে জড়িত। ব্যক্তি অন্য যেকোন সময়ের তুলনায় সমাজের উপর তার নির্ভরশীলতার ব্যাপারে অনেক বেশি সচেতন। কিন্তু সে এই নির্ভরশীলতাকে অস্তিবাচক সম্পদ হিসেবে দেখে না, জৈবিক বন্ধন ভাবে না, রক্ষাকারী শক্তি মনে হয় না বরং তার স্বাভাবিক অধিকার ও অর্থনৈতিক অস্তিত্বের প্রতি হুমকি মনে করে। সমাজে তার এমন অবস্থান তৈরী হয় যে, তার ইগোকেন্দ্রিক আকাঙ্ক্ষাগুলি সবসময় তুঙ্গে থাকে, আর তার সামাজিক তাড়নাগুলি স্বাভাবিকভাবেই থাকে দুর্বল আর আস্তে আস্তে কমতে থাকে। মানুষ সমাজের যে স্তরেই থকুক না কেন দিনে দিনে এই ক্রমহ্রাসমান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। নিজের ইগোর জালে অনিচ্ছাকৃতভাবে বন্দী হয়ে মানুষ নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করে, একাকীত্ব লাভ করে আর জীবনের সহজ, স্বাভাবিক ও সাবলীল আনন্দলভ থেকে বঞ্চিত হয়। মানুষ শুধুমাত্র সমাজের প্রতি আত্মনিবেদনের মাধ্যমেই ক্ষুদ্র ও ঝঞ্ঝাপূর্ণ জীবনের মানে খুঁজে বের করতে পারে। আমার মতে সকল প্রকার অশুভের উৎস হলো আজকের পুঁজিবাদী সমাজে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য। আমরা আমাদের সামনে দেখতে পাই এক বিশাল উৎপাদক শ্রেণী যারা তাদের যৌথ শ্রমের ফল থেকে পরস্পরকে বঞ্চিত করতে অবিরাম চেষ্টা করছে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নয়, বরংচ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠিত আইনের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, উৎপাদনের উপায় তথা ভোক্তাপণ্য উৎপাদনের জন্য যে সামগ্রিক উৎপাদকযন্ত্র ও মূলধনজাতীয় দ্রব্যের প্রয়োজন তা আইনীভাবে আধিকাংশেই মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি।
আলোচনার সুবধার্থে এখন থেকে আমি যাদের উৎপাদনের উপায়ের উপর মালিকানা নেই তাদেরকে “শ্রমিকশ্রেণী” বলে আখ্যায়িত করব, যদিও এই শব্দটির যথার্থ প্রায়োগিক জায়গা নয়। উৎপাদনের উপায়ের উপর যার মালিকানা থাকে সে শ্রমিকের শ্রমকে কিনে নেয়ার মত অবস্থানে থাকে। উৎপাদনযন্ত্রে শ্রমিক নতুন দ্রব্য তৈরী করে যা পুঁজিবাদীর সম্পত্তিতে পরিণত হয়। এখানে ধর্তব্য হলো শ্রমিকের উৎপন্ন দ্রব্য ও তার মজুরির মধ্যে প্রকৃত মূল্যে নির্ণায়িত সম্পর্কের ব্যাপারটি। যেহেতু শ্রমচুক্তির ব্যাপারটি “বিনামূল্যে” নির্ধারিত হয়, তাই শ্রমিক যা গ্রহণ করে তা প্রকৃতমূল্যে নির্ণায়িত নয়, বরং তার ন্যূনতম প্রয়োজন এবং পুঁজিপতির প্রয়োজন এবং শ্রমের যোগানের উপর নির্ভর করে। আমাদের অবশ্যই এটা বোঝা দরকার যে, শ্রমিকের মজুরি তার উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য অনুযায়ী নির্ধারিত নয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি অল্প কিছু ব্যক্তির কুক্ষিগত হতে থাকে। এর কারণ অংশত পুঁজির প্রতিযোগীতা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন। ক্রমবর্ধিষ্ণু শ্রমবিভাগের ফলে ছোট ছোট উৎপাদন ইউনিটের জায়গায় বড় বড় ইউনিট গড়ে উঠে। এর ফলে তৈরী হয় এমন এক ব্যবস্থা যেখানে মূলধন জড়ো হতে থাকে সীমিত কিছু ব্যক্তির কাছে, এবং এই শক্তিকে গনতান্ত্রিক রাজনৈতিক সমাজের দ্বারা আর নিয়ন্ত্রন করা যায় না। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট কারণ নিজেদের প্রয়োজনেই পুঁজিপতিরা নির্বাহী বিভাগকে নির্বাচনের দ্বারা আলাদা রেখে, রাজনৈতিকদলগুলিকে আর্থিক ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে, প্রভাবিত করে এবং এদের মধ্যে থেকেই আবার বিভিন্ন নির্বাহী প্রতিনিধি নিয়োগ করে। এর পরিণতি হলো সমাজের এই সব প্রতিনিধিরা সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর স্বার্থ যথেষ্ট পরিমাণে রক্ষা করতে পারেনা। আর এ অবস্থায় এই সব পুঁজিপতিরাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সকল প্রকার প্রধান সংবাদ মাধ্যমকে/ তথ্য উৎসকে নিয়িন্ত্রণ করে(প্রেস, রেডিও, শিক্ষা )। এর ফলে একজন ব্যক্তির পক্ষে নৈর্ব্যক্তিক উপসংহারে উপনীত হওয়া বা তার রাজনৈতিক অধিকারসমূহের সঠিক ব্যবহার দুষ্কর এবং কিছু ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়ে। মূলধনের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণাকেন্দ্রিক এই অর্থণীতির বিরাজমান অবস্থাকে দুটি মূল নীতির দ্বারা সুচিত করা যায়ঃ প্রথমত উৎপাদনের উপায়(মূলধন) ব্যক্তিগত মালিকানায়, মালিকেরা নিজের ইচ্ছামতো এর বিনিময় করে এবং দ্বিতীয়ত বিনামূল্যের শ্রমচুক্তি। অবশ্য এর ফলে প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ পুঁজিবাদী সমাজ বলতে কোন কিছু নেই। এটা বোঝা উচিত যে, শ্রমিকশ্রেণীকে তিক্ত রাজনৈতিক সঙ্ঘাতের মধ্য দিয়ে কিছু শ্রেণীর শ্রমিকের জন্য “বিনামূল্যের শ্রমচুক্তির” চেয়ে ভালো কোনো অবস্থায় পৌছে গেছে। তবে মোটের উপর এই অবস্থা “বিশুদ্ধ” পুঁজিবাদ থেকে খুব বেশি পৃথক নয়। উৎপাদন করা হয় মুনাফার জন্য, চাহিদা অনুযায়ী নয়। এমন কোনো ব্যবস্থা নেই যে সমর্থ ও ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য সবসময় কর্মসংস্থানের সযোগ রয়েছে, একটা বিশাল “বেকার জনতা” সবসময়ই পাওয়া যায়। একজন শ্রমিক সবসময় তার কাজ হারানোর ভয়ে থাকে। যেহেতু বেকার এবং নিম্ন আয়ের শ্রমিকেরা মুনাফাজনক বাজারের তৈরী করে না, তাই ভোক্তা দ্রব্যের উৎপাদন সীমিত আকারে ঘটে যার ফলাফল বিপুল দুর্ভোগ। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন প্রায়শই সকলের শ্রমের বোঝা কমানোর চেয়ে বেশি করে বেকারত্বের সৃষ্টি করে। মূলধনের বন্টন ও সুষ্ঠ ব্যবহার না হবার ফলে যে ক্রমবর্ধমান হতাশার উদ্রেক হচ্ছে তার জন্য দায়ী হলো মুনাফাকেন্দ্রিক চিন্তা আর সেই সাথে পুঁজিপতিদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগীতা। এই অসীম প্রতিযোগীতার ফলে ঘটে শ্রমের বিরাট অপচয় ও সামাজিক সচেতনতার প্রতি ব্যক্তির অনীহা যা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। ব্যক্তিমানুষের এই অনীহাকে আমি পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা মনে করি। সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা এই সমস্যা ভোগ করে। এক ধরণের অতিশায়িত প্রতযোগীতামূলক ভীতি একজন ছাত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়, তাকে ভবিষ্যত জীবনের জন্য অর্জিত সাফল্যের সাধনার শিক্ষা দেয়া হয়। আমি মনে করি এই সব ভয়াবহ সমস্যার দূর করা সম্ভব সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা ও একই সাথে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ যার উদ্দিষ্ট হবে সামাজিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের দিকে। এধরণের ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায়সমুহের মালিকানা থাকবে সমাজের হাতে এবং উপযোগের ব্যবহার ঘটবে সূষ্ঠু। একটি পরিকল্পিত অর্থনীতি যা উৎপাদনের সাথে সমাজের চাহিদার সমন্বয় সাধন করে, সকল কর্মক্ষম মানুষের মধ্যে সঠিকভাবে কাজের বন্টন করবে এবং প্রত্যেক নর, নারী ও শিশুর জীবন নির্বাহ নিশ্চিত করবে। প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষা তার সহজাত প্রবৃত্তির উন্নয়নের পাশাপাশি সমাজে ক্ষমতা ও সাফল্যের জায়গায় এক ধরণের দায়িত্ববোধ তৈরী করবে। এটা খেয়াল রাখতে হবে যে পরিকল্পিত অর্থনীতির মানেই সমাজতন্ত্র নয়। পরিকল্পিত অর্থনীতি ব্যক্তির দাসত্বের মধ্য দিয়েও অর্জিত হতে পারে। সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য কয়েকটি দুরহ সমাজ-রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে হবেঃ কিভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রিয়করণ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, আমলাতন্ত্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া ও অনিয়ন্ত্রিত অবস্থা ঠেকানো যাবে? ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষা করে বিপরীতে কিভাবে গনতান্ত্রিক আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা নিশ্চিত করা যায়? সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য ও সমস্যা সম্বন্ধে স্পষ্টতা আমাদের এই পরিবর্তনের যুগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যেহেতু বর্তমানে এই সমস্যাগুলি নিয়ে মুক্ত ও অবাধ আলোচনার খুব বেশি সুযোগ নেই আমি মনে করি জনকল্যাণে এই পত্রিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
ছাত্র, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||
|
|
|
|
|