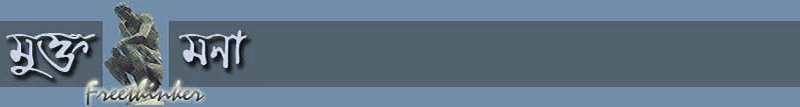
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||
|
|
|
ধর্ম চেতনা ও ঈশ্বর-বিশ্বাস ওয়াহিদ রেজা ১ আদিম বা আদম মানব মানব গোষ্ঠীর প্রারম্ভিক যুগে পৃথিবীতে না ছিল কোনো ঈশ্বর, না ছিলো কোনো ধর্মের অস্তিত্ব। মানুষের মন থেকেই ধর্মের জন্ম, ঈশ্বর নামক অদৃশ্য অলীক ব্যক্তিটির গর্ভপাত। তারপরও মানুষ তার অ-মানুষ স্তর থেকে মানুষের অবস্থায় বিবর্তিত হওয়ার কালে কেন বা কি করে ধার্মিক হয়ে উঠলো এবং আজ পর্যন্তই বা কেন ধর্মবিশ্বাসকে আগলে রেখেছে, কোন নিয়মে বা কোন প্রয়োজনে মানুষ তার আদিম জীবনের স্থুল ধর্মীয় ধারণাকে পরবর্তী যুগে উচ্চতর মার্জিত রূপ দান করেছে এ প্রশ্নের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত উত্তরটিতে যে কথাগুলো উঠে আসে, তা হলো সম্প্রদায়ের আধিপত্য বিস্তার ও ধর্মীয় চেতনার ধোঁয়ার অস্পষ্টতায় ক্ষমতার লিপ্সা । অর্থাৎ প্রভুত্ব। ধর্মীয় মৌলবাদের রাজত্ব। অরাজকতা। মানবতার অবমূল্যায়ন। মানুষের স্বাধিকার হরণের একচ্ছত্র শোষণ। আজ ঐতিহাসিকভাবে এ কথা প্রমাণিত সত্য যে, প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত কোনো ধর্মই রক্তপাতহীন প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। সব ধর্মেরই প্রাতিষ্ঠানিকতার পবিত্র হাতে লেগে রয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তের দাগ। ধর্ম তার এই তথাকথিত অগ্রগতির সঙ্গে নিজের যথার্থতা নিরূপণের জন্য অতীয়ন্দ্রিয় সত্তার সমর্থন ব্যতীত ধর্ম স্বপ্নের অর্থহীন শিল্পকলায় বা একটি সুন্দর মায়ায় পর্যবসিত হয়। বিস্তৃত বিশ্বজগতের অন্তর্নিহিত সত্তার সঙ্গে রয়েছে ধর্মবোধের চিরবৈরিতা। আজ বিজ্ঞান ও বস্তুবাদী দর্শনের ক্রমউৎকর্ষকালে মানুষের মৌলিক মেধা, মনন ও জ্ঞান চর্চা যখন প্রতি পদে পদে সকল রকম কুসংস্কার ও অন্ধত্বের কালো পর্দা ছিঁড়ে ছিঁড়ে বিশ্বমানবতার সার্বজনীন ঊষার আলোমুখি ধাবমান তখন ধর্মের অন্তঃসার শূণ্যতা ও ধর্মবোধের অযথার্থতা যে আগামী একদিন প্রমাণিত হবেই এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। তখন ধ্বংস হয়ে যাবে ধর্মের ভীতিকর অলীক ঈশ্বরতত্ত্ব। ধুলায় মিলিয়ে যাবে ধর্মীয় লোভ ও বিভীষিকার তথাকথিত স্বর্গ-নরকের পরলৌকিক বাগাড়ম্বর। মানুষের জ্ঞান বিকাশের প্রাথমিক স্থরটি ছিল ভয়, সংশয়, দ্বিধা, দ্বন্দ্বের অধ্যায়। প্রাকৃতিক বিবর্তন, আলোড়ন, দুর্যোগ ইত্যাদি এ সবের মূল কারণ। তৎকালীন সময় অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগে এ সমস্ত প্রাকৃতিক কার্যবিধির যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা-হীনতারই একমাত্র কারণ, অবলম্বন বা ধারণাই মানব মস্তিষ্ককে বাধ্য করেছে অতীন্দ্রিয় বা অলৌকিক নামক ভুয়া সংশয়ের কাছে আত্মসমর্পণে। যার ধারাবাহিক অনিবার্য ফলশ্রতি হলো ধর্মচেতনা। আর এই ধর্মচেতনাই হয়ে দাঁড়িয়েছে পরবর্তী উন্নত মানুষের মৌলিক উন্নতির প্রধান অন্তরায়। পুরাকালে এই মতের সমর্থক ছিলেন এপিকিউরীয় দার্শনিকগণ এবং ল্যাটিন কবি ল্যুক্রেটিয়াস। তাঁরা ধর্মবিশ্বাসকে কুসংস্কারের যমজভাই বিবেচনা করতেন। পেট্রোনিয়াসের বিখ্যাত একটি পংক্তিতে এই মতের সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যায়। Primus in orbe deos facit timor (প্রাথমিকভাবে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য ভয় থেকে এসেছে)। আধুনিককালে হিউম ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের উৎস হিসেবে ভয়ের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অবশ্য সেই সঙ্গে তিনি আরো একটি কথা যোগ করে দিয়েছেন- ঈশ্বরের প্রতি ভয়, তাঁর সদিচ্ছা লাভের রূপ পরিগ্রহ করে। আধুনিককালে অনেক বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী, যেমন রিবট এই ‘ভীতির মতবাদ’কে সমর্থন করেন। আদিম অবস্থায় ধর্মে ভয়ের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একটি রহস্যময় শক্তিতে বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মচেতনা। ধর্মীয় মনোভাব হলো অধিকতর শক্তিশালী কোনো অদৃশ্য ব্যক্তির নিকট আত্মসমর্পণ। একেশ্বরবাদী ধর্ম বিশ্বব্রক্ষ্মান্ডের অনন্ত শক্তিকে একজন ব্যক্তি হিশেবে চিন্তা করে। আর সেই অদৃশ্য ব্যক্তিটিই হলেন ঈশ্বর বা আল্লাহ। এটি অবশ্য উন্নত ধর্মচেতনার আধুনিক পরিণতি। প্রাথমিক স্থরে আদি টোটেম ছিলো তার প্রতীক। রবার্টসন স্মিথ এই মত দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করেন। তাঁর বহু পরিচিত একটি অনুচ্ছেদ এখানে উদ্ধৃত হলো, ‘আদিম মানুষেরা অসংখ্য বিপদের দ্বারা নিজেদের পরিবেষ্টিত বলে মনে করতো, সঠিকভাবে তারা বিপদটা কি জানতো না; কিন্তু অদৃশ্য কোনো ব্যক্তির রহস্যময় শক্তিই যে বিপদের (প্রাকৃতিক দুর্যোগ) কারণ এমন একটা উপলব্ধি বা ধারণা তাদের মধ্যে জন্ম লাভ করে। এবং এই উপলব্ধি থেকে তারা বুঝতে শেখে যে সেই অদৃশ্য ব্যক্তি মানুষের চেয়েও অধিকতর শক্তিশালী ’ (W. R. Smith, The Religion of Semites, P. 55)। মূলত এই প্রাচীন উপলব্ধি বা ধারণা থেকেই ঈশ্বর ও ধর্মচেতনার আদি অঙ্কুরের বিকাশ। ধর্মবোধের আদি অবস্থা থেকে আধুনিক ধর্মচেতনা ভয়-ভীতি প্রদর্শনের ভূমিকা যে লুপ্ত হয়ে যায়নি তার পরিষ্কার দৃষ্টান্ত হলো বাইবেল ও কোরান। ওল্ড টেষ্টামেন্টের জনপ্রিয় নীতি হচ্ছে, ‘প্রভুর প্রতি ভয়ই হলো জ্ঞানলাভের সূচনা’ (eg Ps. exi.10. Prov. ix. 10) এবং নিউটেষ্টামেন্টে মানুষকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এই বলে, ‘ঈশ্বরকে স্বীকার করে নিয়ে উপাসনা করো কিন্তু ঈশ্বর হিসেবে তাঁকে ভয় ও শ্রদ্ধা করো’ (Heb. xxii-28, Moffe- এর অনুবাদ)। ভয় + শ্রদ্ধা? না মনোবিজ্ঞান আজ এ কথাটি প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ভয় থেকে কখনো প্রকৃত শ্রদ্ধাবোধ জন্মাতে পারে না। তবে বাইবেলের চেয়ে কোরান ভয় প্রদর্শনে অত্যধিক তীক্ষ্ন ও শাণিত। কোরানের আল্লাহ চক্ষু রাঙিয়ে পাতায় পাতায় ভয়-ভীতির তর্জনী উঁচিয়ে রেখেছেন মানুষের প্রতি! তিনি একদিকে নিজেকে পরম দয়ালু ও অন্যদিকে চরম নিষ্ঠুর দাবি করেন। কিন্তু প্রকৃত দয়ালু যে কখনো নিষ্ঠুর হতে পারেন না এর বিশদ ব্যাখ্যার কী কোনো প্রয়োজন আছে? ধর্মচেতনার সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্কের চেয়ে অন্ধ আবেগ, অনুভূতির সম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠতর এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর এর পেছনের মূল ভিত্তিটি হলো- বিশ্বাস। আর বিশ্বাস হচ্ছে প্রশ্নহীন, যুক্তিহীন, বুদ্ধিবিবেচনাহীন একটি বিষয়। জগৎ যেভাবে দৃশ্যমান ঠিক সেই ভাবে ধর্মীয় চেতনা জগতকে গ্রহণ করে না। ধর্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরে একটি অফুরন্ত, অপার্থিব শক্তির অস্তিত্ব অনুমান করে। অতীন্দ্রিয় জগতের প্রতি ধর্মের যতোটা আস্থা রয়েছে পরিদৃশ্যমান জগতের প্রতি ততোটা নেই (এটা প্রমাণ করতে বেশি দূর দৌড়ুনোর প্রয়োজন নেই, আজকের ধর্মীয় মৌলবাদী রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর কথাবার্তা, কার্যকলাপ লক্ষ করলেই এর সত্যতা পাওয়া যাবে)। ধর্ম বিশ্বাস করতে শেখায় সেই অতীন্দ্রিয় অপার্থিব জগৎ যা মানুষের সকল প্রত্যাশা পূরণ করতে সমর্থ। এটা সম্পূর্ণই একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস। আর এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে অবলম্বন করেই জগতে বিচরণ করছে অধিকাংশ মানুষ। এবং এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে পুঁজি করেই ধর্মীয় ব্যাখ্যাকারগণ যুগ যুগ ধরে মানুষকে ধর্মচেতনার আজগুবি অতীন্দ্রিয় জগতের লোভ প্রদর্শন করে বিপথগামী করেছে, অর্থাৎ মানুষের মৌলিক বিকাশ ও মানবতার স্বতঃস্ফুর্ত বহিঃপ্রকাশকে রুদ্ধ করে রেখেছে, কল্পনাপ্রবণ এই সব চিন্তাবিদদের অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ আরোহমূলক ধর্মীয় ব্যাখ্যাকে অকারণ বাগাড়ম্বরপূর্ণ ভন্ডামি বলা যেতে পারে। প্লেটোর সম্পর্কে জুবার্ট যেমন অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তার অনুকরণে ম্যাথু আর্নল্ড শেলির সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছিলেন এই বলে যে, ‘এক সুন্দর কিন্তু নিষ্ফল দেবদূত। সে তার দ্যুতিময় পাখা মহাশূন্যে বৃথাই আন্দোলন করেছিলো’। বাক্যটি একটু ওলট পালট করে আমরা কল্পনাপ্রবণ ধর্মীয় ভাববাদী ও পান্ডাদের সম্পর্কেও প্রয়োগ করতে পারি। তারাও তাদের পাখা (ধর্ম প্রতিষ্ঠা পাবার আগেই) মেলে দিয়েছিলেন কল্পনারাজ্যের মহাশূন্যে। সেখানে কোনো বায়ুমন্ডল নেই। যদিও থাকে তা এতোই লঘু যে কেউ তাতে পাখা উড়ে যেতে পারে না। এই কল্পনার সঙ্গে ঐতিহাসিক রূঢ় বাস্তবতার কোনো মিল নেই। কোঁতে তাঁর ‘Religion of Humanity’ গ্রন্থে বলেছেন, ‘ধর্ম হলো মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত একটি কৃত্রিম সৃষ্টি’। কিন্তু এই কৃত্রিমতা যে ক্রমান্নয়ে মানুষের মেধায় ও মননে বায়বীয় এক অকৃত্রিমতার রূপ লাভ করেছে এ কথা অস্বীকার করা যাবে না। ধর্ম তাই এক ধরনের অতীন্দ্রিয় বিশেষ অভিজ্ঞতা প্রতিটি ধার্মিকের কাছে। আর ধার্মিক মাত্রই বিশ্বাসী। আর বিশ্বাস মাত্রই প্রশ্ন-যুক্তি-আকাংক্ষাহীন বিষয়। বিজ্ঞান বুদ্ধিভিত্তিক। বিজ্ঞান প্রশ্ন-যুক্তি-কৌতহল-আকাংক্ষার সমন্নয়। কিন্তু ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় বুদ্ধির ভূমিকা গৌণ। প্রশ্ন-যুক্তি নিষিদ্ধ। ধর্মের সঙ্গে বুদ্ধি অপেক্ষা কাল্পনিক অনুভূতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। ধর্ম অপার্থিব শক্তিতে বিশ্বাসী। সে অপার্থিব শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করে। এবং বুদ্ধিনিরপেক্ষ অনুভূতির সাহায্যে ধর্ম পরম সত্তাকে উপলব্ধি করতে চায়। এর কোনোটিই বিজ্ঞানের কাজ নয়। এর কোনোটিই বিজ্ঞান সমর্থন করে না। তাই ধর্মকে এখন অবশ্যই বিজ্ঞান ও বস্তুবাদী দর্শনের আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত। ‘মানুষের ইতিহাস হলো প্রকৃতপক্ষে ধর্মের ইতিহাস’-মানব সভ্যতার মূলের দিক থেকে বিচার করলে ম্যাক্সমূলারের এই উক্তিতে খুব একটা অতিশয়োক্তি নেই। কারণ এমন কোনো আদিম মানব গোষ্ঠী বা সমাজ ছিলো না যেখানে অজ্ঞতা থেকে ধর্মের ধারণা প্রথম সৃষ্টি লাভ করে নি। অবশ্য আজকের সুসংগঠিত, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমতের সঙ্গে আদিম ধর্মমতের পার্থক্য ছিলো অনেক। ধর্মের প্রথম উৎপত্তিও ক্রমবিকাশের প্রশ্নটি ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। আর তারপরই ধর্মের স্বরূপ ও কার্যাবলী পর্যবেক্ষন করা সম্ভব। কিন্তু এ ধরনের একটি সীমিত রচনায় তার বিশদ আলোচনা অসম্ভব। এখানে কেবল মানুষের প্রাচীন ধর্মবোধ থেকে বর্তমান ধর্মবোধের উন্নত অবস্থা লাভের একটি সংক্ষিপ্তসার টানা যেতে পারে যা কোনোভাবেই পূর্ণাঙ্গ নয় – ‘ধর্ম একটি অত্যন্ত জটিল বিষয়। একে কোনো একটি মাত্র সামাজিক রীতির বৃদ্ধি বা বিস্তৃতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। যতোই আদিম রূপের হোক না কেন কোনো উপাসনা কোনো একটি মাত্র চিন্তার বা একটি মাত্র আবেগের প্রকাশ বলা যায় না। বরং ধর্ম হলো (মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্তনশীল ধারার বহু বহু পূর্বের) অনেকগুলো জটিল ও শক্তিশালী চিন্তার সৃষ্টি’ (M. Jastrow, The Study of Religion, P. 185)। মানুষের মনেই ধর্মের জন্ম। জ্ঞানের ঊষালগ্নে মানুষের জীবনের উপর ব্যাখ্যাহীন প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। এই শক্তির অস্তিত্ব অনুমানের ফলে মানুষের মনে যে আবেগ জন্মেছিলো তার থেকেই ধর্মচেতনার উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন যুগের মতো আজকের স্বঘোষিত উন্নত ধর্মগুলোও ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে মানুষের বিশ্বাসের প্রশ্রয়ে অলীক জগতের হাতছানি দেয়; ঈশ্বর, দেব দেবী, জীন, ফেরেশতা, স্বর্গ, নরকের গপ্পো শোনায়, আত্মা অমরত্বের লোভ দেখিয়ে উর্বর মানব মস্তিষ্কের বিকলাঙ্গতা ঘটায়। সালোমন রেইনখ ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, ‘আমি এইভাবে ধর্মের সংজ্ঞা দিতে চাই- আমাদের কর্মদক্ষতার স্বাধীন প্রকাশকে বাধাদান করে যে সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তার সমষ্টিকেই ধর্ম বলে’ (Salomon Reinach Orepheus [ E. Tr. 109] p.3)। এ কথা অনস্বীকার্য যে অযৌক্তিক বিধি-নিষেধ প্রগতির পরিপন্থী। খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলাম ধর্ম উভয়ই প্রগতীর পরিপন্থী। তারপরও এদুটি ধর্মের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ আজ এতোটা স্ফীত কেন? এর জবাব খুঁজতে যাবার আগে ধর্মের ইতিহাস একটা নিরবিচ্ছিন্ন প্রগতির ইতিহাস এরকম অনুমান করা থেকে বিরত থাকতে হবে, পরিবর্তে শোষণ, প্রভুত্ব, ক্ষমতালোলুপতার ধারাবাহিক ইতিহাসের কথাটি মাথায় রাখতে হবে। কারণ অনেক পুনরাবৃত্তি, অবক্ষয়, অসভ্যতা ও কুসংস্কারের জটিল আবর্তনের কাহিনী রয়েছে ধর্মের ইতিহাসে। যুগে যুগে প্রগতি যখন এক জায়গায় বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে অন্যত্র তখন সে পরিবর্তনের পথে বিকশিত হয়ে নতুন পথ আবিস্কার করে নিয়েছে। ঐতিহাসিক ভাবে চিহি¡ত ধর্মের আদিম যুগের ফেটিশবাদ কোনোভাবেই প্রগতি নয়। এটা প্রত্যাবর্তন বা পশ্চাৎগতির নিদর্শন। Fetish কথাটি এসেছে পর্তুগীজ Feitico শব্দ থেকে। Feitico শব্দের অর্থ হলো মুগ্ধ হওয়া বা বিস্মিত হওয়া। আবার Feitico শব্দ এসেছে ল্যাটিন Factitius শব্দ থেকে। Factitius শব্দের অর্থ হচ্ছে কৃত্রিম। অবশ্য মধ্যযুগে ল্যাটিন এই শব্দটির অর্থ ছিলো - ঐন্দ্রজালিক। পশ্চিম আফ্রিকার আদিবাসীদের উপাস্য-বস্তুকে উল্লেখ করার জন্য পঞ্চদশ শতকের পর্তুগীজ নাবিকেরা এই শব্দটি ব্যবহার করতো। ফেটিশ একটি জড় পদার্থ। আত্মা বা রহস্যময় শক্তির এটি আবাসস্থল। অন্তত কিছু সময়ের জন্য এই বস্তুটির উপর আত্মা ভর করে বলে বিশ্বাস করা হতো। সেই জন্য জড় বস্তুটিকে উপাসনা করা হতো এবং সৌভাগ্য লাভের চেষ্টা হতো। প্রাকৃতিক বস্তু হিশেবে ফেটিশের নিজস্ব কোনো মূল্য ছিলো না। যে আত্মা তাতে বসবাস করে বা এসে অবস্থান করে সেই আত্মার গুণে মূল্যায়ন হতো ফেটিশের। হয়তো কোনো অদ্ভুত-দর্শন প্রাকৃতিক জিনিস, যেমন অস্বাভাবিক একটা পাথর কিংবা লাঠি, অথবা হাড় বা নখ প্রথম মানুষের মনযোগ আকর্ষণ করতো। তারা ভাবতো হয়তো এখানে অপার্থিব কোনো শক্তি থাকতে পারে। এই ভাবনা থেকে তারা উপাসনা করতে শুরু করে। ফেটিশের কাছে উৎসর্গ ও প্রার্থনা করা হতো। কিন্তু যদি দেখা যেতো তাতে কোনো লাভ হচ্ছে না তখন বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আকাংখিত বস্তুটি চাওয়া হতো। তাতেও না পাওয়া গেলে আদেশ করা হতো। কিন্তু তারপরও যদি আকাংখিত বস্তুটি পাওয়া না যেতো তখন শুরু হতো গালাগালি। এমন কি চাবুকও মারা হতো ফেটিশকে। কিন্তু যদি তাও ব্যর্থ হতো তখন ধরে নেয়া হতো জিনিসটিকে ছেড়ে আত্মা চলে গেছে। প্রয়োগবাদের আদিমতম রূপটি সম্ভবত এখানে প্রকাশ পেয়েছে। একটি ফেটিশ থেকে যতক্ষন কাজ পাওয়া যায় ততক্ষন সে পবিত্র। নইলে দাও আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে। অবশ্য এর ফলে ফেটিশকদের সমাপ্তি ঘটছে না। একটা ফেটিশ গেলে নতুন আরেকটা বস্তুকে ফেটিশ হিশেবে গ্রহণ করা হতো। স্পষ্টতঃ ফেটিশবাদ অত্যন্ত অনুন্নত মানের ধর্ম। ফেটিশ একটি ব্যক্তিগত দেবতা। অসভ্যরা নিজেদের নির্দেশে তাকে কাজ করতে বাধ্য করতো। এই ধারণা ব্যক্তিগত এবং খামখেয়ালী চিন্তার এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এবার আরো একটি ধর্মীয় মানের অধোগতির বিষয় বলা যেতে পারে। ফেটিশবাদের মতো বহু আত্মা উপাসনাবাদও (Polydoemonism) ধর্মীয় মানের আধোগতির নিদর্শন। সমগ্র চরাচর অসংখ্য আত্মায় পরিব্যাপ্ত। মানুষ প্রতি মুহুর্তে নিজেদের সুবিধা বা অসুবিধার জন্য তাদের উপস্থিতি বুঝতে পারে। স্বপ্ন থেকে যে এই ধারণার উৎপত্তি হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আদিম মানুষের কাছে স্বপ্নের অভিজ্ঞতা জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতার মতোই বাস্তব ছিলো। তারা আত্মাকে নিজেদের অজ্ঞাত ও অস্পষ্ট প্রতিরূপ বলে ভাবতো। ঘুমের সময় আত্মা দেহ ছেড়ে ঘুরে বেড়ায় আবার জেগে উঠার আগে দেহে ফিরে আসে- এই ভাবে তারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতো। স্বপ্ন এবং মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য হলো স্বপ্নে আত্মা ফিরে আসে কিন্তু মৃত্যু হলে আত্মা আর দেহে ফিরে আসে না অথবা বলা যেতে পারে আত্মা দেহে না ফিরে এলে মৃত্যু হয়। আদিম মানুষ নিজেদের আত্মার মতো তার চারপাশের জীব ও জড় সব কিছুর মধ্যে আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করতো। ফেটিশ শ্রেণীকে বাদ দিয়ে জগতের এই অসংখ্য আত্মাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমত- নদী, পর্বত, সমুদ্র, গাছ, পাথর, পাখি, সাপ প্রভৃতি প্রাকৃতিক জিনিসের আত্মার কল্পনা। এসবের নির্বাচিত আত্মাগুলোকে আদিম মানুষেরা নিজেদের চেয়ে শক্তিশালী মনে করতো। অন্তত এদের অনিস্ট করার ক্ষমতা যে বেশি সেটা তারা বিশ্বাস করতো। দ্বিতীয় শ্রেনীর আত্মা হলো মৃত মানুষের আত্মা। মৃত্যুর পর আত্মা বেঁচে থাকে এরকম এরকম অলীক ধারণা যে আদি মানুষদের মধ্যে ছিলো (আজও অনেকের মধ্যেই আছে) তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মৃত্যুর ফলে আত্মার ভালো বা মন্দ করার ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় বলে তারা বিশ্বাস করতো। পূর্বপুরুষদের উপাসনা সকল অসভ্য সমাজে প্রভূত বিস্তৃতি লাভ করেছিলো। তৃতীয় শ্রেণীতে রয়েছে বিশাল প্রাকৃতিক (সৌর কেন্দ্রিক) বস্তুগুলোর আত্মাকে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্তিকরণ। যেমন আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি একসময় মানুষের উপাস্য হয়ে উঠেছিলো। মানুষের ধারণা যখন কিছুটা উন্নত হয়েছিলো তখন তাদের মনযোগ গেলো এই বিশাল প্রাকৃতিক জিনিসগুলো সম্পর্কে। এন্ড্রু ল্যাঙ্গে তাঁর Making of Religion গ্রন্থে বলেছেন, ‘সর্বপ্রাণবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে অসভ্য মানুষেরা বিশ্বব্রক্ষ্মান্ডে অসংখ্য আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করলেও তারা সংজ্ঞার সাহায্যে একজন পিতার বা সবকিছুর স্রষ্টার কল্পনা করতো। তিনি আদি। অন্যান্য সাধারণ আত্মা অপেক্ষা তাঁর স্থান উর্ধ্বে। সেই আত্মার এতোদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, অসভ্যদের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টধর্মালম্বীদের মতোই একেশ্বরবাদী ছিলো। তাদেরও একজন পরমেশ্বর ছিলেন’ (Andrew Lange ; The Making of Religion, P. 167)। একথা হয়তো সত্য যে সমস্ত কিছুর অস্পষ্ট পশ্চাৎপটে একজন পরমেশ্বরের ধারণা অসভ্যদের মধ্যে একেবারে অপরিচিত ছিলো না। সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী আদিম মানুষ অনুভব করতো যে শত্রুভাবাপন্ন অসংখ্য আত্মার দয়ার উপর নির্ভর করে তাদের বাঁচতে হয়। তাই তারা সেই আত্মাদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতো। আত্মার সংখ্যা যতো বেড়ে যেতো তাদের সম্পর্কে ভয়ও ততো বাড়তো। এভাবেই ধর্মে ভয়ের ভূমিকা প্রাধান্য পেয়েছে। অসভ্য মানুষের ধর্মে ভয়ই প্রধান এবং ত্রুটি অসংখ্য। এদের এই সব অজস্র ত্রুটি এবং স্থুলতা, ছেলেমানুষী এবং অজ্ঞতা থাকার পরও বলা যায় সভ্য মানুষের আত্মার ধারণা অসভ্যদের আত্মার ধারণারই সংস্কৃত রূপ। ই বি টাইলর তাঁর Primitive Culture গ্রন্থের প্রথম খন্ড শেষ করেছেন এই কথা বলে – ‘আত্মা সম্পর্কিত মতবাদ (সর্বপ্রাণবাদ) ধর্মের দার্শনিক পদ্ধতির একটি প্রধান অংশ। বর্বরদের ফেটিশ উপাসনা এবং সুসভ্য খ্রীষ্টানদের উপাসনার মধ্যে মানসিক সংযোগের যে অবিচ্ছিন্ন ধারাটি রয়েছে তা এই মতবাদের ফলেই সম্ভব হয়েছে। যে বিভেদ বিশ্বের সকল বৃহৎ ধর্মমতগুলোকে পৃথক করে রেখেছে সেই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সুগভীর পার্থক্যের তুলনায় সর্বপ্রাণবাদ এবং জড়বাদের পার্থক্য অনেক বাহ্যিক।’ গোষ্ঠীর রীতি-নীতির প্রতি আনুগত্য থেকে নৈতিক চেতনা বিকশিত হয়েছে। মূলত টোটেমবাদ থেকে এর ধারাবাহিকতা শুরু গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য থেকে যেমন প্রশ্রয় পেয়েছে রক্ষণশীলতা, তেমনি আত্মিক বিশ্বাসের একটি পরিবেশও সৃষ্টি হয়েছে। অনেক সময় কোনো সাধারণ শত্রুর ভয়ে ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলো একত্রিত হতো। আবার কখনো কোনো শক্তিশালী গোষ্ঠী দুর্বলতর গোষ্ঠীগুলোকে জয় করে একটি বৃহৎ জনসমষ্ঠীতে পরিণত হতো। তার ফলে মানুষের মানসিক দিগন্তের বিস্তৃতি ঘটে এবং তার জীবনবোধ হয় গভীরতর। সামাজিক সংগঠনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনায়ও বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। সে সময় থেকেই বহু আত্মাবাদ বহু ঈশ্বরবাদে রূপান্তরিত হয়। আগে যে বহু আত্মা উপাসনা হতো সেই আত্মাগুলোকে কোনোমতে দেবতা বলা যায় না। তাদের কোনো ইতিহাস ছিলো না, ব্যক্তিগত চরিত্র ছিলো না, এমন কি একটা নামও ছিলো না। প্রাকৃতিক সেই আত্মাগুলোই ক্রমশ আধুনিকরণে মনুষ্য গুণসম্পন্ন হয়ে উঠলো। কল্পনা করা হলো, মানুষের মতো তাঁদেরও ভালোলাগা মন্দলাগা রয়েছে, আবেগ উচ্ছ্বাস আছে, তাঁদের আহ্বান করা যায়, এবং তাঁদের একটি নামও রয়েছে। এর অর্থ এই ধরা যাবে না যে, এরপর নদী, গাছ, আগুন, মেঘ, আকাশ প্রভৃতিতে যে সব আত্মা বসবাস করতো তাদের ধারণা শেষ হয়ে গেলো। বরং পূর্বে যে সব স্বর্গীয় দেবতাদের পুঁজো করা হতো না তারাই এসে আত্মার স্থান দখল করে বসলো। প্রকৃত ঘটনাটা কিন্তু অন্য রকম। নতুন কোনো স্বর্গীয় ঈশ্বর তখনো হাজির হয়নি। তাঁর উপস্থিতির আগেই ওইসব প্রাকৃতিক আত্মাগুলো ক্রমশ দেবত্বের মর্যাদা পেতে থাকে। কল্পনা শুরু হয় দেবতারা স্বর্গবাসী। তারপরও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আদিম সম্পর্কটি একেবারে মুছে গেলো না। অবশ্য ধীরে ধীরে দেবতার সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক কমে আসতে লাগলো। দেবতারা ক্রমশ নৈতিক ও মানবিক গুণসম্পন্ন হয়ে উঠলেন। তারা একেকজন প্রধান হয়ে উঠলেন রাষ্ট্র ও ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন বিভাগে। যেমন যুদ্ধের দেবতা, ভালোবাসার দেবতা, কৃষি, শিল্প ও সৌভাগ্যের, ঝড়-ঝ³ার আলাদা আলাদা করে দেবতা কল্পিত হলো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বৈদিক ‘অগ্নি’ আগুনের দেবতা, পারস্যের ‘আহুরা’ আলোর দেবতা, ব্যাবিলনের ‘মার্দুক’ এবং মিশরের ‘রা’ হলেন সূর্যদেবতা, গ্রীসের ‘জিউস’ এবং ল্যাটিন ‘জুপিটার’ স্বর্গের দেবতা, জার্মানের ‘ওডিন’ এবং বৈদিক ‘ইন্দ্র’ ঝড়ের দেবতা। এই সব ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বুনিয়াদের উপর আশ্রয় করে ধর্মীয় কল্পনার জাল বুনে দেবতাদের ব্যক্তিত্বের রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে। প্রাকৃতিক আত্মায় মানবত্ব আরোপ করার ফলেই যে সকল দেবতার সৃষ্টি হয়েছে এই ধারণা ঠিক নয়। মানুষের ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতির মধ্য থেকে এবং উৎসর্গ ও প্রার্থনার দ্বারাও অনেক দেবতার সৃষ্টি হয়েছে। এই ধরনের জাতীয় দেবতার মধ্যে আছেন, যেমন ভারতীয় ব্রহ্মা, মিশরের ওশিরিস, গ্রীসের অ্যাপোলো, ল্যাটিন মার্স, বৈদিক বরুন ও বিষ্ণু, হিব্রু জিহোভা প্রভৃতি। একবার যখন এঁদের ব্যক্তিগত গুন আরোপ করা হলো তখনই তাঁদের মরজগতের উর্ধ্বে, একটা অর্ধেক বাস্তব ও অর্ধেক আত্মিক জগতে স্থাপন করার মানসিক প্রবণতা দেখা দিলো। সেই জগতে দেব-দেবীদের নিয়ে একটি সমাজ কল্পনা করা হলো। আসলে ধর্ম বুদ্ধিধর্মী হওয়ার আগে থেকেই কল্পনা ও আবেগ প্রধান। ধর্ম হলো একরকমের অনুভূতি এবং সেই সঙ্গে চিন্তা ও ইচ্ছার সংমিশ্রণ। যথেচ্ছ কল্পনা অপরিণত চিন্তার প্রকাশ। জাতীয়ভাবে ধর্ম-বিকাশের ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ গতিভঙ্গি রয়েছে। প্রথমটি দেবতাদের উপর নৈতিক গুন আরোপ অন্যটি একেশ্বরবাদ অভিমুখি যাত্রা। দেবতাদের উপর নৈতিক গুনারোপের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বস্তুর আত্মা সম্পর্কিত ব্যাপারটি বাদ দিতে হবে। কারণ এর কোনো নৈতিক আলোচনা হতে পারে না। কিন্তু যখন আত্মার ধারণা প্রাকৃতিক বস্তুর আওতা ছাড়িয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের উর্ধ্বে মোটামুটি একটি অতীন্দ্রিয় জগতে স্থাপিত হলো এবং আত্মাকে মনুষ্যরূপে কল্পনা করা হলো, অন্তত আত্মাকে মনুষ্যগুনসম্পন্ন বলে মনে করা হলো, আর তখুনি প্রশস্ত হয়ে গেলো দেবতাদের মঙ্গলময় ও ন্যায়বান বলে ধারণা করার পথ। এরপর ক্রমশ দেবতারা মানুষের আদর্শ এবং নৈতিক অভিভাবক হয়ে উঠলেন। ধারণা প্রতিষ্ঠিত হলো তিনি সৎকে পুরুষ্কৃত করেন এবং অসৎকে শাস্তি দেন। তারপর থেকে দেবতাদের নৈতিক জগতের ধারক ও বাহকরূপে কল্পনা করা হতে থাকে। হফডিং বলেছেন, ‘প্রাকৃত ধর্ম থেকে নৈতিক ধর্মে উত্তরণকে ধর্মের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হিশেবে যে গণ্য করা হয়তো তা যথার্থ। বহু ঈশ্বরবাদী ধারণার একেশ্বরবাদে পরিবর্তিত হওয়ার ঘটনা অপেক্ষা এই পরিবর্তন অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ’ (H. Hoffding, The Philosophy of Religion, 1906, p. 326)। এভাবে দেবতাদের নৈতিক গুনারোপ করার কালে এক একজন দেবতা এক একটি গুনের প্রতীক হয়ে উঠেন। বিভিন্ন জাতির কাহিনীতেই এর উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন - ইন্দ্র (বেদ), মার্স (ল্যাটিন), থব (টিউটানিক) প্রভৃতি দেবতারা হয়ে উঠলেন বিশেষ করে সৌন্দর্যের প্রতীক বরুণ (বেদ) ও ওশিরিস (মিশরীয়) হলেন ন্যায় বিচারের দেবতা। পল্লস এ্যাথেনী (গ্রীক) প্রজ্ঞার দেবী, হেসিটা (গ্রীক) সতীত্ব ও গাহর্স্থ্য আদর্শের দেবী, জরথুস্ত্র ধর্মের প্রধান দেবতা আহুরা মাজদা হলেন অমঙ্গলের শত্রু এবং বিশ্বে নৈতিকতার পরিচালক। খ্রীষ্টপূর্ব ধর্মে ও টেস্টামেন্টেই দেবতাদের সম্পর্কে নৈতিক ধারণা সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থায় পৌঁছেছিলো। একেশ্বরবাদে অগ্রগতির ক্ষেত্রে জাতীয় ধর্মে কালক্রমে অনেক দেবতার মধ্যে কোনো একটি দেবতাকে বেশি করে প্রশংসা করার একটি প্রবণতা দেখা যায়। মানুষের সামাজিক জীবনের উপমার সাহায্যে দেবতাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা হতো। পৃথিবীর সমাজে একজন রাজা থাকেন, অতএব দেবতাদের সমাজে একজন রাজা থাকা স্বাভাবিক। এরপর আর অন্য দেবতাদের সমান ক্ষমতাসম্পন্ন থাকা সম্ভব হয় না। স্বর্গে একজন প্রধান দেবতার নেতৃত্বে অন্যান্য দেবতাদের প্রাধান্য অনুসারে ক্রমপর্যায়ে সাজানো হলো। উদাহরণস্বরেৈপ বলা যায়, গ্রীকের লোকেরা বিশ্বাস করতো- দেবতাদের এবং সকল মানুষের পিতা হলেন জিউস। রোমানদের মতে জুপিটার হলেন প্রধান। ব্যাবিলনে মার্দুক, আসিরিয়ায় অসুর এবং প্রাচীন চৈনিকধর্মে তায়েন (স্বর্গ) এবং সাংতি (দেবতাদের প্রধান) কে প্রধান বলে মনে করা হতো। পৃথিবীর সব জায়গায়, সকল জাতীয় ধর্মে দেবতাদের একটি রাজ্য কল্পনা করার প্রবণতা দেখা যায়। এই ধরনের বিশ্বাসকে দেবতাদের রাজতন্ত্রবাদ বলা যেতে পারে। ম্যাক্সমুলার যাকে একদেব প্রাধান্যবাদ বলেছেন তার মধ্যেও এই এক দেবতার প্রাধান্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। অন্য আরো একভাবে বহুর ধারণা ‘একে’ বিলীন হয়ে গিয়েছিলো। চিন্তনের সহায়তায় সকল দেবতাকে এক ঈশ্বরের বহুরেৈপে প্রকাশ বলে সিদ্ধান্ত করার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বহু দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করেও একেশ্বরের ধারণা যে লাভ করা সম্ভব তার প্রমাণ প্রাচীন মিশর। প্রাচীন মিশরে সূর্যদেবতাকে সকল দেবতার আত্মারূপে বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন - ‘আমিই স্বর্গ ও মর্ত্যের স্রষ্টা, ...... আমিই সকল দেবতার প্রাণ ..... আমিই সকালের চেপেরা (chepera), দুপুরের রা (Ra) এবং সন্ধ্যার ৎমু (Tmu)।’ ভারতেও অনেক বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে এই প্রবনতা নিদর্শন পাওয়া যায়। তার মধ্যে বহু পরিচিত মন্ত্রটি হলো, ‘ওগো অগ্নি, তুমি যখন জন্মগ্রহণ করো তখন বরুণ, যখন নিহত হও তখন মিত্র, তুমিই সকল দেবতা।’ তিনি এক। মুনিরাই তাঁকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। পরবর্তীকালে উপনিষদের কালে এই প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ব্রক্ষ্মা বা পরমসত্তা এক। পার্থিব জগতের এই বহুত্বের ধারণা ভ্রমজ্ঞান বা মায়া। বহুর মধ্য দিয়ে ‘এক’ নিজেকে প্রকাশ করেছে। বহু দেবতার ধারণা ও অন্যান্য সব কিছুর মতো এক সত্তার ধারণায় রেৈপান্তরিত হয়েছে। ভারতবর্ষে এই একশ্বরবাদ ব্যবহারিক প্রয়োজনে বহু ঈশ্বরের উপাসনা স্বীকার করে নিয়েছে। গ্রীসে এই প্রবণতার বিকাশ হয়েছিলো প্রধানত : জেনোফেনিস, পারমেনিডিস এবং স্টয়িক দার্শনিকদের প্রভাবে। গ্রীসে মানবরূপী বহু ঈশ্বরের ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে জেনোফেনিস এক পরম ঐক্যের ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন। ইন্দ্রিয়জ কল্পনার দ্বারা সেই ‘এক’ কে কখনো জানা সম্ভব নয়। সর্বেশ্বরবাদীদের মতো স্টয়িক দার্শনিকগণও ঈশ্বরকে ব্রক্ষ্মান্ডের আত্মা হিশেবে এবং বিশ্বচরাচরে অন্তর্বর্তী কারণ হিশেবে কল্পনা করেছিলেন। ধর্মের একেশ্বরবাদের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল ইস্রায়েলে। পৌত্তলিক ধর্মগুলোতে অতি অল্প সংখ্যক ভাববাদীর অন্তর্দৃষ্টিতে একেশ্বরবাদী ধারণা কখনো কখনো পেয়েছে, কিন্তু কখনোই এটি জনগণের ধর্ম হয়ে উঠতে পারেনি। পারস্যের জরথুস্ত্র একেশ্বরবাদের কাছাকাছি এসেছিলেন, কিন্তু তিনি ব্যক্তিগতভাবে যে সব দেবতাদের নির্বাসিত করেছিলেন, জেন্দ আভেস্তায় তাঁর উত্তরাধিকারীরা সেই সব দেবতাদের পূনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইস্রায়েলের সূচনায়ও প্রকৃত অর্থে একেশ্বরবাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সেখানে জাতীয় জীবনের সূচনায় কেবল শিক্ষক এবং নেতারাই জিহোভা-কে একমাত্র দেবতা বলে স্বীকার করতেন কিন্তু অন্যান্য জাতীয় দেবতাদের অস্তিত্বকে তখনো অস্বীকার করা হয় নি। যেমন মোয়াবাইট জাতির দেবতা ছিলেন ক্যামোস, অ্যামোনাইট-দের দেবতার নাম ছিলো মোলক, জিদোনীয়-দের দেবতা ছিলেন বাল। তথাপি জিহোভাই ছিলেন প্রধান বা একমাত্র দেবতা, যে দেবতাকে ইস্রায়েলের মানুষ উপাসনা করতো। জিহোভা ছিলেন তাদের একমাত্র ধর্মীয় আকর্ষণ। ধর্মীয় যা কিছু অভিজ্ঞতা বা যা কিছু আদর্শ তারা লাভ করতো, সব কিছুই পেতো জিহোভার কাছ থেকে। অন্য দেবতাদের উপাসনা রাজদ্রোহ হিশেবে গণ্য হতো। তার মানে এই নয় যে, সমস্ত লোক অন্য দেবতাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করতো। কিন্তু তারপরও তাদের কাছে জিহোভাই ছিলেন ইস্রায়েলের একমাত্র দেবতা। একে ঠিক একেশ্বরবাদ বলা যায় না। বরং একে দেবতা উপাসনা বলা যেতে পারে। অ্যামোসের সময় থেকে ইস্রায়েলের জননায়কদের মধ্যে উপলব্ধি হতে শুরু করে যে জিহোভার ঐশ্বরিক এবং নৈতিক রাজত্ব এতোদূর বিস্তৃত যে, তাঁকে কেবল ইস্রায়েলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সঙ্গত নয়। তাঁর রাজত্ব রয়েছে সমগ্র বিশ্বজুড়ে। অন্য কোনো দেবতাদের স্থান আর সেখানে নেই। এই জিহোভারই পরিবর্তিতরূপ ইসলামের আল্লাহ্। হঠাৎ করে ধর্মের বিশ্বজনীনতা প্রাপ্তি ঘটে নি। এর পেছনে ছিলো যথেষ্ট প্রস্তুতি। কিছু কিছু জাতীয় ধর্মে তৎকালীন সময় এই ধরনের প্রবণতা দেখা দিয়েছিলো। গ্রীস ও রোমান জগতে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতাব্দী থেকে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত যে রহস্যময় ধর্ম বিস্তৃতি লাভ করেছিলো তার মধ্যে বিশ্বজনীনতার লক্ষণ ছিলো সুস্পষ্ট। ইস্রায়েলে খ্রীষ্টপূর্ব অস্টম শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত ভাববাদীগণ বিশ্বজনীন ধর্মের শিক্ষা দিয়েছিলেন। রোমান এবং গ্রীসে জাতীয় দেবতাদের উপাসনা করা হতো প্রাচীন পদ্ধতিতে। ইস্রায়েলে এ্যামোস, ইশা (ীসাািড) এবং দ্বিতীয় ইশার শিক্ষায় জাতীয় ধর্মানুষ্ঠান অপেক্ষা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং অন্তরের বিশ্বাস বড় হয়ে উঠেছিলো। জেরোমিয়া (ঝরেমোিড) যখন ঘোষনা করেছিলেন, ঈশ্বর তাঁর শিষ্যদের নিয়ে ‘নতুন ধর্মশালা’ গড়ে তুলতে বলছেন, তখনই ধর্মের ইতিহাসে ‘আদর্শের বৃহত্তম এবং নবতম মূল্যায়ন’ হয়েছিলো বলা যায়। ‘আমি আমার আইন তাদের অন্তঃকরণে স্থাপন করবো, এবং তা তাদের হৃদয়ে লিপিবদ্ধ করে দেবো’ (ঝরে. ষষষি ৩১-৩৪)। ঈশ্বর ও মানুষের সম্পর্ক যদি আন্তরিকতা ও নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে যারাই সেই শর্ত পালন করবে তাদে স্কলের জন্য ধর্মের দুয়ার থাকবে উন্মুক্ত। জেরোমিয়া অবশ্য ঠিক এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত করেন নি। কারণ তখনো তাঁর চিন্তা ইস্রায়েলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। তবে তাঁর ‘নতুন ধর্মশালা’র ধারণার মধ্যে এরকম সিদ্ধান্েতর একটি প্রচ্ছন্নতা ছিলো। একই সঙ্গে ইস্রায়েলে আরো একটি ধারণার সৃষ্টি হয়েছিলো যে, জিহোভা কেবল ইস্রায়েলের নন, তিনি সমগ্র বিশ্বের একমাত্র ঈশ্বর। এই বিশ্বাসকে একেশ্বরবাদ বলা যেতে পারে। তিনি সমগ্র ইস্রায়েলের মানুষের যেমন বিচার করবেন তেমনি আরব, মিশর, ব্যাবিলনের মানুষেরও বিচার করবেন। পরবর্তীকালে ইহুদীরা ধর্মীয় এই ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গীকে সম্পূর্ণরেৈপে ত্যাগ করায় জুডাবাদ ক্রমশ একটি সংকীর্ণ বিশেষ মতবাদে প্রত্যাবর্তন করে। এইভাবে ইস্রায়েলের ধর্ম বিশ্বজনীন খ্রীষ্টধর্মের বুনিয়াদ গড়ে দিলেও নিজে জাতীয় ধর্ম থেকে যায়। তবে একথা সত্যি যে, সমস্ত শ্রেণী ও জাতির বাধা ভেঙে সকল মানুষকে পরিত্রাণের প্রথম পথ দেখিয়েছিলো বৌদ্ধধর্ম। যেমন খ্রীষ্টধর্মের আবির্ভাব হয়েছিলো জুডাবাদ থেকে, তেমনি ব্রাক্ষ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং সংস্কার সাধন করে উৎপত্তি হয়েছিলো বৌদ্ধ ধর্মের। ব্রাক্ষ্মণ্য ধর্ম এক স্বতন্ত্র শ্রেনীর ধর্ম। এই ধর্মে আছে অত্যন্ত শ্রমসিদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান, কৃচ্ছতাসাধন এবং সর্বেশ্বরবাদী দূর কল্পনা। বৌদ্ধ ধর্ম ধর্মীয় ক্রমবিকাশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। লক্ষনীয় বিষয় হলো এই ধর্মে পাপ থেকে পরিত্রানের কথা চিন্তা করা হয় নি। দুঃখ কষ্টের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের কথা বলা হয়েছে মাত্র। যখন সকল আবেগ ও আকাংক্ষা, এমন কি বাঁচার আকাংক্ষাও লোপ পাবে, তখনই মানুষ নির্বাণ লাভ করতে পারবে। নির্বাণ হলো সম্পূর্ণ নিস্পৃহ এক শান্তির অবস্থা। ব্রাক্ষ্মণ্য ধর্মের আত্মা সম্পর্কিত অনেক ধারণাকে গৌতম বুদ্ধ অস্বীকার করেছেন। ব্রাক্ষ্মণ্য ধর্মে আত্মা দ্রব্য হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু বুদ্ধদেব তাও স্বীকার করেন নি। তাঁর মাত্র তথাকথিত আত্মা মায়া মাত্র। মানুষ কতগুলো কামনা-বাসনার সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ যা করে তার মধ্যে দিয়েই তার মনুষ্যত্বের প্রকাশ ঘটে। কর্ম যোগই প্রকৃত সত্য। নীতিগতভাবে বুদ্ধ হয়ত নাস্তিক ছিলেন না, কিন্তু তিনি দেবতাদের অস্বীকার করেছেন। ব্রাক্ষ্মণ্য দর্শনের ব্রক্ষ্ম সম্পর্কে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিলো না। মানুষকে ভবচক্র থেকে মুক্ত করার কোনো সাহায্য দেবতারা করতে পারেন না। কারণ দেবতা মানেই তথাকথিত একটি কল্পিত বিষয়। বুদ্ধ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, ‘‘মুক্তির জন্য মানুষকে নিজেরই চেষ্টা করতে হবে। কোনো দৈব সাহায্য সে পাবে না। প্রার্থনা একটা অন্তঃসার শূন্য ব্যাপার। উপাসনা নিরর্থক।’’ বৌদ্ধ ধর্মকে অনেকেই ধর্ম বলে স্বীকার করতে রাজী নন। কারণ এই ধর্মে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান নেই। মোক্ষ লাভের ক্ষেত্রে দেবতাদের কোনো ভূমিকা নেই। বুদ্ধদেব স্বয়ং তাঁর শিষ্যদের উপাসনা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়েছেন। অথচ যে মতবাদ তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন ধর্ম হিসেবে বৌদ্ধ ধর্ম বর্তমানে সেই মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কালানুক্রমিকভাবে খ্রীষ্টধর্ম হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বজনীন ধর্ম। মূল থেকেই এ ধর্মটি পুরোপুরি মিথ্যাশ্রয়ী (অবশ্য মিথ্যার অবলম্বন ছাড়া কোনো ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার্য নয়)। একটি কুমারী মাতার গর্ভে ‘অলৌকিক’ জন্মকে কেন্দ্র করে, সমস্ত সাধারণ ঘটনার অসাধারণ রূপায়নের নাম হচ্ছে- খ্রীষ্ট ধর্ম। সেন্ট পল এর মতো ধুরন্ধর, মিথ্যেবাদী, বজ্জাত লোকের আবির্ভাব না ঘটলে খ্রীষ্টধর্মের বিশ্বজনীনতার প্রশ্ন ছিলো অবান্তর। অত্যন্ত মিথ্যেবাদী, চতুর, দুধর্ষ, গুন্ডাপ্রকৃতির লোক ছিলেন পল। যীশু নিজে কোনো ধর্ম দিয়ে যাননি, এবং সবচেয়ে মজার ঘটনা হচ্ছে ক্রুশেও মৃত্যু ঘটে নি তাঁর। আজ ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে এ কথা প্রমাণিত সত্য। এমনকি ৪: ১৫৭ বচনে কোরানও এ কথা স্বীকার করে যে, ক্রুশে যীশুর মৃত্যু হয়নি। তারপরও উক্ত ধর্মের অধিকাংশ মানুষ একথা বিশ্বাস করে আবেগাপ্লুত হল যে, যীশু সশরীরে স্বর্গে চলে গেছেন এবং অদ্যাবধি তিনি ঈশ্বরের দক্ষিণে অবস্থান করছেন এবং বিশ্ব ধ্বংস প্রাপ্তির সময়, অর্থাৎ কেয়ামতের পূর্বে আবার তিনি সশরীরে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করবেন। ইসলামী দর্শনে এমন একটি গাঁজাখুরি মতবাদের প্রশ্রয় লাভ ঘটেছে প্রারম্ভিককালে ইসলামে ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টানদের অন্ধ-কুবিশ্বাস থেকে। এ ব্যাপারে আমার যীশু সম্পর্কিত গবেষণামূলক (‘‘যীশু শুয়ে আছেন ভারতে’’ গ্রন্থটি পড়া যেতে পারে, এ ছাড়া মুক্তান্বেষায় প্রকাশিত ‘যীশুর মৃত্যু- একটি রহস্য’ দ্রঃ) গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে খ্রীষ্টান ধর্মের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে অনেক সাদৃশ্যও রয়েছে। তরবারির যে অমানবিক রক্তপাতে ইসলাম প্রথম সমাজের অশিক্ষিত, দুর্বল, নিম্নশ্রেনীর মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিলো তারচেয়ে ও নির্দয় ও বীভৎস কায়দায় প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হয়েছে ভন্ড পলের সৃষ্ট খ্রীষ্ট ধর্মের পান্ডারা। তাঁরা ক্রুশে মৃত্যু না হওয়ার পর আতঙ্কজনক, পলায়মান যীশুর কাল্পনিক গল্প প্রচার করে, জোর-জবরদস্তি আইন করে, তৎকালীন সমাজের বিজ্ঞানমনস্ক মানুষদের সমাজে একঘরে করে, তাঁদের বইপত্র, পান্ডুলিপি পুড়িয়ে, যীশুর ‘হোলি স্প্রীট’ এর ভুয়া ধুঁয়া তুলে ‘খ্রীষ্টধর্মের দর্শন’ প্রতিষ্ঠা করেছে। এর প্রায় ছয়শ বছর পর একই কায়দায় ইসলামের আবির্ভাব। অত্যন্ত ধৈর্যহীন, অসহিষ্ণু এই ধর্ম হলো তরুণতম বিশ্বজনীন ধর্ম। অন্য দুটি বিশ্বজনীন ধর্ম অপেক্ষা ইসলাম প্রকৃতিতে অনেক কম সার্বজনীন। যুগের পর যুগ ধরে এই ধর্ম মূল সীমেটিক এবং এমনকি আরবীয় চরিত্র পালন করে এসেছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করার মতো স্বচ্ছতা, প্রসারতা এই ধর্মের নেই। ইসলাম অত্যন্ত গোঁড়া ধর্ম। স্থবির ধর্ম। আরবীয় স্টাইলের বাইরে এর কোনো নড়াচড়া নেই। কোনো রকম পরিবর্তন এই ধর্মে স্বীকৃত নয়। এমন কি আচার অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটিগুলিও অপরিবর্তনযোগ্য। নতুনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের যে সুযোগ খ্রীষ্টধর্মে রয়েছে, ইসলামে তা নেই। কোরানের একটি জের-জবর-নক্তাও ইসলাম পরিবর্তনের অনুমোদন করে না। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মুসলমানেরা আজ যে কোরানকে একেবারে অপরিবর্তিত ঐশ্বরিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করে, প্রথম দিকে, গ্রন্থনকালে এর ব্যাপক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকরের সময় কোরানের প্রথম লিপিবদ্ধ পান্ডুলিপিগুলো তৃতীয় খলিফা ওসমানের সময় আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। প্রথম অবস্থায় কোরানের সাত প্রকারের সংস্করণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছিলো। এগুলো ছিলো প্রথম দুটি মদীনায়, তৃতীয়টি মক্কায়, চতুর্থটি কুফা নগরে, পঞ্চমটি বসরায়, ষষ্ঠটি সিরিয়ায় এবং সপ্তমটি এমন কদর্য ছিলো যে, সেটাকে সামান্য সংস্করণ হিসেবে লিপিকারগণ সেটির স্থানের নামই উল্লেখ করেন নি। সেই সাতটি লিপিবদ্ধ কোরানে এমন অনেক বিষয়াদি ছিলো ‘যা পাঠে মানুষ বিপথগামী হইবে’ এই বিবেচনায় সেগুলোকে পুড়িয়ে নষ্ট করে নতুনভাবে সংকলিত করা হয় ‘ঐশীগ্রন্থ’ নামক আজকের কোরানকে। এরকম রুক্ষ কথা শুনে অনেক মুসলমানই অতৃপ্ত হতে পারেন, কিন্তু পারেন না ঐতিহাসিক সত্যকে হাওয়ায় মিলিয়ে দিতে। গোঁড়া ইসলামপন্থীরা এতোই অসহিষ্ণু ও ধর্মান্ধ যে এরা সুস্থিরভাবে ধর্মীয় কোনো ব্যাপারকেই বিবেচনায় নিতে অক্ষমতা প্রকাশ করে, অথচ নিজেরা ইসলামী বিধি-বিধান, নিয়মকানুন একজনও সঠিক, সুষ্ঠভাবে পালন করে না, কিন্তু নিজেদেরকে ‘মুসলমান’ বলে আত্মপরিচয় দিতে তৃপ্তি বোধ করে। ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মোহম্মদের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুকালে কোরান গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ ছিলো না। তাঁর মৃত্যুর পরের বছরই ওমরের পরামর্শে প্রথম খলিফা আবু বকর কোরান গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার জন্য জনৈক যায়েদ ইবন্ সাবেতকে প্রধান করে ১০ জনের একটি কমিটি গঠন করেন। এ ব্যাপারে ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন তাঁর অনূদিত কোরানের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় লিখেছেন, ....‘জয়দ নামক জনৈক মদীনাবাসী পন্ডিত উৎসাহের সহিত এই সংগ্রহকার্যে প্রবৃত্ত হইয়া বহু পরিশ্রমে নানা স্থান হইতে খর্জুর-পত্রে লিখিত, শ্বেত প্রস্তরে খোদিত এবং মানুষের বক্ষে চিত্রিত আয়াত সকল সংগ্রহ করেন। এই সংগ্রহীত বচন সকল প্রথমত আমীর আবু বকরের নিকট ছিল, পরে তাঁহার মৃত্যুকালে হফ্সা নাম্নী হযরতের পত্নীর নিকটে গচ্ছিত থাকে। নেতৃবর ওমর ফারুক যাবজ্জীবন এই গ্রন্থকেই মান্য করিয়া চলিয়া ছিলেন। তাঁরা মৃত্যুর পর আমীর ওসমানের সময় নানা স্থানে ইহার প্রতিলিপি বিস্তৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে সমস্ত পরস্পর এতো বিভিন্নরূপে লিখিত হইয়াছিল যে, তাহার জন্য মোসলমান মন্ডলীর মধ্যে ভয়ানক বিবাদ আরম্ভ হইল। ইহাতে ওসমান পুনরায় সেই জয়াদের দ্বারা কোরান সংগ্রহ করিয়া তাহাই সমস্ত মুসলমানকে মান্য করিতে বাধ্য করেন। তিনি এই নূতন গ্রন্থের বহু খন্ড প্রতিলিপি করাইয়া সমস্ত প্রধান নগরে প্রেরণ পূর্বক পূর্বলিখিত সমস্ত কোরআন অগ্নিতে দগ্ধ করাইয়া ফেলেন’ (ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন অনূদিত ‘কোরআন শরীফ’ এর ২য় সংস্করণের ভূমিকা, পৃঃ ১১-১২, হরফ প্রকাশনী, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা)। এ বিষয়টি সম্প্রতি বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত মোহম্মদ মতিওর রহমানের ‘ঐতিহাসিক অভিধান’ গ্রন্থে উল্লেখিত আছে। আবু বকর থেকে ওসমান পর্যন্ত কোরানের প্রথম পর্বে লিখিত সংস্করণগুলোর সময়কাল ছিল ১৯ বছর। ৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে ওসমান আবু বকরের সময়কার যায়েদ কর্তৃক কোরানের প্রথম লিপিবদ্ধ সংস্করণগুলো পুড়িয়ে ফেলেন। এবং পরবর্তিতে ওসমান সেই যায়েদ ইবনে সাবেতকেই আবার নতুন করে কোরানকে লিপিবদ্ধ করার কাজে মনোনীত করেন। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গিরিশ চন্দ্র তাঁর ভূমিকাতে ১২ পৃষ্ঠার টিকায় কোরান সংগ্রহকারী বলে ‘জয়দ’ নামের যার কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি তাঁকেই মোহম্মদের মৃত্যুর ক্রীতদাস-পরে ধর্মপুত্র যায়েদ বিবেচনা করেছেন, এ তথ্য সঠিক নয়। কারণ মোহম্মদের মৃত্যুর তিন বৎসর আগে তাঁর ধর্মপুত্র যায়েদ সিরিয়ার সন্নিকটে রোমান-শাসক শোহারাবিলের সৈন্যদের হাতে নিহত হন, এবং যায়েদের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী জয়নবকে মোহম্মদ বিবাহ করেন। অতএব কোরান লিপিবদ্ধ কাজে নেতৃত্বদানকারী যায়েদ এবং মোহম্মদের ধর্মপুত্র যায়েদ কিভাবে একই ব্যক্তি হন? ইসলাম ধর্মে আরবের মুসলমান এবং ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য আলোচিত ধর্মমতগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ইসলাম ধর্মে বিশেষ কোনো অভিনবত্ব দেখা যায় না। ইসলাম ধর্ম হলো জুডাবাদের (ইহুদীদের) বিশেষ কয়েকটি দিক, এবং অধঃপতিত খ্রীষ্টধর্মের (খ্রীষ্টানদের) কিছু ভ্রান্ত জ্ঞানের সংমিশ্রণ। খ্রীষ্ট ধর্মের ঈশ্বরের ধারণার থেকে ইসলামের ধারণা যে শ্রেষ্ঠ এবং ইসলাম ধর্মেই বৌদ্ধিক এবং সামাজিক প্রগতি যে অধিকতর হয়েছে এটিকে প্রতিপন্ন করার জন্যে জ্ঞান অপেক্ষা, বল ও ক্ষমতার প্রয়োগ করতে হয়েছে বেশি। আজ থেকে প্রায় ছয়শত বছর আগে ইবন বতুতা তাঁর ‘রেহলা’ গ্রন্থে লিখেছেন, .... ‘যে দিন থেকে আরবরা তলোয়ার হাতে নিয়েছে, সে দিন থেকেই অন্য জাতিরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ শুরু করেছে।’ এই ধর্মের আল্লাহ্ সম্পূর্ণরূপে অতিবর্তী। একজন প্রাচ্য দেশীয় এক নায়ককে খুব বড় করে দেখলে যেমন হয় ইসলাম ধর্মের আল্লাহ্ তেমনি স্বেচ্ছাচারী, দায়িত্বজ্ঞানহীন, এবং স্বৈরশাসকরূপী প্রভু। কথায় কথায় চোখ রাঙানো হচ্ছে তাঁর বড় কাজ। তিনি স্বর্গের সুলতান। কিন্তু তাঁকে দেখাও যায় না, বোঝাও যায় না, অথচ মানুষ তাঁর দান, একান্তরূপে তাঁর সম্পত্তি! এবং বিশ্বের সকল কিছু তাঁর ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত! ইসলামের আল্লাহর গুনের মধ্যে কোনো প্রেম বা পবিত্রতার স্থান নেই, আছে কেবল ধমক আর হুমকি, সঙ্গে পরকাল বিষয়ক ইন্দ্রিয় সুখ-ভাগের লোভনীয় ইঙ্গিত। আগাগোড়াই ইসলাম প্রগতি-পরিপন্থী। ২ ‘ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন’ এই তত্ত্বটির মধ্যে রয়েছে ধর্মের সবচেয়ে বড় ফাঁকি। আদমের উৎপত্তি কাল থেকে বাইবেলের হিসেব অনুযায়ী আব্রাহাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন আদমের ১৯৪৮ বছর পর। এবং আব্রাহামের জন্ম থেকে যীশুর আবির্ভাব ঘটেছিলো ১৮৫২ বছর পর। অর্থাৎ আদম থেকে যীশুর সময়ের ব্যবধান ৩৮০০ বছর। বাইবেলে বিশ্বসৃষ্টির সময়কাল যেমন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনি পৃথিবীতে কবে মানুষের আবির্ভাব হয়েছিলো তাও নির্দিষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। আজকের ২০০৮ সনকে ভিত্তি হিসেবে হিসেবে ধরে নিলে ওই হিসেব অনুসারে দেখা যায় আজ থেকে মাত্র ছয় হাজার বছর আগে (যীশুর জন্মের ৩/৪ বছর পর থেকে খ্রীষ্টীয় সন গণনা শুর হয়, সেই হিসেবে) বিশ্বসৃষ্টির সূচনা ঘটেছিলো। আর মানুষ সৃষ্টি হয়েছিলো, অর্থাৎ প্রথম মানব আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে- এর মাত্র দিন কয়েক পরেই। বাইবেলের এই সৃষ্টিতত্ত্বকে ইসলাম সমর্থন করে। কিন্তু এই সৃষ্টিতত্ত্ব আজ বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত মিথ্যে। এখন থেকে প্রায় ২৫০০০ বছর আগে বিশুদ্ধ আধুনিক মানুষ ক্রোম্যাগনন্ মানুষ বা হোমস্যাপিয়েন্স -এর উদ্ভব। তার আগে পর্যন্ত বহু হাজার বছর ধরে নিয়ানডার্থাল মানুষ পৃথিবীর নানা প্রান্তে টিকে ছিলো। তারা ছিলো শিকারী, গুহায় বসবাস করতো। পরিবার গঠনের প্রাথমিক প্রয়াস তাদের মধ্যেই লক্ষ করা গেছে। তাদের মস্তিষ্ক আধুনিক মানুষের মতো উন্নত ও জটিল না হলেও পূরববর্তী যে কোনো মানব প্রজাতির চেয়ে বিকশিত ছিলো। এবং এর সাহায্যে তারা দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য নানা কিছুর মতো, জীবনের রহস্য ও মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা অথবা এ ব্যাপারে চিন্তা করতে পারার প্রচেষ্টায় তারা সফল হতে পেরেছিলো বলেই মনে হয়। কারণ মাটি খুড়ে তাদের কবরের গুহা ও গহ্বর থেকে এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে যা থেকে স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে, মৃত্যুর পরেও যাতে মৃত ব্যক্তির কোনো অসুবিধা না হয় তার জন্য দৈনন্দিন প্রয়োজনের কিছু দ্রব্যাদি শবের সঙ্গে রেখে দেওয়ার পদ্ধতি তারা অনুসরণ করতো। মৃত শরীরকে নষ্ট না করে বা অবহেলায় ফেলে না রেখে কবর দেওয়ার ব্যাপারটিও ছিলো অভিনব ও যুগান্তরকারী একটি আবিষ্কার। আর এভাবেই মৃত্যু পরবর্তী ‘প্রাণ’ বা প্রাণের কারণ হিসেবে ‘আত্মা’ জাতীয় কোনো একটি কিছুর সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা যে তারা ধীরে ধীরে শুরু করেছিলো তা বোঝা যায়। মানুষের লিখিত ইতিহাসের বয়স মাত্র ৫০০০ বছর। ৭/৮ হাজার ধরে সে ধাতু ব্যবহার করেছে। তার আগে লক্ষ লক্ষ বছর আদিম মানুষ পাথরই ব্যবহার করতো, তখন তাদের ধর্মচেতনাও ছিলো অনুরেৈপভাবে আদিম। কিন্তু ধর্মের প্রাথমিক উপাদান ৪০/৫০ হাজার বছর আগে নিয়ানডার্থাল মানুষের চেতনাতেই উদ্ভাসিত হয়। সম্ভবত তারাই প্রথমে আত্মা, অলৌকিক শক্তি, অতীন্দ্রিয় শক্তি ইত্যাদি ধারণার ভিত্তি সৃষ্টি করে। আত্মার আদিম ধারণাই হাজার হাজার বছর পল্লবিত হয়েছে ওই আদিম মানুষের মনে। আর সেটাই বহু সহস্র যুগ নিয়ানডার্থাল থেকে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণীর বংশ পরম্পরার ধারাবাহিকতায় ক্রম বিবর্তনের ফলে এই বিশ্ব ব্রক্ষ্মান্ডের সৃষ্টিকর্তা, তথা প্রাণের সৃষ্টিকর্তা ও সমস্ত আত্মার উৎস-স্বরূপ এক পরমশক্তি বা পরমেশ্বরের ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীতে ধর্মগুলোর সৃষ্টি হয়েছে বড় জোর বিগত ২ থেকে ৪ হাজার বছরের মধ্যে। এখনো অব্দি পাওয়া বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে এটি জানা গেছে, মানুষের মনে ধর্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিলো এখনকার মানুষের পূর্বসূরী নিয়ানডার্থাল ,মানুষের আমলে - যারা পৃথিবীতে ছিলো এখন থেকে আড়াই লক্ষ থেকে ৪০/ ৫০ হাজার বছর আগে Mousterian Period: Pleistocene epoch -এর একটি অংশ। তখন শাসক শাসিত শ্রেণীবিভাগ ছিলো না। মানুষ নিছক তার অনুসন্ধিৎসার ফলে, অজ্ঞতা ও অসহয়াতার কারণে তার ‘উন্নত’ কল্পনাশক্তির সাহায্যে তথাকথিত আদি ধর্মের সৃষ্টি করেছে। তখনকার পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এটি ছিলো একটি উন্নতর বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। ধর্মকে শাসক শ্রেণীর অপব্যবহারের কাজ, যা ঐতিহাসিক প্রকৃয়ায় সৃষ্টি হয়েছে, সেটা অনেক অনেক পরের ব্যাপার। নিয়ানডার্থাল মানুষের আগের স্তর অর্থাৎ পিথেকানথ্রোপাস বা সিনানথ্রোপাস-দের মধ্যে ধর্মাচরণের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নি। তখনকার মানুষের মস্তিষ্ক তথা চিন্তা করার ক্ষমতা এতোটা উন্নত ছিলো না, যার সাহায্যে ধর্ম ও অতিপ্রাকৃতিক শক্তি জাতীয় উন্নতর চিন্তা করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতো। মানুষকে তখন স্থুল জৈবিক প্রয়োজনেই প্রকৃতির প্রতিকুল অবস্থা ও জীবজন্তুদের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয়েছে। নিতান্তই ব্যবহারিক প্রয়োজনে তাদের চেতনা ব্যতিব্যস্ত ছিলো। প্রাণ ও প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু হাজার হাজার বছরের অস্তিত্বের মাধ্যমে তাদের মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে, জীবনযাত্রা রেৈপান্তরিত হয়েছে, পথ পরিষ্কার হয়েছে নিয়ানডার্থাল সৃষ্টির। ধর্ম আলোচনার প্রসঙ্গে নিয়ানডার্থাল মানুষের আগেরকার ঐ অবস্থাকে বিজ্ঞানীরা বলে প্রাকধর্মীয় অবস্থা। এরপর উদ্ভব হয় নিয়ানডার্থাল মানুষদের, পৃথিবীতে তখন চতুর্থ হিমযুগ চলছে। ১৮৫৬ সালে জার্মানির ডুসেলডর্ফের কাছে নিয়ান্ডার উপত্যকায় পাওয়া গেলো এই ধরণের ভিন্নতর ও উন্নতর মানুষের অসম্পূর্ণ কঙ্কাল। তার আগে জিব্রাল্টারেও অবশ্য এ ধরনের একটি কঙ্কাল পাওয়া যায়। পরে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ইতালী, স্পেন, রাশিয়া, পোল্যান্ড, ক্রিমিয়া, এশিয়া মাইনর, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, ইরাক, উত্তর আরবের মরুভূমি অঞ্চল, উত্তর আফ্রিকা, চীন ইত্যাদি বহু অঞ্চলে, এ ধরনের মানুষের কঙ্কাল, কবর ও অন্যান্য নানা নিদর্শন পাওয়া গেছে। ক্রোম্যাগনন্ মানুষের মতো বুদ্ধিমান মানুষের অস্তিত্বের পর্যাপ্ত ও সঠিক প্রমান বিজ্ঞানের হাতে এখন মজুত আছে। আজ এ সব তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের কাল ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত গল্প-কথার প্রথম আদম সৃষ্টির সময়কালের চেয়েও অনেক-অনেক বেশী প্রাচীন। মজার ব্যাপার হলো এই মানুষ সম্পর্কে বাইবেলেই রয়েছে উল্টোপাল্টা, স্ববিরোধী কথাবার্তা। অস্ট্রেলিয়ার ‘র্যাশনালিষ্ট এসোসিয়েশন অব নিউ সাউথ ওয়েলস’ বাইবেল থেকে এমন পরস্পর বিরোধী বহু উদাহরণ প্রকাশ করেছেন। এখানে কেবল মাত্র মানুষ সম্পর্কিত বাইবেলের ৬টি স্ববিরোধী উক্তি উল্লেখ করা হলো :- (১) মানুষ সৃষ্টি হওয়ার আগে গাছ এলো (জেনেসিস ১: ১১-১২), মানুষ তৈরি হওয়ার পর গাছ সৃষ্টি হলো (জেনেসিস ১: ৭-৯)। (২) জন্তু জানোয়ারদের পরে মানুষ সৃষ্টি হলো (জেনেসিস ১: ২৫-২৬), জন্তু জানোয়ারদের আগে মানুষ সৃষ্টি হলো (জেনেসিস ২: ১৮-২০)। (৩) আদম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার দিনই মরবে (জেনেসিস ২: ১৭), আদম ৯৩০ বছর বেঁচে ছিলো (জেনেসিস ৫: ৫)। (৪) ঈশ্বর মানুষকে লোভ দেখান না (জেমস ১: ১৩), ঈশ্বর মানুষকে লোভ দেখান (জেনেসিস ২২: ১/২, স্যামুয়েল ২৪: ১)। (৫) কোনো মানুষ ঈশ্বরকে দেখননি বা দেখতে পারেন না (জন ১: ১৮/১, টিম ৬: ১৬), অনেকের কাছেই তিনি দেখা দিয়েছেন (জেনেসিস ২৬:২, এক্সোডাস ২৪: ৯-১০, ৩৩: ২২-২৩)। (৬) কেউই ঈশ্বরের মুখ দর্শন করার পর বেঁচে থাকতে পারে না (এক্সোডাস ৩৩: ২০), জেকব ও মুসা দু’জনেই ঈশ্বরকে মুখোমুখি দেখেছেন কিন্তু মরেন নি (জেনেসিস ৩২ : ৩০, এক্সোডাস ৩৩: ১১)। বাইবেলের আরো যে বিখ্যাত অপবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটি মিথ্যে প্রতিপন্ন হয়েছে তা হলো পৃথিবী সম্পর্কিত তত্ত্ব। বাইবেল ও কোরানের ভাষ্য অনুযায়ী পৃথিবী স্থির। কিন্তু এখন আমরা নিশ্চিত, পৃথিবী স্থির নয়। সে ঘুরছে। আজ থেকে চারশ বছর আগে খ্রীষ্টধর্মের পান্ডা-পুরুতগণ ব্রুনোকে ক্রুশে বেঁধে জীবনত পুড়িয়ে মেরেছিলেন কেবলমাত্র এই অপরাধের জন্য যে, তিনি এরিস্টটলের তত্ত্বকে অস্বীকার করে কোপার্নিকাসের গ্রন্থের মতবাদকে সমর্থন করে বলেছিলেন, সূর্য স্থির নয়, এই পৃথিবীটাই ঘুরছে সূর্যের চারপাশে। এটা ছিলো বাইবেলে বর্ণিত পৃথিবীতত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত বা বিরোধী মতবাদ। এখানে এ বিষয়ে একটি কথা বলে নেওয়া অত্যন্ত জরুরী যে, কোপার্নিকাসেরও দু’হাজার বছর আগে মানব সভ্যতার কিছু কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত ছিলো যে, পৃথিবী বৃত্তাকার, সে একটি গ্রহ এবং ঘূর্ণায়মান। আয়োনীয় সভ্যতার কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে তিনটি সুপষ্ট স্থরে ভাগ করা চলে - আয়োনীয়, এথেনীয় ও হেলেনীয় যুগ। এ তিনের মধ্যে বিজ্ঞান ও বস্তুবাদের চরম উৎকর্ষের দাবি রাখে আয়োনীয় সভ্যতা। আয়োনীয় যুগ খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। আয়োনীয় সভ্যতাতেই প্রথম ঘটেছিলো বস্তুবাদের উন্মেষ। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ট শতাব্দীতে আয়োনীয়ার মাইলেটাস ছিলো গ্রীক জগতের বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র এবং সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ অঞ্চল। এখানে এ সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব বিয়াকশ ঘটে। যাকে অনেক ভাববাদী ঐতিহাসিকগণ অলৌকিক বলে অভিহিত করেন। কিন্তু গভীর ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে আয়োনীয়ার যে প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিলো তা অলৌকিক কিছু তো নয়ই, আকস্মিকও নয়। গ্রীক সভ্যতা ছিলো পূর্বাগামী প্রাচ্য সভ্যতার অনুবৃত্তি। গ্রীক বৈজ্ঞানিক তৎপরতার ভিত্তিভূমি দীর্ঘকাল ধরে রচিত হয়েছিলো মিশর ও ব্যাবিলনিয়ার। ভৌগলিকভাবেও মাইলেটাস ছিলো প্রাচীন সভ্যতাগুলোর নিকটবর্তী। মিশরের সাথে জলপথে এবং ব্যাবিলনের সঙ্গে স্থলপথে এর যোগাযোগ ছিলো। বস্তুতঃ গ্রীক পন্ডিত ও দার্শনিকগণ যে প্রাচ্য সভ্যতার কেন্দ্রগুলো ভ্রমণ করতেন তা নিশ্চিত ধারণা করার সঙ্গত কারণ আছে। আর এই আয়োনীয়াতেই তিনশ’ বছর আগে হোমার যে ধর্মীয় সংস্কারহীন মুক্ত চিন্তাধারার সৃষ্টি করেছিলেন, তা আয়োনীয় বিজ্ঞানের উৎপত্তি ভাবগত পটভূমি হিসেবে কাজ করেছিলো। আয়োনীয়াতে যে বিজ্ঞান ভূমিষ্ট হয়েছিলো, সে বিজ্ঞান হলো, অধ্যাপক বেঞ্জামিন ফ্যারিংটনের ভাষায় - ‘একটি বিজ্ঞানমনস্ক নবীন জাতির স্বাভাবিক কর্মতৎপরতা, একটি বলিষ্ঠ মানবতাবোধ এবং একটা বিশ্বজনীন সংস্কৃতির মিলিত ফল। ’ আয়োনীয় যুগ বিজ্ঞান ও দর্শনের ইতিহাসে মানুষের এক গৌরবময় অধ্যায়। আয়োনীয় দর্শন ছিলো বস্তুবাদী দর্শন। কিন্তু আয়োনীয়দের এই বিজ্ঞানচর্চার মুক্ত পরিবেশ স্থায়ী হয়নি। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে আয়োনীয় সভ্যতার বিলুপ্ত ঘটে। পারসিক আক্রমণে আয়োনীয়ায় রাজনৈতিক ও সামাজিক গোলোযোগ দেখা দেয়। এর ফলে সেখানকার বৈজ্ঞানিক দার্শনিক পন্ডিতগণ বাস্তুহারা হয়ে পড়েন। মানব সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় সবচেয়ে উজ্জ্বল সভ্যতা আয়োনীয়া হয়ে পড়ে মৃত! জ্যোতির্বিজ্ঞানে আয়োনীয়রা ২৬০০ বছর আগেই এমন উন্নতি সাধন করেছিলো যা আজ ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। আজ আমরা মানুষেরা পৃথিবী নামক শ্যামল গ্রহে বসে চাঁদ এবং মঙ্গলকে বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা করছি, যে স্বপ্ন দেখছি, সেই মানুষেরা তাদের জ্ঞানের সংগ্রাম শুরু করেছিলো লক্ষ বছর আগে। তারপরও তথাকথিত ঈশ্বর, দেবতাদের প্রভাবকে এড়িয়ে, একটি সাধারণ নিয়মের মাধ্যমে পদার্থ ও বিশ্বকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা প্রথম হয়েছিলো আয়োনীয়াতে - থেলিস, অ্যানাক্সিম্যান্ডার, অ্যানাক্সিমেনিস, হিরাক্লিটাস, পিথাগোরাস, ডেমোক্রিটাস, এমপিডক্লাস, অ্যানাক্রোগোরাসের মতো বিজ্ঞানীদের হাতে। তাঁরা বলেছিলেন, সবকিছু পরমানু দিয়ে তৈরি, মানব প্রজাতি বা অন্যান্য প্রাণীদের উদ্ভব ঘটেছে খুবই সরল অবস্থা থেকে, এ কোনো ঈশ্বর বা দেবতাদের কারসাজি নয়, পৃথিবী শুধুই একটি গ্রহ যা সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে আর নক্ষত্রেরা অনেক দূরে। তারাই ছিলেন কৃষকের, নাবিকের, তাঁতীদের সন্তান। এঁদের হাতে ছাব্বিশশো বছর আগে বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছিলো। তারপরেও তাদের ধ্বংস হয়ে যেতে হয়েছে কোনো ধারাবাহিকতা না রেখে। এর শত বছর পরে অনেকটা একইভাবে, তবে আরো সুসংগঠিত চিন্তা আর কসমোপলিটন স্বপ্ন নিয়ে জেগে উঠেছিলো ভূমধ্যসাগরের তীরে আলেক্সান্দ্রিয়া। তাঁরা পৃথিবীর পরিধি পরিমাপ করেছিলেন, স্টীম ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেছিলেন। এখানে কাজ করেছিলেন ইরাটোস্থেনিস, ইউক্লীড, আর্কিমিডিস, অ্যারিস্টোকার্স, হাইপেশিয়ার মতো মহাকালের প্রতিভারা। এখানেই গড়ে উঠেছিলো বিশ্বের সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগার। কিন্তু তাদেরকেও ধ্বংস হয়ে যেতে হয়েছিলো রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উন্মাদনার করাল গ্রাসে কোনো ধারাবাহিকতা না রেখে। পর্যায়ক্রমে রোমান, খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্মের বর্বরা তাদের ধর্মীয় উন্মাদনায় পুড়িয়ে দিয়েছে আলেক্সান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের হাতে লেখা পাঁচ লক্ষাধিক বই। এর ফলে নেমে এসেছিলো মধ্যযুগীয় অন্ধকার, আমরা পিছিয়ে গিয়েছিলাম দেড় হাজার বছর। আলেক্সান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারে ব্যাবিলনের এক ধর্মযাজকের লেখা একটি গ্রন্থে ওল্ড টেষ্টামেন্টে উল্লেখিত সময়পুঞ্জির চেয়ে শতগুন পুরাতন সময়ের ইতিহাস ছিলো - প্রায় ৪ লক্ষ ৩২ হাজার পূর্বের। কী লেখা ছিলো সেই গ্রন্থে? এই প্রশ্নের উত্তরকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদের বর্বর পান্ডা-পুরুতগণ। তারপর অনেক অনেক যুগ পেরিয়ে এসে কোপার্নিকাস, কেপলার, গ্যালিলিওর মতো পন্ডিতদের অনেক কিছুই পুনঃআবিষ্কার করতে হয়েছিলো। কোপার্নিকাসের পুনঃআবিষ্কারকেই ব্রুনো সাহসীকতার সঙ্গে প্রচার করেছিলেন, নিকোলাস কোপার্নিকাস নিজে যা প্রচার করতে পারেন নি ধর্মীয় গুন্ডাদের ভয়ে। আর সেটাই করেছিলেন বিজ্ঞানের নির্ভুল সত্য প্রচারের নির্ভীক সৈনিক এবং প্রথম শহীদ জিওর্দানো ব্রুনো। এটাই ছিলো তাঁর অপরাধ। এ জন্যই তাঁকে ধর্মীয় উন্মাদরা ইতালীর পিয়ম্বো নগরে দীর্ঘ আট বছর বন্দি করে রেখেছিলেন এমন একটি ঘরে যার ছাদ ছিলো সীসে দিয়ে তৈরি। গরমের সময় ঘরটি হয়ে উঠতো প্রায় অগ্নিময় আর শীতকালে বরফের মতো হিমশীতল। বিচারের সময় ব্রুনো ধর্মযাজকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ‘ শাস্তির কথা শুনে আমি যতোটা ভয় পেয়েছি তারচেয়েও অনেক বেশি ভয় পেয়েছো তোমরা’। ১৬ জন প্রধান ধর্মযাজক তাঁর মৃত্যুদন্ড রায়ের ঘোষনায় বলেন, ‘পবিত্র গীর্জার আদেশে পাপী ব্যক্তির একবিন্দু রক্তও নষ্ট না করে প্রাণদন্ড কার্যকর করতে হবে’। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে রোমে ব্রুনোর মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয় তাঁকে ক্রুশে বেঁধে, প্রকাশ্য দিবালোকে, অগ্নিদগ্ধ করে। ব্রুনো কোপার্নিকাসের চিন্তাকে আরো প্রসারিত করেছিলেন। ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, কতগুলো গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে, পৃথিবীও সেই গ্রহগুলোর একটা। আরো অনেক গ্রহ আবিষ্কৃত হবে এটাই সৌরজগৎ। দূরের নক্ষত্রগুলোও এক একটি সূর্যের মতো, তাদেরও অনেকেরই আছে গ্রহ কিংবা গ্রহমন্ডলী। শুধু পৃথিবীই নয়, সূর্য ঘুরছে তার আপন মেরুতে। এই বিশ্ব অসীম। এর কেন্দ্রে বা প্রান্েত কিছু আছে এ কথা বলা অর্থহীন। পৃথিবী যে স্থির নয়, সে যে ঘুরছে, এ কথা আজ বৈজ্ঞনিকভাবে প্রমাণিত সত্য। ব্রুনোর মতবাদই বিজ্ঞানে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। মিথ্যে হয়ে গেছে বাইবেলের বয়ান। এতো গেলো ইসলাম পূর্ব বাইবেলের মিথ্যাচার। কিন্তু ইসলাম, মাত্র ১৪০০ বছরের নির্ভুল, আধুনিক ধর্ম? সে বাইবেলের একই ভুলকে কী করে প্রশ্রয় দেয়? ইসলামের আল্লাহ যদি জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সর্বজ্ঞানের জ্ঞানীই হন তাহলে তিনি কী করে বাইবেলের মিথ্যে বর্ণনাকে সমর্থন করতে পারেন? কোরানের ২৭:৬১ ও ৩০:২৫ পঙক্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, পৃথিবী স্থির। ১৯৯০ সালে কলকাতার মল্লিক ব্রাদার্স থেকে প্রকাশিত জৈনক মুহম্মদ নুরুল ইসলাম তাঁর ‘পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে’ নামক গ্রন্থে কোরানের ১১টি সুরার ১২টি পঙক্তি দ্বারা জোরজবরদস্তি প্রমাণ করতে চেয়েছেন- পৃথিবী অনড়, স্থির। তাঁর মতে পৃথিবী যদি সত্যি সত্যি ঘুরতো তাহলে আমরা সমস্ত জীবজন্তু উড়ে উড়ে ছিটকে পড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতাম, আর গাছপালা-দালান-কোঠা পাহাড়-পর্বত সব ভেঙ্গেচুড়ে তছনছ হয়ে যেতো! তাঁর এই অপবৈজ্ঞানিক ধারণাকে আজ কোনো বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের পক্ষেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। একে ধর্মীয় অন্ধত্বের উন্মাদনা ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না। এ সমস্ত উন্মাদদের গাঁজাখুরি অপব্যাখ্যা এবং বাইবেল, কোরানের পৃথিবীর অনড়তত্ত্বকে মিথ্যে প্রমাণিত করে আমাদের শ্যামল পৃথিবী নামক গ্রহটি ঘুরেই চলছে সেকেন্ডে সূর্যের চারিদিকে ১৬ মাইল বেগে। আর সূর্য অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহকে নিয়ে ছুটে চলছে আন্তঃনাক্ষত্রিক শূণ্যতার মধ্য দিয়ে সেকেন্ডে ৪২ মাইল গতিতে। এবং এইভাবে পুরো মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিকে একবার ঘুরে আসছে ২৫ কোটি বছরে। কি স্বপ্নের মতো এই বিজ্ঞান, অথচ বাস্তব এবং সত্য। আর কি চকমকে সত্যের মতো মানুষের ধর্মচেতনা ও ঈশ্বর বিশ্বাস, যা আসলেই অবাস্তব ও অলীক। =========================== ডাঃ ওয়াহিদ রেজা বাঙলাদেশের প্রখ্যাত কবি ও কথাসাহিত্যিক। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। লেখাটি আমাদের মুক্তমনার পরবর্তী বই -‘বিজ্ঞান ও ধর্ম – সংঘাত নাকি সমন্বয়?’– প্রকাশিতব্য সংকলন-গ্রন্থের জন্য নির্বাচিত হল - মুক্তমনা সম্পাদক।
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||
|
|
|
|
|